৪৭তম বিসিএস প্রশ্ন সমাধান PDF | 47th BCS Question Solution PDF
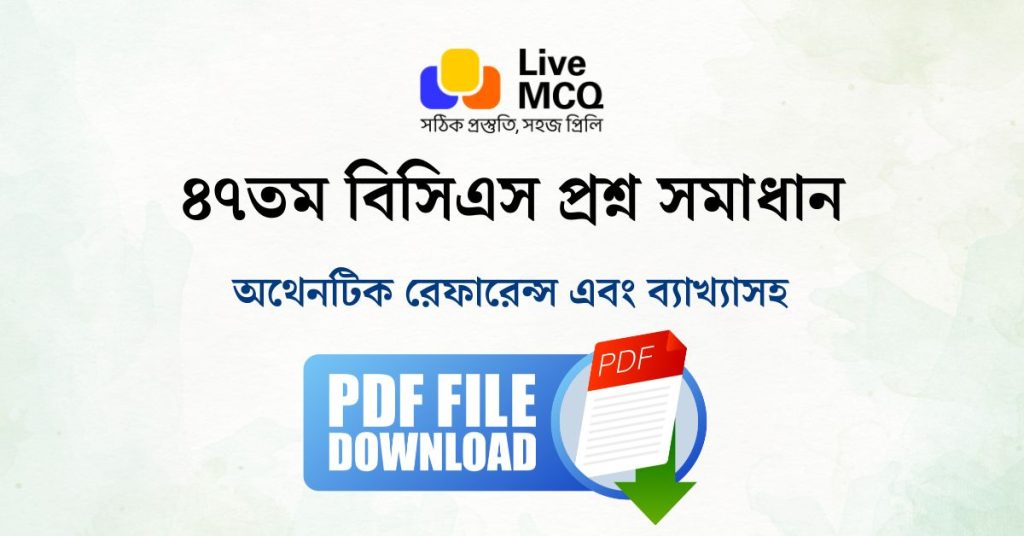

প্রিয় চাকরিপ্রত্যাশীগণ, ৪৭তম বিসিএস প্রশ্ন সমাধান PDF সংক্রান্ত ব্লগে আপনাদের স্বাগতম। চাকরির প্রার্থীগণের কাছে বিসিএস একটি স্বপ্নের নাম। সেই স্বপ্ন জয়ের প্রথম ধাপ-ই হলো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এই ধাপ সফলভাবে অতিক্রম করতে প্রয়োজন কার্যকর প্রস্তুতি। বিসিএস পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের জন্য বিগত সালের প্রশ্ন সমাধানের বিকল্প নেই। কারণ প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রার্থীরা পরীক্ষার ধরণ, প্রশ্নের মান, এবং বিষয়ভিত্তিক গুরুত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারেন।
আপনারা জানেন গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ক্যাডার শূন্য পদ সংখ্যা ৩ হাজার ৪৮৭ ও নন-ক্যাডার পদ রয়েছে ২০১টি। অর্থাৎ ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে মোট ৩ হাজার ৬৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। উক্ত প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন কয়েক লক্ষাধিক প্রার্থী। পরীক্ষার মূল প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পূর্ববর্তী বিসিএস পরীক্ষার মতো এখানেও বাংলা, ইংরেজি, গণিত, সাধারণ জ্ঞান, বাংলাদেশ বিষয়াবলি, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি, ভূগোল, বিজ্ঞান ও কম্পিউটার থেকে সুষম প্রশ্ন করা হয়েছে।
আজকের ব্লগে আমরা অথেনটিক রেফারেন্স ও ব্যাখ্যাসহ ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান PDF প্রকাশ করেছি। এর ফলে প্রার্থীরা খুব সহজেই প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণ করে তাদের প্রস্তুতিকে আরও সুসংহত করতে পারবেন বলে আশা রাখছি। ৪৭তম বিসিএস প্রশ্ন সমাধান PDF-টি আপনারা যেকোন ডিভাইসে ডাউনলোড করতে পারবেন এবং চাইলে প্রিন্ট করেও পড়তে পারবেন।
আরও দেখুন: ৩৫-৪৫ তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন PDF
আরও দেখুন: BCS Question Bank – ১০-৪৬ তম বিসিএস প্রশ্ন ব্যাংক PDF
কেন প্রশ্ন সমাধান গুরুত্বপূর্ণ?
প্রশ্নের ধরণ বোঝা যায় – কোন বিষয় থেকে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে তা সহজে অনুধাবন করা যায়।
সঠিক প্রস্তুতির দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় – কোন অংশে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে এবং কোন অংশে কম সময় দিলেও হবে তা নির্ধারণ করা সহজ হয়।
কমন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে – পূর্ববর্তী বিসিএস পরীক্ষার অনেক প্রশ্নই সরাসরি বা সামান্য পরিবর্তন করে আসতে দেখা যায়।
দুর্বলতা ও শক্তি চিহ্নিত করা যায় – কোন বিষয়ে ভালো প্রস্তুতি আছে আর কোন বিষয়ে ঘাটতি আছে তা বোঝা যায়।
সময় ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে – প্রশ্ন সমাধান অনুশীলনের মাধ্যমে পরীক্ষায় নির্দিষ্ট সময়ে সব প্রশ্ন শেষ করার দক্ষতা তৈরি হয়।
47th BCS Question Solution PDF Download Now
৪৭তম বিসিএস প্রশ্ন সমাধান
পরীক্ষার তারিখ – ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫
মোট নম্বর: ২০০
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
প্রশ্ন ১. ’লুই ভণই গুরু পুছিঅ জান।’- এখানে ’ভণই’ শব্দের অর্থ কী?
ক) বলে খ) ভাবে গ) চায় ঘ) দেখে
সঠিক উত্তর: ক) বলে
Live MCQ Analytics: Right: 20%; Wrong: 13%; Unanswered: 66%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ‘লুই ভণই গুরু পূছিঅ জাণ।’- পঙ্ক্তিটির রচয়িতা চর্যার কবি লুইপা।
– পঙ্ক্তি আধুনিক গদ্যে রূপান্তর- লুই বলেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জানো।
পঙ্ক্তিটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ হলো-
• ‘ভণই‘ অর্থ- বলে। প্রকাশ করে। ভণতি > ভণই।
• ‘পূছিঅ’ অর্থ- জিজ্ঞাসা করে। পুচ্ছতিঃ > পুচ্ছিঅ > পূছিঅ।
• ‘জাণ’ অর্থ- জানো। জানথ > জানহ > জাণঅ > জাণ।
• লুইপা: – ‘চয্যাচর্যবিনিশ্চয়’-এর প্রথম কবি লুইপা। তিব্বতি ঐতিহ্যে প্রাপ্ত চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের নামের তালিকায় লুইয়ের নাম আদিতম। তিনি চর্যার ১ ও ২৯নং পদের রচয়িতা।
– অনেক পণ্ডিত লুইপাকে প্রথম চর্যাগীতি রচয়িতা বলে মনে করেন। তাঁর জীবৎকাল ৭৩০-৮১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। সে সময় ছিল রাজা ধর্মপালের রাজত্বকাল। হিন্দিভাষীরা লুইপাকে মগধ বা বিহারের অধিবাসী বলে দাবি করেন। যোগতন্ত্রশাস্ত্রেও লুইপার উল্লেখ রয়েছে।
তন্ত্রশাস্ত্রের লুইপার অন্য নাম মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। মৎস্যের সঙ্গে নামের মিল থাকায় কোনো কোনো পণ্ডিত ১৮ চর্যাগীতি পাঠ লুইকে শবরপা-এর শিষ্য ও ধীবর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেন।
– এ লুইপা আদি সিদ্ধাচার্য (সকল সিদ্ধাচার্যের গুরু) বলে অনেকের ধারণা। লুইপাকে সংস্কৃত টীকাকার মুনি দত্ত আদি সিদ্ধাচার্য বলে উল্লেখ করেছেন। তবে, তারানাথের মতে, লুইপা চতুর্থ সিদ্ধাচার্য, আর সরহ হলেন আদি সিদ্ধাচার্য। তাঁর মতে, লুইপা ছিলেন উড্ডীয়ান-রাজ উদয়নের কর্মচারী। তিনি শবর পা-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
– চর্যাগীতির লুইপা আর তন্ত্রশাস্ত্রের লুইপা অভিন্ন নয় বলেই মনে করা হয়। কেননা বলা হয়েছে, লুইপা ছিলেন গৌড় অঞ্চলের অধিবাসী। আর তন্ত্রশাস্ত্রের মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের বাড়ি দক্ষিণবঙ্গে। তিনি ছিলেন গোরক্ষনাথের গুরু। তাই ধারণা করা হয়, লুইপা ও মীননাথ অভিন্ন ব্যক্তি নয়।
– হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধারণা লুইপা ছিলেন বাঙালি। রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের মতে, লুইপা রাজা ধর্মপালের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লুইপা বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।
– তিব্বতি অনুবাদের মাধ্যমে লুইয়ের বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ক তিনটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। এগুলো হলো: ‘শ্রীভগবদভিসময়’, ‘অভিসময়বিভঙ্গ’ ও ‘তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টিনাম’।
চর্যার ১নং পদ-
কাআ তরুবার পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
উৎস: চর্যাগীতি পাঠ, মাহাবুবুল হক।
প্রশ্ন ২. ’শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের অংশ নয় কোনটি?
ক) নৌকা খণ্ড খ) হার খণ্ড
গ) রাধা বিরহ ঘ) প্রণয় খণ্ড
সঠিক উত্তর: ঘ) প্রণয় খণ্ড
Live MCQ Analytics: Right: 40%; Wrong: 42%; Unanswered: 17%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ’শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যের অংশ নয় – ঘ) প্রণয় খণ্ড।
• “শ্রীকৃষ্ণকীর্তন” কাব্য:
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন স্বীকৃত। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার করেন।
– ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পুথিটি ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
– পুথির প্রথম দুটি এবং শেষপৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি বলে এর নাম ও কবির নাম স্পষ্ট করে জানা যায় নি। কবির ভণিতায় ‘চণ্ডীদাস’ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ‘বড়ু চণ্ডীদাস’ পাওয়া যাওয়ায় এই গ্রন্থের কবি হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করা হয়।
– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতি-আলেখ্য। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা এর বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থের প্রধান তিনটি চরিত্র হচ্ছে- কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি।
– কাব্যের চরিত্র-মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত আছে; বাক-বিতণ্ডতা, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি আছে। ফলে কাব্যটি গতিশীল ও নাট্যরসাশ্রিত হয়েছে।
– এতে গীতিরসেরও উপস্থিতি লক্ষণীয়। কাব্যটি শৃঙ্গাররসপ্রধান এবং ঝুমুর গানের লক্ষণাক্রান্ত। এটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।
– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে খণ্ডিতপদসহ মোট পদের সংখ্যা ৪১৮টি। পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক আছে ১৬১টি।
– পুঁথির পাতার সংখ্যা ২২৬, অতএব পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫২; এর মধ্যে মাঝের মোট ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। ৪৫ পৃষ্ঠা বাদ গেলে পুঁথির প্রাপ্ত পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪০৭।
– পুঁথির লিপি তিন হাতের লেখা। ৪১৮টি পদের মধ্যে কবির ভণিতা আছে ৪০৯টি।
– শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মোট তের খণ্ডে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেের খণ্ডগুলো হলো-
– জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড,নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড, বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও রাধাবিরহ।
অর্থাৎ, প্রণয় খণ্ড – নামে কোন খণ্ড শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। সুতরাং, সঠিক উত্তর – প্রণয় খণ্ড।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. মাহাবুবুল আলম।
প্রশ্ন ৩. বিবৃত স্বরধ্বনি বলতে বোঝায় –
ক) যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট বেশি খোলে
খ) যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভ উঁচু হয়
গ) যে স্বরধ্বনি অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়
ঘ) যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে বিকৃতি ঘটে
সঠিক উত্তর: ক) যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট বেশি খোলে
Live MCQ Analytics: Right: 70%; Wrong: 13%; Unanswered: 16%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • বিবৃত স্বরধ্বনি বলতে বোঝায়- বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে।
• স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটুকু খোলা বা বন্ধ থাকে অর্থাৎ কী পরিমাণ উন্মুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি চারভাগে বিভক্ত:
– সংবৃত: [ই], [উ];
– অর্ধ-সংবৃত: [এ], [ও];
– অর্ধ-বিবৃত: [অ্যা] [অ];
– বিবৃত: [আ]।
সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খেলে; বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে।
আবার,
• উচ্চারণের সময়ে জিভ কতটা উপরে ওঠে বা কতটা নিচে নামে সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত। যথা-
১. উচ্চ স্বরধ্বনি [ই], [উ]।
২. উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি [এ], [ও]।
৩. নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি [অ্যা], [অ]।
৪. নিম্ন স্বরধ্বনি- [আ]।
উচ্চ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ উপরে ওঠে; নিম্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ নিচে নামে।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (২০২২- সংস্করণ)।
প্রশ্ন ৪. মনোয়েল দ্যা আসসুম্পসাঁও অভিধান প্রকাশের আগে কত বছর ধরে শব্দ সংগ্রহ করেন?
ক) ২-৩ বছর খ) ৫-৭ বছর
গ) ৯-১০ বছর ঘ) ১৪-১৫ বছর
সঠিক উত্তর: গ) ৯-১০ বছর
Live MCQ Analytics: Right: 11%; Wrong: 9%; Unanswered: 78%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ‘Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes’ — গ্রন্থ রচনার জন্য ৯-১০ বছর ধরে শব্দ সংগ্রহ করেছেন।
– মনোএল ভাওয়ালের একটি গির্জায় ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালনকালে ১৭৩৪-৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে Vocabolario em idioma Bengalla, e Potuguez dividido em duas partes শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি ১৭৪৩ সালে প্রকাশ করেন।
বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস:
প্রথম পর্যায়:
• প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় — ১৭৪৩ সালে।
• এটি পর্তুগিজ ভাষায় রচিত, লেখক ছিলেন — মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ।
• তিনি তাঁর — বাংলা-পর্তুগিজ অভিধানের ভূমিকাংশ হিসেবে এই ব্যাকরণ রচনা করেন।
ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ:
• ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় — নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত বাংলা ব্যাকরণ।
• নাম: A Grammar of the Bengal Language. এটি ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ।
• ১৮০১ সালে — উইলিয়াম কেরি ইংরেজি ভাষায় রচনা করেন — A Grammar of the Bengalee Language। এর বঙ্গানুবাদ করেন — জন রবিনসন (১৮৪৬)।
বাংলা ভাষায় রচিত ব্যাকরণ:
• ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হয় — রামমোহন রায়ের — ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’।
• এটি বাংলা ভাষায় রচিত — প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।
উৎস: – বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (নবম-দশম শ্রেণি, সংস্করণ ২০২১)। বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৫. ‘আলালের ঘরের দুলাল‘ প্রথমে কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়?
ক) বিবিধার্থ সংগ্রহ খ) সংবাদ প্রভাকর
গ) মাসিক পত্রিকা ঘ) বঙ্গদর্শন
সঠিক উত্তর: গ) মাসিক পত্রিকা
Live MCQ Analytics: Right: 29%; Wrong: 30%; Unanswered: 40%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: “আলালের ঘরের দুলাল” উপন্যাস:
– প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম গ্রন্থ ‘আলালের ঘরের দুলাল’। আলালের ঘরের দুলাল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সফল উপন্যাসও। আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসটি ১৮৫৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এর আগে ১৮৫৪ সাল থেকে ‘মাসিক পত্রিকা‘তে ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হতে থাকে।
– কলকাতার সমকালীন সমাজ এর প্রধান বিষয়বস্তৃত। উচ্চবিত্ত ঘরের আদুরে সন্তান মতিলালের উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার এতে বর্ণিত হয়েছে। ‘ঠকচাচা’ এর অন্য একটি প্রধান চরিত্র।
– কথ্যভঙ্গির গদ্য ব্যবহার করে লেখক উপন্যাসকে বাস্তবধর্মী করে তুলেছেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার নতুন সম্ভাবনাও আবিষ্কৃত হয়েছে। প্যারীচাঁদ প্রথমবারের মতো এতে যে কথ্য চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন, পরবর্তীকালে তা ‘আলালী ভাষা’ নামে পরিচিতি লাভকরে।
– কাহিনি ও চরিত্রের যথাযথ পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে লেখক এতে প্রচুর তদ্ভব, চলিত এবং বিদেশি শব্দও ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটি প্রথমে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকায় (১৮৫৪) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে হীরালাল মিত্রকৃত এর নাট্যরূপ বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় (জানুয়ারি ১৮৭৫)। গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।
– উপন্যাসটিতে দেশীয় বন্ধ্যা শিক্ষা ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে লেখক তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন।
– ধনী বাবুরামের পুত্র মতিলাল কুসঙ্গে পড়ে এবং শিক্ষার ব্যাপারে পিতার অবহেলা তাকে অধঃপতনে নিয়ে যায়। পিতার মৃত্যুর পর মতিলাল তার বাবার প্রাপ্ত সব সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে।
– উপন্যাসটিতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো মোকাজান মিয়া বা ঠকচাচা।এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে রয়েছে-
– বাবুরাম, বাবুরামের পুত্র মতিলাল, ধূর্ত উকিল বটলর, অর্থলোভী বাঞ্ছারাম, তোষামোদকারী বক্রেশ্বর ইত্যাদি।
• প্যারীচাঁদ মিত্র:
– প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন একজন লেখক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী ও ব্যবসায়ী। ১৮১৪ সালের ২২ জুলাই কলকাতায় তাঁর জন্ম।
– প্যারীচাঁদ মিত্রের শিক্ষাজীবন শুরু হয় পারিবারিক পরিমণ্ডলে। তিনি পণ্ডিত ও মুনশির নিকট যথাক্রমে বাংলা ও ফারসি শেখেন। ১৮২৭ সালে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং খ্যাতিমান শিক্ষক হেনরি ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করেন।
– কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান হিসেবে ১৮৩৬ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের কর্মজীবন শুরু হয়।
– বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে এবং বিবর্তনের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের (১৮৪১-৮৩) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্যের যে সাধুরূপ গড়ে উঠেছিল, প্যারীচাঁদ মিত্র তা অনুকরণ না করে বাংলা গদ্যের ধারায় এক অভিনব লঘু ভঙ্গির প্রবর্তন করেন।
প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্যকর্মগুলো হলো-
• প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ ‘মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়’ ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মধ্যে তৎকালীন গোঁড়া শ্রেণির ব্যক্তিদের চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। আলালের ঘরের দুলালের ভাষার মতই সহজ সরল এর ভাষা, কিন্তু কিছু পরিমাণে সাধুভাষা ঘেঁষা বলে বিশুদ্ধতর। সমসাময়িক কোন কোন লেখকের ওপর এই গ্রন্থ বেশ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল।
• প্যারীচাঁদের অন্যান্য গ্রন্থ ‘রামারঞ্জিকা’ (১৮৬০) স্ত্রীশিক্ষামূলক গ্রন্থ।
• ‘কৃষিপাঠ’ (১৮৬১), ‘যৎকিঞ্চিৎ’ (১৮৬৫), ‘ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত’ (১৮৭৮) প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধ পুস্তক। • ‘অভেদী’ (১৮৭১), ‘আধ্যাত্মিকা’ (১৮৮০) ইত্যাদি গ্রন্থ সংলাপপ্রধান গল্পমূলক রচনা এবং মূলত নীতিবিষয়ক।
•’গীতাঙ্কুর’ (৩য় সংস্করণ, ১৮৭০) ব্রহ্মবিষয়ক গানের সমষ্টি।
• ‘এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা’ (১৮৭৮) গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের নারীদের শিক্ষা ও মহত্ত্বের পরিচয় উপলক্ষে পৌরাণিক নারীচরিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
‘বামাতোষিণী’ (১৮৮১) প্যারীচাঁদ মিত্রের সর্বশেষ রচনা-নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটির রচিত।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. মাহাবুবুল আলম এবং বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৬. ‘সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।‘- কোন কবিতার অংশ?
ক) পরার্থে খ) পাছে লোকে কিছু বলে
গ) বড় কে ঘ) সুখ
সঠিক উত্তর: ঘ) সুখ
Live MCQ Analytics: Right: 11%; Wrong: 88%; Unanswered: 0%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ‘সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।‘ পঙ্ক্তিদ্বয় কামিনী রায় রচিত ‘সুখ‘ কবিতার অন্তর্গত।
– মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি ‘আলো ও ছায়া’ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ‘সুখ’ কবিতাটি ঐ কাব্যগ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত।
– আমরা সবাই জীবনে সুখী হতে চাই। কিন্তু কীভাবে জীবনে সুখ আসতে পারে, ‘সুখ’ কবিতায় কবি সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা তুলে ধরেছেন।
‘’সুখ’ কবিতার কিছু অংশ সংক্ষেপে দেয়া হলো-
সুখ
– কামিনী রায়
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী ‘পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।
পঙ্ক্তিটির বিষয়ে প্রচলিত কিছু বিভ্রন্তি:
কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘আলো ও ছায়া’ যার একটি কবিতার নাম ‘সুখ’। ‘পরার্থে’ নামে কামিনী রায়ের কাব্যগ্রন্থে কোন কবিতা নেই। কিন্তু, পুরনো বোর্ড বইয়ে [২০১৪ সালের] ‘সুখ’ কবিতার কিছু অংশ নিয়ে ‘পরার্থে’ নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। বড় গ্রন্থের অংশ বিশেষ নিয়ে অন্য নামে কবিতা বা গল্প বোর্ড বইয়ে দেওয়া হয়ে থাকে এবং ক্ষেত্রেও সেরকম ঘটেছে।বর্তমান ২০২৫ সালের বোর্ড বইতে মূল কবিতার নাম অনুসারে ‘সুখ’ কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সেই অনুসারেই উত্তর ধরা হয়েছে।
দ্রষ্টব্য: আমাদের আর্কাইভে যে দুয়েকবার এটা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, সেখানে অপশনে ‘সুখ’ ছিল না।
বিভ্রান্তির কারণ:
– সুখ কবিতার উল্লিখিত পঙ্ক্তিতে পরার্থপরতা ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ‘পরার্থে’ শব্দটি এই পঙ্ক্তির মূল ভাবের সাথে মিলে যাওয়ায় অনেকে ভুল করে এটিকে ‘পরার্থে’ নামক কবিতার অংশ মনে করেন। কিন্তু কামিনী রায়ের কোনো কবিতা ‘পরার্থে’ নামে পরিচিত নয়।
? পরীক্ষায় যদি অপশনে শুধু পরার্থে থাকে → উত্তর হবে পরার্থে।
? যদি শুধু সুখ থাকে → উত্তর হবে সুখ।
? যদি সুখ ও পরার্থে দুটোই থাকে → সঠিক উত্তর হবে সুখ।
• কামিনী রায়:
– কামিনী রায় ছিলেন কবি ও সমাজকর্মী। ১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর বাকেরগঞ্জের বাসন্ডা গ্রামে তাঁর জন্ম।
– একসময় তিনি ‘জনৈক বঙ্গমহিলা’ ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর কবিতা সহজ, সরল, মানবিক ও উপদেশমূলক। তাঁর কবিতায় জীবনের মহৎ আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় আছে।
– সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২৯) ‘জগত্তারিণী পদকে’ সম্মানিত হন।
– তিনি ‘নারী শ্রম তদন্ত কমিশন’ (১৯২২-২৩) এর সদস্য ছিলেন।
– তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সালে হাজারীবাগ, বিহারে মৃত্যুবরণ করেন।
– ‘আলো ও ছায়া’ (১৮৮৯): এটি তাঁর ১৫ বছর বয়সে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
– ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।
তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হলো:
– নির্মাল্য, পৌরাণিকী, গুঞ্জন (শিশুকাব্য), ধৰ্ম্মপুত্র (অনুবাদ), মাল্য ও নির্মাল্য, অশোকসঙ্গীত (সনেট), অম্বা (নাটক)।
উৎস: বাংলাপিডিয়া; ‘আলো ও ছায়া’ কাব্যগ্রন্থ এবং চারুপাঠ ষষ্ঠ শ্রেণি (২০১৯-সংস্করণ)।
প্রশ্ন ৭. কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয়নি?
ক) অগ্নিবীণা খ) বিষের বাঁশি
গ) ভাঙার গান ঘ) চন্দ্রবিন্দু
সঠিক উত্তর: ক) অগ্নিবীণা
Live MCQ Analytics: Right: 68%; Wrong: 19%; Unanswered: 11%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • কাজী নজরুল ইসলামের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ৫টি।
যথা-
– যুগবাণী: প্রবন্ধ গ্রন্থ, নিষিদ্ধ হয় ২৩ নভেম্বর, ১৯২২, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১৯৪৭।
– বিষের বাঁশী: কবিতাগ্রন্থ, নিষিদ্ধ ২২ অক্টোবর, ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞাপা প্রত্যাহার ২৭ এপ্রিল, ১৯৪৫।
– ভাঙার গান: কবিতাগ্রন্থ, নিষিদ্ধ ১১ অক্টোবর, ১৯২৪।
– প্রলয় শিখা: কবিতাগ্রন্থ, নিষিদ্ধ, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।
– চন্দ্রবিন্দু: গানের সংকলন, নিষিদ্ধ ১৪ অক্টোবর, ১৯৩১।
– নজরুলের আরও কিছু বই বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ থাকলেও শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়নি।
যেমন- অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা, ফণিমনসা, সর্বহারা, রুদ্রমঙ্গল এ বইগুলো বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ থাকলেও নিষিদ্ধ হয়নি।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাজী নজরুল ইসলামের ‘অগ্নিবীণা‘ কাব্যগ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়নি।
তবে এই কাব্যের অংশবিশেষ বা এর সাথে সম্পর্কিত কবিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বিশেষত ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে ‘ধূমকেতু’ পত্রিকার ১২-তম সংখ্যায় নজরুলের রাজনৈতিক কবিতা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’ প্রকাশের জন্য ব্রিটিশ সরকার নজরুলকে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং ঐ সংখ্যাটি নিষিদ্ধ করে। তবে, অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থটি কখনো নিষিদ্ধ হয়নি, বরং এর প্রকাশনা ব্রিটিশ শাসনের অধীনেই সম্পন্ন হয়েছিল।
১৯২২ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৫টি গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়। গ্রন্থগুলো হলো:
• “যুগবাণী” প্রবন্ধ গ্রন্থ:
– নজরুলের প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হয় তার নাম “যুগবাণী”। ‘নবযুগ’ পত্রিকায় লেখা কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি নিবন্ধনের সংকলন হলো এই ‘যুগবাণী’ প্রবন্ধ গ্রন্থটি।
– ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর ফৌজদারি বিধির ৯৯এ ধারানুসারে তৎকালীন বাংলার ব্রিটিশ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে (গেজেট নং ১৬৬৬১পি)। সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও বর্মা সরকার যুগপৎ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে “যুগবাণী” নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
– তৎকালীন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে ‘যুগবাণী’কে একটি ভয়ংকর বই হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়, লেখক বইটির মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করছেন।’ক্রীতদাস মানসিকতার’ ভারতীয় জনগণকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শাসনভার দখলের মন্ত্রণা জোগাচ্ছেন।
• ‘বিষের বাঁশি” ও “ভাঙার গান” কাব্যগ্রন্থ:
– দ্বিতীয় পর্যায়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নজরুলের দুটি কবিতার বই ‘বিষের বাঁশি” ও “ভাঙার গান”।
– ১৯২৪ সালের ২২ অক্টোবর (মতান্তরে ২৪ অক্টোবর) গেজেট ঘোষণায় (গেজেট নং-১০৭২পি) ‘বিষের বাঁশি’ নিষিদ্ধ হয়। ‘ভাঙার গান’ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ১৯২৪ সালের ১১ নভেম্বর।
• ‘প্রলয়শিখা’ কাব্যগ্রন্থ:
– কাজী নজরুল ইসলামের চতুর্থ নিষিদ্ধ হওয়া গ্রন্থের নাম প্রলয়শিখা। প্রলয়শিখা কাব্যগ্রন্থটি ১৯৩০ সালের আগস্টে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩০ সালের ১৭সেপ্টেম্বর গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়।
– এই গ্রন্থের ‘যতীন দাশ’, ‘পূজা অভিনয়’, ‘হবে জয়’, ‘জাগরণ’, ‘নব ভারতের হলদিঘাট’ প্রভৃতি কবিতাগুলোকে রাজদ্রোহমূলক আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ (গেজেট নং ১৪০৮৭পি) করা হয়।
• “চন্দ্রবিন্দু” সঙ্গীত-গ্রন্থ:
কবির সর্বশেষ নিষিদ্ধ হওয়া গ্রন্থ “চন্দ্রবিন্দু”। এটি একটি গীতিগ্রন্থ। ১৪ অক্টোবর ১৯৩১ তারিখে ‘চন্দ্রবিন্দু’ নিষিদ্ধ হয় (গেজেট নং ১৭৬২৫)।
উপসংহার:
– কাজী নজরুলের প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হয় তার নাম ‘যুগবাণী’।
১৯২২ সালে ফৌজদারি বিধির ৯৯এ ধারানুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।
– প্রথম নিষিদ্ধ হওয়া কাব্যগ্রন্থ – বিষের বাঁশি।
১৯২৪ সালের ২২ অক্টোবর (মতান্তরে ২৪ অক্টোবর) গেজেট ঘোষণায় (গেজেট নং-১০৭২পি) ‘বিষের বাঁশি’ নিষিদ্ধ হয়।
– কবির সর্বশেষ নিষিদ্ধ হওয়া গ্রন্থ “চন্দ্রবিন্দু”। এটি একটি গানের সংকলন।
১৪ অক্টোবর ১৯৩১ তারিখে ‘চন্দ্রবিন্দু’ নিষিদ্ধ হয় (গেজেট নং – ১৭৬২৫)।
– পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সংখ্যায় নজরুলের কবিতা আনন্দময়ীর আগমনে প্রকাশিত হয়। এই রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় ৮ নভেম্বর পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; নিষিদ্ধ নজরুল, শিশির কর; প্রথম আলো ও দৈনিক সমকালে প্রকাশিত নজরুল জন্মবার্ষিকীর বিশেষ সংখ্যা এবং বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৮. জসীম উদ্দীনের ‘কবর‘ কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?
ক) বালুচর খ) রাখালী
গ) ধানক্ষেত ঘ) মা যে জননী কান্দে
সঠিক উত্তর: খ) রাখালী
Live MCQ Analytics: Right: 81%; Wrong: 6%; Unanswered: 11%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ‘কবর‘ কবিতা:
– ‘কবর’ কবিতাটি কবি জসীম উদ্দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘রাখালী‘ (১৯২৭) এর অন্তর্ভুক্ত।
– কবর কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ‘কল্লোল’ পত্রিকায়। এটি মত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত যাতে ১১৮টি পঙ্ক্তি আছে।
– কাহিনিধর্মী এই কবিতাটিতে সহজ সরল ভাষায় এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবনের প্রিয়জন হারানোর বেদনার স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে বৃদ্ধ যে তাঁর আপনজনদের হারিয়ে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন, তারই বর্ণনা কবি গভীর সহানুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।
– ‘কবর’ কবিতাটি সংক্ষেপে দেয়া হলো-
কবর
–জসীম উদ্দীন
এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালি ঊষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙল লইয়া খেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
• ‘রাখালী‘ কাব্যগ্রন্থ:– জসীম উদ্দীন রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে।
– বইটিতে মোট ১৯টি কবিতা আছে। এই কাব্যের প্রথম কবিতা হচ্ছে ‘রাখালী’।
– তাঁর বিখ্যাত ‘কবর’ কবিতাটি এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
• জসীম উদ্দীন:
– তিনি একাধারে করি, কাব্যোপন্যাসিক, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, ভ্রমণকাহিনীকার, নাট্যকার, স্মৃতিকথক, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক ইত্যাদি বছবির পরিচয়ে পরিচিত।
-১৯০০ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে মাতুলালয়ে তার জন্ম। পৈতৃক নিবাস একই জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে।
– তাঁর নকশী কাঁথার মাঠ ও সোজন বাদিয়ার ঘাট বাংলা ভাষার গীতি-কবিতার উৎকৃষ্টতম নিদর্শনগুলোর অন্যতম।
– ‘বোবা কাহিনী’ তাঁর একমাত্র উপন্যাস।
• তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ:
রাখালী, নকশী কাঁথার মাঠ, বালুচর, ধানক্ষেত, সোজন বাদিয়ার ঘাট, হাসু, মাটির কান্না, এক পয়সার বাঁশী, সবিনা,
মা যে জননী কান্দে, পদ্মা নদীর দেশে ইতাদি।
• তাঁর রচিত নাটক:
পদ্মাপার, বেদের মেয়ে, পাল্লীবধূ ইত্যাদি।
• তার রচিত আত্মকথা:
যাদের দেখেছি, ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়, জীবন কথা ইত্যাদি।
• তাঁর ভ্রমণ কাহিনি:
চাল মুসাফির, হলদে পরির দেশে, যে দেশে মানুষ বড় ইত্যাদি।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; বাংলাপিডিয়া এবং দ্বাদশ শ্রেণি সাহিত্য পাঠ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ৯. গৌড়ী প্রাকৃত বলতে বোঝায়-
ক) গৌড় অঞ্চলের মুখের ভাষা খ) গৌড় সাহিত্যের স্বাভাবিক রীতি
গ) গৌড় ভাষার লিখিত নমুনা ঘ) গৌড় ভাষার বিকৃত উচ্চারণ
সঠিক উত্তর: ক) গৌড় অঞ্চলের মুখের ভাষা
Live MCQ Analytics: Right: 40%; Wrong: 30%; Unanswered: 28%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • গৌড়ী প্রাকৃত বলতে বোঝায়- গৌড় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা।
• ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে , গৌড় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অর্থ প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে।
অর্থাৎ বাংলা ভাষার উৎপত্তি গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে, অর্থাৎ সপ্তম শতকে, গৌড়ি প্রাকৃত থেকে জন্ম নিয়েছিল আধুনিকতম প্রাকৃত বাংলা ভাষার। তাহলে দেখা গেল বাংলা ভাষার উৎপত্তি সরাসরি সংস্কৃত ভাষ্য থেকে হয়নি।
– অর্থাৎ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে গৌড়ী অপভ্রংশ হয়ে বঙ্গকামরূপী ভাষার মাধ্যমে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষা স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করে।
• কিন্তু ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন মগধ জনপদের মানুষের মুখের ভাষা। অর্থাৎ মগধ অঞ্চলের প্রাকৃজনের ভাষা বা মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা উৎপত্তি লাভ করেছে।
– সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন দশ শতকে, ১০০ থেকে ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, মাগবি অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।
– কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন খ্রিষ্টীয় সাত শতকে, ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, গৌড় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।
প্রথম থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের বাংলা ভাষাকে প্রধানত তিন যুগে ভাগ করা হয়। যেমন: ১। প্রাচীন যুগ: ৬৫০ (মতান্তরে ১৫০) থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত।২। মধ্যযুগ: ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত।
৩। আধুনিক যুগ: ১৮০০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত।
[এর মধ্যে ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত কালকে সন্ধিযুগ বা অন্ধকার যুগ ধরা হয়।]
বাংলা ভাষা বিবর্তনের রূপরেখা-
উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।
প্রশ্ন ১০. ‘Glossary’ শব্দের বাংলা পরিভাষা-
ক) জ্ঞাপনপত্র খ) সর্বসাকল্যে
গ) শব্দার্থপঞ্জি ঘ) গুদামজাত
সঠিক উত্তর: গ) শব্দার্থপঞ্জি
Live MCQ Analytics: Right: 43%; Wrong: 23%; Unanswered: 32%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ‘Glossary’ (noun).
বাংলা অর্থ:- টীকাপুঞ্জ;– শব্দার্থপঞ্জি;
– ব্যাখ্যাবিশিষ্ট (যথা পরিভাষায় ব্যবহৃত বা অপ্রচলিত) শব্দের ব্যাখ্যাসংবলিত তালিকা;
– টীকাগ্রন্থ বা শব্দকোষ।
অন্যদিকে,
• ‘Hand out’ অর্থ – জ্ঞাপনপত্র।
• ‘Collectively/ In all/ In total’ অর্থ – সর্ব-সাকল্যে।
এরূপ কিছু পারাভাষিক শব্দ হলো-
– Hand-bill – ইশতেহার বা প্রচারপত্র। Paragraph – অনুচ্ছেদ। Pamphlet – পুস্তিকা। Notification – প্রজ্ঞাপন। Broadcast – সম্প্রচার। Advertisement – বিজ্ঞাপন।
উৎস: বাংলা একাডেমি, প্রশাসনিক পরিভাষা এবং অভিগম্য অভিধান।
প্রশ্ন ১১. ‘ঐক্যমত‘ শব্দটি কোন বিবেচনায় অশুদ্ধ নয়?
ক) মতের ঐক্য – এভাবে সমাসসাধিত ধরলে
খ) একমত+য – এভাবে প্রত্যয়সাধিত ধরলে
গ) ঐক্য+মত – এভাবে উপসর্গসাধিত ধরলে
ঘ) ঐক্যমত শব্দটিকে পারিভাষিক শব্দ ধরলে
সঠিক উত্তর: ক) মতের ঐক্য – এভাবে সমাসসাধিত ধরলে
Live MCQ Analytics: Right: 49%; Wrong: 21%; Unanswered: 29%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) মতের ঐক্য – এভাবে সমাসসাধিত ধরলে।
ব্যাখ্যা: ‘ঐক্যমত’ শব্দটি বাংলা ভাষায় একটি সমাসসাধিত শব্দ, যা ‘মতের ঐক্য’ থেকে গঠিত। এটি একটি তৎপুরুষ সমাস, যেখানে ‘মত’ (বিশেষ্য) এবং ‘ঐক্য’ (বিশেষ্য) মিলে ‘মতের ঐক্য’ বোঝায়, অর্থাৎ ‘একই মতামত’ বা ‘মতৈক্য’। বাংলা ব্যাকরণে সমাসের মাধ্যমে এ ধরনের শব্দ গঠন সঠিক এবং প্রচলিত। তাই, ‘ঐক্যমত’ শব্দটি সমাসসাধিত হিসেবে বিবেচিত হলে অশুদ্ধ নয়।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।
প্রশ্ন ১২. ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল-
ক) বানানকে উচ্চারণের কাছাকাছি নেওয়া
খ) বানানের ঐতিহ্যকে বজায় রাখা
গ) বানানের নিয়ম প্রণয়ন করা ঘ) বানানে বিকল্প বর্জন করা
সঠিক উত্তর: গ) বানানের নিয়ম প্রণয়ন করা
Live MCQ Analytics: Right: 39%; Wrong: 20%; Unanswered: 39%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • বাংলা বানানের নিয়ম:
– উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলা গদ্যরচনা আরম্ভ হলে বাংলা বানানে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ব্যাপারটি অনুধাবন করে একটি বানান-রীতি প্রণয়নের জন্য ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ‘কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি’ গঠন করে। এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মে প্রথম বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশ করে।
– প্রায় দুইশ লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করে সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করেছিল।
– কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার-সমিতি বাংলা বানানের এইসব নিয়ম প্রবর্তিত করেছিলেন পঁয়ষট্টি বছর আগে। ইতিমধ্যে প্রচুর বিতর্ক ও আলোচনা গড়িয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বানানে পরিবর্তন এসেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবের মূল কাঠামো স্বীকার করে নিলেও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সংস্থা অনেকগুলি পরিবর্তন সাধন করেছেন, কিছু-কিছু পরিবর্তন ভাষায় স্বাভাবিকভাবে এসেও গেছে।
– বাংলা একাডেমি এই নিয়ম প্রণয়নে উদ্যোগী হয় ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে।
উৎস: বাংলা বানানের নিয়ম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; দৈনিক পত্রিকা রিপোর্ট এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
প্রশ্ন ১৩. অভিধানে ং, ঃ, ঁ, – এই বর্ণগুলোর অবস্থান কোথায়?
ক) স্বরবর্ণের আগে খ) স্বরবর্ণের শেষে
গ) ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে ঘ) এদের নির্দিষ্ট অবস্থান নেই
সঠিক উত্তর: খ) স্বরবর্ণের শেষে
Live MCQ Analytics: Right: 21%; Wrong: 56%; Unanswered: 21%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • বাংলা একাডেমি বর্ণানুক্রম:
এই অভিধানে অনুসৃত বর্ণানুক্রমে ড়-কে ড-এর পরে, ঢ়-কে ঢ-এর পরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ব্যাকরণে হসযুক্ত ব্যঞ্জনকে তার অব্যবহিত পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জনরূপে বিবেচনা করা হয়। এই যুক্তিতে ৎ-র (= ত্) স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে স্বরযুক্ত ত-এর পরে এবং ত এর সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনের অব্যবহিত পূর্বে। হসযুক্ত অন্যান্য ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসৃত হয়েছে। য়-কে য-এর পরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রচলন মেনে অনুস্বার (ং), বিসর্গ (ঃ) এবং চন্দ্রবিন্দুকে (ঁ) স্বরবর্ণের পরে এবং ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে বিন্যাস করা হয়েছে।
বাংলা একাডেমি অভিধানে বর্ণগুলোকে নিম্নোক্ত ক্রমে সাজানো থাকে-
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।
প্রশ্ন ১৪. পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে ‘স্মরণ‘ শব্দের ক্ষেত্রে কোনটি ঘটে?
ক) স-এর উচ্চারণ শ হয়ে যায় খ) ণ-এর উচ্চারণ ন হয়ে যায়
গ) ম-ফলার উচ্চারণ ম হয়ে যায় ঘ) শুরুতে নাসিক্য উচ্চারণ হয় না
সঠিক উত্তর: ক) স-এর উচ্চারণ শ হয়ে যায়
Live MCQ Analytics: Right: 41%; Wrong: 17%; Unanswered: 40%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারেভ স্মরণ (বিশেষ্য পদ) শব্দের প্রমিত উচ্চারণ – শঁরোন্।
• পূর্ববঙ্গীয় (ঢাকাইয়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী ইত্যাদি) উচ্চারণে “স্ম” ধ্বনির শুরুতে “স” প্রায়শই “শ” ধ্বনিতে রূপ নেয়। তাই “স্মরণ” উচ্চারণ হয় “শঁরোন”। সুতরাং পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে স-এর উচ্চারণ শ হয়ে যায়।
অন্যান্য অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
খ) ণ-এর উচ্চারণ ন হয়ে যায়: লিখিত রূপে ‘ণ’ থাকলেও উচ্চারণগত দিক থেকে এ বর্ণটি দন্ত্য ‘ন’-এর সঙ্গে অভিন্ন। ‘ণ’ ও ‘ন’ এর উচ্চারণগত ভিন্নতা নেই দুইটি পরিপূরক বর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। স্মরণ শব্দে ‘ণ’ এর উচ্চারণগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, তাই এটি সঠিক নয়।
গ) ম-ফলার উচ্চারণ ম হয়ে যায়: ‘স্মরণ’ শব্দে ‘ম’ ফলাযুক্ত নয়; এটি একটি স্বাধীন ব্যঞ্জনবর্ণ। তাই এই অপশনটি প্রযোজ্য নয়।
ঘ) শুরুতে নাসিক্য উচ্চারণ হয় না: ‘স্মরণ’ শব্দে শুরুতে নাসিক্য ধ্বনি (ঁ) থাকে (যেমন: শঁরোন্), এবং পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে এই নাসিক্যতা সাধারণত বজায় থাকে। তাই এটি সঠিক নয়।
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান এবং ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।
প্রশ্ন ১৫. ‘গড্ডলিকা প্রবাহ‘ বাগ্ধারার ‘গড্ডল‘ শব্দের অর্থ কী?
ক) নদী খ) স্রোত গ) ভেড়া ঘ) মশা
সঠিক উত্তর: গ) ভেড়া
Live MCQ Analytics: Right: 82%; Wrong: 6%; Unanswered: 11%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • গড্ডল (বিশেষ্য পদ),
– এটি একটি অর্বাচীন সংস্কৃত শব্দ।
অর্থ:
– ভেড়া, মেষ, গাড়ল।
উল্লেখ্য,
• ‘গড্ডলিকা প্রবাহ’ বাগ্ধারার অর্থ- অন্ধ অনুকরণ।
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান এবং ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।
প্রশ্ন ১৬. ‘এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।/পরানে পরান বান্ধা আপনা আপনি।।‘ কার লেখা?
ক) বিদ্যাপতি খ) চণ্ডীদাস
গ) জ্ঞানদাস ঘ) গোবিন্দদাস
সঠিক উত্তর: খ) চণ্ডীদাস
Live MCQ Analytics: Right: 23%; Wrong: 16%; Unanswered: 59%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ‘এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।/পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি।‘- পঙ্ক্তিদ্বয় বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের রচনা।
• শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চণ্ডীদাসের পদাবলি থেকে। কবি রাধার মনের বিচিত্র অনুভূতিকে আশ্চর্য সুন্দর ভাষায় রূপদান করে বাঙালির চিরদিনের সমাদর লাভের উপযোগী করে গেছেন। তাঁর পদাবলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতির রূপকের মাধ্যমে সে ধর্মীয় চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এর রূপকের বাইরে একটা সর্বজনীন ও সার্বভূমিক আবেদন বিদ্যমান।
• চণ্ডীদাস রাধাকে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারারূপে চিত্রিত করেছেন। দেহগত কামনা-বাসনা রাধাচরিত্রে প্রাধান্য পায় নি। কবি তাকে মর্ত্যলোক থেকে বহু দূরদুর্গম অধ্যাত্মতীর্থে স্থান দিয়েছেন। চণ্ডীদুল রাধার কামগন্ধহীন প্রেম অত্যন্ত সহজ সরল কথায় ছন্দে ও অলঙ্কার প্রয়োগে প্রস্ফুটিত করেছেন। কবি রাধার চরিত্রে মিলনের আনন্দের চেয়ে বিচ্ছেদের বেদনা তীব্রতর করে রূপ দিয়েছেন। কবি এই অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন:
এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি।
দুই কোরে দুই কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।
জল বিনু মীন যেন কবহু না জীয়ে।
• চণ্ডীদাস:
– চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ছিলেন। চণ্ডীদাসকে বাংলা ভাষার প্রথম মানবতাবাদী কবি বলা হয়।
– তিনি ‘শুনহ মানুষ ভাই/ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই’ বলে জাত-পাতযুক্ত সমাজে প্রথম মানবতার বাণী কাব্যে ধারণ করেছেন বলে তাকে মানবতার কবি বলা হয়। তাছাড়া ব্যক্তিজীবনেও
তিনি জাত-সংস্কারের ঊর্ধ্বে ছিলেন।
– চন্ডীদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন “চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি-এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি”।
– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি বলেছিলেন।
উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. মাহাবুবুল আলম এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
প্রশ্ন ১৭. ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বে রচিত বাংলা বইগুলো-
ক) সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ খ) ফারসি বইয়ের অনুবাদ
গ) ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ ঘ) পণ্ডিতদের রচিত মৌলিক গ্রন্থ
সঠিক উত্তর: ক) সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ
Live MCQ Analytics: Right: 12%; Wrong: 63%; Unanswered: 23%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • সঠিক উত্তর- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বে রচিত বাংলা বইগুলো- সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ।
• ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত) পর্বে (বিশেষত ১৮০১-১৮১৫) বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু এই সময়ে রচিত বাংলা গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে রচিত হয়েছে। উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে দেশীয় পণ্ডিতরা (যেমন, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলকনাথ শর্মা) এই কাজ করেন। এই গ্রন্থগুলো কলেজের ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত হয়েছে, যাতে সংস্কৃতের কৃত্রিম গাম্ভীর্য এবং সাধু ভাষার প্রাধান্য লক্ষণীয়।
উদাহরণস্বরূপ:
• হিতোপদেশ (গোলকনাথ শর্মা, ১৮০২; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ১৮০৮): সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ।
• বত্রিশ সিংহাসন (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ১৮০২): সংস্কৃত কথাসাহিত্যের অনুবাদ।
• রাজাবলি (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ১৮০৮): সংস্কৃত ইতিহাসের অনুবাদ।
• রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (রামরাম বসু, ১৮০১): এটি বাংলা গদ্যের প্রথম মুদ্রিত জীবনচরিত্র, কিন্তু সংস্কৃত শৈলীতে রচিত এবং ঐতিহাসিক উৎসের ভিত্তিতে (মৌলিক বলে বিবেচিত হলেও, সংস্কৃত প্রভাব প্রধান)।
যদিও কিছু গ্রন্থে পণ্ডিতদের নিজস্ব শৈলী প্রকাশ পেয়েছে (যেমন, কথোপকথন বা লিপিমালা), তবুও অধিকাংশই অনুবাদভিত্তিক। এই পর্ব বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতীকরণ করেছে, যা পরবর্তীকালে চলিত ভাষার প্রসারে সাহায্য করেছে।
অন্যান্য অপশনগুলো কেন সঠিক নয় তা বিশ্লেষণ করা হলো:
খ) ফারসি বইয়ের অনুবাদ: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফারসি ভাষার শিক্ষা দেওয়া হলেও বাংলা গদ্যপুস্তকগুলো ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ ছিল না। এগুলো মূলত সংস্কৃত গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত হয়।
গ) ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ: এই পর্বে বাংলা গদ্যে ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদের উদাহরণ তেমন পাওয়া যায় না। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক বিকাশে সংস্কৃত প্রভাবই প্রধান ছিল।
ঘ) পণ্ডিতদের রচিত মৌলিক গ্রন্থ: যদিও কিছু গ্রন্থে পণ্ডিতদের নিজস্ব রচনাশৈলী প্রকাশ পেয়েছে (যেমন, উইলিয়াম কেরির কথোপকথন বা রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র), তবুও এই গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে রচিত। তাই এটিকে সম্পূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ বলা যায় না।
• ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ:
বাংলাদেশে কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য তৎকালীন ইংরেজশাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ঠা মে কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবস হলেও ২৪শে নভেম্বর থেকে কলেজের কাজ শুরু হয়েছিল। ওয়েলেসলি অনুভব করেছিলেন যে কোম্পানির দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে বিলাত থেকে যারা আসে, তারা অধিকাংশ চৌদ্দ থেকে আঠার বৎসরের নাবালক, স্বদেশে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি, এ দেশেও তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়ে এই সিবিলিয়ানদের উপযুক্ত করে তোলার জন্যই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। এই কলেজে ১৮০১ সালে বাংলা বিভাগ প্রবর্তিত হলে অধ্যক্ষ হিসেবে আসেন শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রি এবং বাইবেলের অনুবাদক বাংলায় অভিজ্ঞ উইলিয়াম কেরি। তিনি তাঁর অধীনস্ত দু জন পণ্ডিত এবং ছয় জন সহকারী পণ্ডিতের সহযোগিতায় বাংলা গদ্যে কলেজের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলাফল দিয়েই বাংলা গদ্যের অনুশীলনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা নিরূপণ করা হয়।
ফোর্ট উইলিয়ামের পর্বে ১৮০১ থেকে ১৮১৫ সালের এই সময়ের মধ্যে ৮ জন লেখক ১৩ খানি বাংলা গদ্যপুস্তক লিখেছিলেন:
• কেরি রচিত- কথোপকথন (১৮০১)।
• রামরাম বসু রচিত- ইতিহাসমালা (১৮১২), রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), লিপিমালা (১৮০২)।
• গোলোকনাথ শর্মা রচিত- হিতোপদেশ (১৮০২)।
• মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত- বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলি (১৮০৮), প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩)।
• তারিণীচরণ মিত্র রচিত- ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩)।
• রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত- মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)।
• চণ্ডীচরণ মুর্শী রচিত- তোতা ইতিহাস (১৮০৫)।
• হরপ্রসাদ রায় রচিত- পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)।
উল্লেখ্য,
বাংলা ভাষার সংস্কৃতীকরণ বাংলা গদ্যের সূচনাতেই এর রূপের পরিবর্তন ঘটেছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে যে লেখকগোষ্ঠী গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরাই বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতঘেঁষা করে তোলেন। এতদিন পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় তদ্ভব, আরবি-ফারসি ও দেশজ শব্দমিশ্রিত যে ভাষা প্রচলিত ছিল তা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রভাবে সংস্কৃত শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং গদ্যরীতির মধ্যে কৃত্রিম গাম্ভীর্য আনীত হয়। এমনিভাবে বাংলা গদ্য একটা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।
উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড মাহাবুবুল আলম এবং বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ১৮. সাহিত্যের রূপ ও রীতির বিচারে কোন গ্রন্থটি ব্যতিক্রম?
ক) বাংলা কাব্য খ) দিবারাত্রির কাব্য
গ) শেষের কবিতা ঘ) নদী ও নারী
সঠিক উত্তর: ক) বাংলা কাব্য
Live MCQ Analytics: Right: 51%; Wrong: 23%; Unanswered: 24%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • সাহিত্যের রূপ ও রীতির বিচারে ব্যতিক্রমী গ্রন্থটি হলো — ‘বাংলা কাব্য‘।
কারণ, ‘দিবাবাত্রির কাব্য’ (বিখ্যাত উপন্যাস), ‘শেষের কবিতা’ (উপন্যাস) এবং ‘নদী ও নারী’ (উপন্যাস) – এই তিনটিই গদ্য সাহিত্য বা উপন্যাস।
• ‘দিবারাত্রির কাব্য‘ উপন্যাস:
– ‘দিবারাত্রির কাব্য’ উপন্যাসটির লেখক- ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’।
– উপন্যাসটি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত।
– এর প্রধান চরিত্র- হেরম্ব ও আনন্দ প্রমুখ।
• শেষের কবিতা‘ উপন্যাস:
– ‘শেষের কবিতা’ তাঁর একটি রোমান্টিক- মনস্তাত্ত্বিক কাব্যিক উপন্যাস।
– এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে।
– এটিকে কাব্যোপন্যাসও বলা হয়।
– শেষের কবিতা উপন্যাস বিংশ শতকের বাংলার নবশিক্ষিত অভিজাত সমাজের জীবনকথা।
• “নদী ও নারী” উপন্যাস:
– ‘নদী ও নারী’ হুমায়ুন কবিরের একমাত্র উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম তিনি রচনা করেন ইংরেজিতে Men and Rivers নামে। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। এর সাত বছর পর প্রকাশিত হয় বাংলা উপন্যাসটি (১৯৫২ সালে)।
– ‘নদী ও নারী’ একসময়ের পূর্ববঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশের পদ্মাবিধৌত ফরিদপুর অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষিশ্রমজীবী বাঙালি মুসলমানের জীবনচিত্র। বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের সমাজইতিহাসে উপন্যাসটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।
– এই উপন্যাসে আমরা দেখি নদী ও নারী জীবনকে কতটা গভীরভাবে আলোড়িত করে। উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে লেখক বাঙালি মুসলমানের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনের ভেতর-বাহিরকে চমৎকার নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবন যে শেষপর্যন্ত সার্বক্ষণিক যুদ্ধেরই জীবন এই সত্যই পদ্মার চরাঞ্চলের মানুষের মধ্য দিয়ে লেখক রূপায়িত করেছেন।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ১৯. ‘বিরাট গরু-ছাগলের হাট‘ – ব্যানারে লেখা এই শিরোনামকে অপপ্রয়োগ বলা যায় না কেন?
ক) বিরাট শব্দটি হাটকে বিশেষিত করছে
খ) বিরাট শব্দটি গরু-ছাগলকে বিশেষিত করছে
গ) বিশেষণের অবস্থান যে-কোনো জায়গায় হতে পারে
ঘ) বহুল ব্যবহারে প্রয়োগ-অশুদ্ধতা হারিয়েছে
সঠিক উত্তর: ক) বিরাট শব্দটি হাটকে বিশেষিত করছে
Live MCQ Analytics: Right: 33%; Wrong: 44%; Unanswered: 22%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) বিরাট শব্দটি হাটকে বিশেষিত করছে।
বিস্তারিত ব্যাখ্যা:
ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ:
• “বিরাট” একটি বিশেষণ (adjective) যা পরবর্তী বিশেষ্য (noun) কে বিশেষিত করে।
এখানে, “বিরাট” শব্দটি “হাট” কে বিশেষিত করছে, “গরু-ছাগল” কে নয়। অর্থাৎ, শিরোনামটির প্রকৃত অর্থ হলো— “বিরাট (বৃহৎ) গরু-ছাগলের হাট”।
• গঠনগতভাবে, “গরু-ছাগলের” একটি সম্বন্ধ পদ যা হাটের ধরন বোঝাচ্ছে (গরু-ছাগলের জন্য নির্দিষ্ট হাট)। সঠিক পদক্রম:বিরাট (বিশেষণ) + গরু-ছাগলের (সম্বন্ধ পদ) + হাট (বিশেষ্য)।
অপপ্রয়োগ না হওয়ার কারণ:
বাংলা বাক্যের গঠন অনুযায়ী, বিশেষণ সাধারণত যে বিশেষ্যকে বিশেষিত করে, তার আগে বা কাছাকাছি অবস্থান করে। এখানে ‘বিরাট’ শব্দটি ‘হাট’-এর আকার, পরিমাণ বা গুরুত্বের বর্ণনা দিচ্ছে, যা ব্যাকরণগতভাবে সঠিক এবং অর্থপূর্ণ। তাই এটিকে অপপ্রয়োগ বলা যায় না।
উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
প্রশ্ন ২০. ‘অজর‘ শব্দের বিপরীত কোনটি?
ক) অমলিন খ) বার্ধক্য গ) অমর ঘ) ব্যাধিগ্রস্ত
সঠিক উত্তর: খ) বার্ধক্য
Live MCQ Analytics: Right: 21%; Wrong: 28%; Unanswered: 50%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে,
‘অজর’ শব্দের অর্থ- বার্ধক্যরহিত।
ব্যাখ্যা:
‘অজর’ শব্দের অর্থ — ‘যা জরা বা বৃদ্ধত্ব দ্বারা অস্পৃষ্ট’, অর্থাৎ ‘যে বার্ধক্যজনিত ক্ষয় বা জরায় আক্রান্ত হয় না, অর্থাৎ চিরযৌবনসম্পন্ন’। এর বিপরীত অর্থ হবে এমন কিছু যা বৃদ্ধত্ব বা জরাগ্রস্ততার সঙ্গে সম্পর্কিত। ‘বার্ধক্য’ শব্দটির অর্থ ‘বৃদ্ধাবস্থা’ বা ‘জরা’, যা ‘অজর’-এর সরাসরি বিপরীত।
অপশন বিশ্লেষণ: ক) অমলিন: এর অর্থ ‘নির্মল’ বা ‘পরিষ্কার’। এটি ‘অজর’-এর বিপরীত নয়, বরং ‘মলিন’-এর বিপরীত।
খ) বার্ধক্য: এর অর্থ ‘বৃদ্ধাবস্থা’ বা ‘জরা’। এটি ‘অজর’-এর সরাসরি বিপরীত, কারণ ‘অজর’ হলো জরার অভাব, আর ‘বার্ধক্য’ হলো জরার অবস্থা।
গ) অমর: এর অর্থ ‘যার মৃত্যু নেই’। এটি ‘অজর’-এর সমার্থক বা নিকটবর্তী (যেমন, অমরত্বের ধারণা), কিন্তু বিপরীত নয়। ‘অজর’ বিশেষভাবে বার্ধক্যের ক্ষয়কে নির্দেশ করে, মৃত্যুকে নয়।
ঘ) ব্যাধিগ্রস্ত: এর অর্থ ‘রোগাক্রান্ত’। এটি ‘অজর’-এর বিপরীত নয়, কারণ ‘অজর’ রোগের পরিবর্তে বার্ধক্যের ক্ষয়হীনতাকে বোঝায়।
সুতরাং, সঠিক উত্তর খ) বার্ধক্য।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।
প্রশ্ন ২১. ‘ব্যাং‘ শব্দটি ‘ং‘ দিয়ে লিখতে হবে, কারণ-
ক) এর হসন্ত উচ্চারণ ং হয় খ) ্যা-এর পর ং হয়
গ) ‘ ং’ বাংলা ভাষার নিজস্ব বর্ণ ঘ) ব্যাং একটি একাক্ষর শব্দ
সঠিক উত্তর: ক) এর হসন্ত উচ্চারণ ং হয়
Live MCQ Analytics: Right: 39%; Wrong: 17%; Unanswered: 42%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: ক) ঙ-এর হসন্ত উচ্চারণ ং হয়।
ব্যাখ্যা: ‘ব্যাং’ শব্দটি বাংলা ভাষায় ‘ব্যাঙ’ (ব্যাঙ বা ব্যাঙা, যা ব্যাঙের উচ্চারণ) থেকে এসেছে। বাংলা বর্ণমালায় ‘ঙ’ (অনুনাসিক বর্ণ) যখন হসন্ত (অর্থাৎ, স্বরবর্ণ ছাড়া) ব্যবহৃত হয়, তখন এর উচ্চারণ ‘ং’ (অনুনাসিক ধ্বনি) হিসেবে হয়। ‘ব্যাং’-এ ‘ং’ ব্যবহৃত হয় কারণ এটি ‘ঙ’-এর হসন্ত রূপ, যা শব্দের শেষে অনুনাসিক ধ্বনি প্রকাশ করে।
“ঙ এবং ং” এর উচ্চারণ:
• শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে।
যেমন: গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।
• তবে, অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে ‘ঙ’ হবে।
যেমন: বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।
আবার, বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।
উৎস: বাংলা একাডেমী আধুনিক বাংলা অভিধান; ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ; ‘কতদূর-এগোল-বাংলা-বানান’- তারিক মনজুর।
প্রশ্ন ২২. ‘সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।‘- এই বাক্য কী কারণে ত্রুটিপূর্ণ?
ক) বানান ভুল আছে
খ) বাক্যের পদবিন্যাস যথাযথ নয়
গ) অর্থ অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ হয়নি
ঘ) বিশেষ্য-বিশেষণের অপপ্রয়োগ ঘটেছে
সঠিক উত্তর: গ) অর্থ অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ হয়নি
Live MCQ Analytics: Right: 26%; Wrong: 25%; Unanswered: 47%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • সঠিক উত্তর: গ) অর্থ অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ হয়নি।
• বাক্যটিতে ব্যবহৃত “কৌতূহল” শব্দটি অর্থের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ।
• “কৌতূহল” শব্দের অর্থ হলো কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা বা কুরিয়োসিটি (Curiosity)। এটি সাধারণত কোনো তথ্য, ঘটনা বা রহস্য বোঝার ইচ্ছাকে নির্দেশ করে।
• কিন্তু বাক্যে “কৌতুক করার কৌতূহল” বলতে বোঝানো হয়েছে “রসিকতা করার আগ্রহ”, যা “কৌতূহল” শব্দের প্রকৃত অর্থের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, কোনো কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশের জন্য “আগ্রহ”, “ইচ্ছা” বা “প্রবৃত্তি” শব্দের ব্যবহার যথার্থ।
• সঠিক শব্দপ্রয়োগে বাক্যটি হবে:
“সে কৌতুক করার আগ্রহ সংবরণ করতে পারল না।”
অথবা
“সে কৌতুক করার ইচ্ছা দমন করতে পারল না।”
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
ক) বানান ভুল আছে: “কৌতুক”, “কৌতূহল”, “সংবরণ” শব্দগুলির বানান সঠিক।
খ) বাক্যের পদবিন্যাস যথাযথ নয়: বাক্যের গঠন (কর্তা + ক্রিয়া) ও পদক্রমে কোনো ত্রুটি নেই। যেমন: “সে” (কর্তা), “কৌতুক করার কৌতূহল” (কর্ম), “সংবরণ করতে পারল না” (ক্রিয়া)।
ঘ) বিশেষ্য-বিশেষণের অপপ্রয়োগ ঘটেছে: “কৌতুক করার” বিশেষণটি “কৌতূহল” বিশেষ্যকে বিশেষিত করছে, যা ব্যাকরণগতভাবে গ্রহণযোগ্য। তবে মূল সমস্যা শব্দের অর্থগত অসঙ্গতিতে, বিশেষ্য-বিশেষণের অপপ্রয়োগে নয়।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ ও ২০২২ সংস্করণ); ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; মাধ্যমিক ব্যাকরণ- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।
প্রশ্ন ২৩. ‘নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে‘-এখানে ‘নিত্য‘ শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?
ক) অতিশয় খ) চিরন্তন গ) প্রকৃতি ঘ) অহরহ
সঠিক উত্তর: ঘ) অহরহ
Live MCQ Analytics: Right: 41%; Wrong: 32%; Unanswered: 25%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ‘নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে’—এই পঙ্ক্তিতে ‘নিত্য’ শব্দের অর্থ হলো ‘প্রতিনিয়ত’ বা ‘নিয়মিতভাবে’। এটি এমন কিছু বোঝায় যা ক্রমাগত বা প্রতিদিন ঘটে। প্রতিশব্দ হিসেবে — ‘অহরহ’ (যার অর্থ ‘নিরন্তর’ বা ‘প্রতিনিয়ত’) এখানে সবচেয়ে উপযুক্ত।
• অভিধান অনুসারে,
অন্যান্য অপশনের বিশ্লেষণ:
(ক) অতিশয়: এর অর্থ ‘অত্যন্ত’ বা ‘খুব বেশি’, যা পরিমাণ বা তীব্রতা বোঝায়, নিত্য’র প্রতিশব্দ নয়।
(খ) চিরন্তন: এর অর্থ ‘অনন্তকাল’ বা ‘চিরস্থায়ী’, যা সময়ের স্থায়িত্ব বোঝায়, কিন্তু ‘নিত্য’র মতো নিয়মিত ঘটনার ধারাবাহিকতা বোঝায় না।
(গ) প্রকৃতি: এর অর্থ ‘স্বভাব’ বা ‘নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য’, যা ‘নিত্য’র অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।
প্রশ্ন ২৪. বাক্যের মধ্যে শব্দ অবস্থান করে কীভাবে?
ক) কর্তা ও ক্রিয়ার পদবিন্যাস অনুযায়ী খ) অর্থ ও ভাব অনুযায়ী
গ) বর্গ বা গুচ্ছ আকারে ঘ) স্বাধীন পদের পরিচয় নিয়ে
সঠিক উত্তর: ক) কর্তা ও ক্রিয়ার পদবিন্যাস অনুযায়ী
Live MCQ Analytics: Right: 47%; Wrong: 26%; Unanswered: 25%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) কর্তা ও ক্রিয়ার পদবিন্যাস অনুযায়ী।
বাক্য গঠনের নিয়ম:
বাংলা বাক্যে শব্দের অবস্থান সাধারণত কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV: Subject-Object-Verb) পদবিন্যাস অনুসারে হয়। এটি বাংলা ভাষার বাক্য গঠনের মূল বৈশিষ্ট্য।
উদাহরণস্বরূপ:
“রানা (কর্তা) বই (কর্ম) পড়ে (ক্রিয়া)।” এই পদবিন্যাস বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করতে এবং ব্যাকরণগতভাবে বাক্যটি সঠিক হতে সাহায্য করে। বাংলায় শব্দের অবস্থান নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে, যেখানে কর্তা সাধারণত বাক্যের শুরুতে, কর্ম (যদি থাকে) মাঝে এবং ক্রিয়া শেষে থাকে।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
খ) অর্থ ও ভাব অনুযায়ী:
যদিও বাক্যের অর্থ ও ভাব শব্দ নির্বাচন ও বিন্যাসে প্রভাব ফেলে, তবু শব্দের অবস্থান প্রাথমিকভাবে ব্যাকরণগত পদবিন্যাস (কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থ বা ভাব দ্বারা নয়।
গ) বর্গ বা গুচ্ছ আকারে:
বাংলা বাক্যে শব্দগুচ্ছ (যেমন: বিশেষণ-বিশেষ্য) থাকতে পারে, কিন্তু শব্দের অবস্থান সরাসরি বর্গ বা গুচ্ছের উপর নির্ভর করে না; বরং পদবিন্যাসের নিয়ম এটি নির্ধারণ করে।
ঘ) স্বাধীন পদের পরিচয় নিয়ে:
শব্দের স্বাধীন পদের পরিচয় (যেমন: বিশেষ্য, ক্রিয়া) বাক্যে তাদের ভূমিকা নির্ধারণে সাহায্য করে, কিন্তু অবস্থান নির্ধারিত হয় বাক্যের পদবিন্যাসের নিয়ম অনুসারে।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ ও ২০২২ সংস্করণ); ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; মাধ্যমিক ব্যাকরণ- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ২৫. বাংলা একাডেমির ‘আধুনিক বাংলা অভিধানে‘র সম্পাদক কে?
ক) আনিসুজ্জামান খ) আবু ইসহাক
গ) মনসুর মুসা ঘ) জামিল চৌধুরি
সঠিক উত্তর: ঘ) জামিল চৌধুরি
Live MCQ Analytics: Right: 26%; Wrong: 34%; Unanswered: 38%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ‘বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান’ এর সম্পাদক: ‘জামিল চৌধুরী‘।
অন্য অপশনের লেখকদের প্রণীত অভিধান:
• আমার অভিধান- আনিসুজ্জামান।
• ‘বাংলা একাডেমি সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান‘ এর সম্পাদক- আবু ইসহাক।
• বাংলায় প্রচলিত ইংরেজী শব্দের অভিধান- মনসুর মুসা মনোয়ার ইলিয়াস।
বাংলা একাডেমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিধান:
• ‘বাংলা একাডেমি ঐতিহাসিক অভিধান‘ এর সম্পাদক- মনজুরুর রহমান।
• ‘বাংলা একাডেমি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান‘ এর সম্পাদক- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।
• ‘বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান এর সম্পাদক- আহমদ শরীফ।
• ‘মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান‘ এর সম্পাদক- মোহাম্মদ আবদুল কাইউম।
• বাংলা একাডেমি বাংলা সাহিত্যকোষ‘ এর সম্পাদক- সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং বাংলা একাডেমি ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ২৬. কোন মঙ্গলকাব্যে ঐতিহাসিক চরিত্র আছে?
ক) মনসামঙ্গল খ) চণ্ডীমঙ্গল
গ) অন্নদামঙ্গল ঘ) ধর্মমঙ্গল
সঠিক উত্তর: গ) অন্নদামঙ্গল
Live MCQ Analytics: Right: 18%; Wrong: 51%; Unanswered: 29%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:• সঠিক উত্তর: গ) অন্নদামঙ্গল।
• ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে মানসিংহ এবং ভবানন্দ প্রধান চরিত্র হিসেবে উল্লিখিত। এই দুটি চরিত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত।
যেমন-
মানসিংহ: ঐতিহাসিকভাবে, মানসিংহ ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি, যিনি বাংলায় বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের মানসিংহ-ভবানন্দ খণ্ডে তাঁর কাহিনি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে মিশে বর্ণিত হয়েছে।
ভবানন্দ: ভবানন্দ মজুমদার বর্ধমানের ঐতিহাসিক জমিদার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত একটি চরিত্র, যা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কিছুটা কাল্পনিকভাবে
উপস্থাপিত হলেও ঐতিহাসিক ভিত্তি রাখে।
আবার
অন্নদামঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে মানসিংহের বাংলায় আগমন এবং রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করার প্রেক্ষাপটে ভবানন্দের কাছে বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কাহিনি বর্ণিত হয়, যা ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই কারণে, অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থিতি সুস্পষ্ট।
• ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য সম্পর্কিত কিছু তথ্য:
– নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররে আদেশে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যটি রচনা করেন।
– ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর শ্রেষ্টসৃষ্টি ‘অন্নদামঙ্গল’ (১৭৫২-৫৩ সালে) রচনা করেন।
– ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো ছন্দ ও অলঙ্কারের সুদক্ষ প্রয়োগ।
– সমালোচক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে: ‘অন্নদামঙ্গলকাব্য অষ্টদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্যতম।
– অন্নদামঙ্গল কাব্য ৩টি খণ্ডে বিভক্ত।
যথা: শিবনারায়ণ, কালিকামঙ্গল এবং মানসিংহ-ভবানন্দ খণ্ড।
• এই কাব্যের প্রধান চরিত্র:
– মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যাসুন্দর, মালিনী, ঈশ্বরী পাটনী ইত্যাদি।
• অন্নদামঙ্গল কাব্যের কিছু বিখ্যাত পঙ্ক্তি হলো:
– আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।
– মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
– হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
– নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?
– না রবে প্রাসাদগুণ না হবে রসাল, অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।
– বড়র পিরীতি বালির বাঁধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষনেকে চাঁদ।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
(ক) মনসামঙ্গল: এই কাব্যে দেবী মনসার পূজা এবং চাঁদ সদাগরের কাহিনি বর্ণিত, যা মূলত পৌরাণিক ও কাল্পনিক। এতে স্পষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ নেই।
(খ) চণ্ডীমঙ্গল: এই কাব্যে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য এবং কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনি বর্ণিত, যা পৌরাণিক ও লোককথা-নির্ভর। ঐতিহাসিক চরিত্র এতে উল্লেখযোগ্য নয়।
(ঘ) ধর্মমঙ্গল: ধর্ম ঠাকুরের নামে এই মঙ্গলকাব্য সৃষ্ট হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত – রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প এবং লাউসেনের গল্প।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম এবং বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ২৭. কোন কাব্যে আলাওল ব্যক্তিগত জীবনের কথা লিখেছেন?
ক) পদ্মাবতী খ) হপ্তপয়কর
গ) সিকান্দরনামা ঘ) তোহ্ফা
সঠিক উত্তর: ক) পদ্মাবতী
Live MCQ Analytics: Right: 7%; Wrong: 53%; Unanswered: 38%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: ক) পদ্মাবতী।
• আলাওলের ‘পদ্মাবতী‘ কাব্য এবং ব্যক্তিগত জীবনের রূপায়ণ:
আলাওল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁর ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে — ব্যক্তিগত জীবনের কিছু উল্লেখ করেছেন। এ কাব্যের প্রথম অংশে, আলাওল তাঁর জীবনের দুঃখ, আরাকানে আগমন, হার্মাদের (পর্তুগিজ জলদস্যুদের) সঙ্গে যুদ্ধ এবং রোসাঙ্গে রাজ-আসোয়ার হিসেবে জীবনযাপনের বিবরণ দিয়েছেন। এই অংশটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জীবনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন ঘটায়। ‘পদ্মাবতী’ কাব্যের প্রস্তাবনা ও অন্যান্য অংশে এই ধরনের ব্যক্তিগত উল্লেখ বেশি প্রকাশ পায়, যা তাঁর অন্যান্য কাব্যের তুলনায় স্বতন্ত্র।
• ‘পদ্মাবতী’ কাব্যে আত্মকথায় কবি লিখেছেন –
মুলুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান।
তথাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান।
বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলেমা।
কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা ।
মজলিস কুতুব তথাত অধিপতি। মুই দীন হীন তান অমাত্য সন্ততি ॥ কার্যহেতু যাইতে পন্থে বিধির ঘটন।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন ।
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত। রণক্ষতে ভোগযোগে আইলু এথাত ।
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলু রাজ-আসোয়ার।
বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত। সদাচারী, কুলীন, পণ্ডিত, গুণবন্ত।
সবে কৃপা করন্ত সম্ভাষি বহুতর। তালিম আলিম বলি করন্ত আদর।
‘পদ্মাবতী’ কাব্য সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য:
• পদ্মাবতী কবি আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য। এটি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় প্রণয়কাব্য।
• কাব্যটি প্রখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সির ‘পদুমাবৎ/ পদুমাবত’ কাব্যের অনুবাদ।
• আলাওল ১৬৫১ সালে আরাকান রাজ সাদ থদোমিন্তারের রাজত্বকালে মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে ‘পদ্মাবতী’ কাব্য রচনা করেন।
• কাব্যটিতে — দুইটি পর্ব রয়েছে।
এদের মধ্যে-
প্রথম পর্বে সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য চিতোররাজ রত্নসেনের সফল অভিযান এবং দ্বিতীয় পর্বে রানি পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির ব্যর্থ সামরিক অভিযানের বিবরণ আছে।
• সাহিত্যিক পরিচিতি:
– মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
– ‘পদ্মাবতী’ কবি আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য।
– ‘পদ্মাবতী’ কবি মালিক মুহাম্মদ জয়সীর ‘পদুমাবত’ কাব্যের অনুবাদ।
আলাওল রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ:
– পদ্মাবতী, তোহফা, সপ্তপয়কার, সিকান্দারনামা ইত্যাদি।
উল্লেখ্য,
– আধুনিক যুগের লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬০ সালে পদ্মাবতী নাটক রচনা করেন।
– এটি একটি পৌরাণিক নাটক গ্রিক পুরাণের ‘অ্যাপেল অব ডিসকর্ড’ গল্প অবলম্বনে রচিত।
অন্যান্য অপশন সম্পর্কিত তথ্য:
(খ) হপ্তপয়কর:
– ‘হপ্তপয়কর’ সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো এক সময়ের রচনা। এটি আলাওল রচিত কাব্য।- আরাকান রাজসভায় আলাওল এই কাব্য রচনা করেন। সম্ভবত ১৬৬৫ এর রচনাকাল।
– প্রসিদ্ধ কবি নিজামির পারসি ভাষায় বর্তমান কাব্য রচনা করেন।
– রাজপুত্র বহরাম সাতরাত্রি ধরে তাঁর সাতজন পরির কাছে যে সাতটি গল্প শোনেন তার সংকলন।
– পারসি ও বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
(গ) সিকান্দরনামা:
– এটি ১৬৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।
– এটি নিজামির গ্রন্থের সরল অনুবাদ।
(ঘ) তোহফা:
– এটি একটি ধর্মীয় ও নৈতিক কাব্য।
– ‘তোহফা’ গ্রন্থটি কবি আলাওলের পঞ্চম রচনা। এই কাব্য বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর ‘তোহফাতুন নেসায়েহ্’ নামক ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ।
উৎস: লাল নীল দীপাবলি, হুমায়ুন আজাদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম এবং বাংলাপিডিয়া
প্রশ্ন ২৮. ‘তুরস্ক-ভ্রমণ‘ কার লেখা?
ক) ইসমাইল হোসেন সিরাজী খ) সৈয়দ মুজতবা আলী
গ) আবু জাফর শামসুদ্দীন ঘ) শামসুদ্দীন আবুল কালাম
সঠিক উত্তর: ক) ইসমাইল হোসেন সিরাজী
Live MCQ Analytics: Right: 51%; Wrong: 13%; Unanswered: 34%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: ক) ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
• ‘তুরস্ক ভ্রমণ’ গ্রন্থ পরিচিতি:
‘তুরস্ক ভ্রমণ’ গ্রন্থটি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত একটি ভ্রমণকাহিনি। তিনি ১৯১০ সালে বঙ্গীয় প্রতিনিধি হিসেবে তুরস্ক ভ্রমণ করেন এবং সেই অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এটি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলোর মধ্যে একটি, যা তৎকালীন তুরস্কের সংস্কৃতি, সমাজ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে।
সাহিত্যিক সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
– সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী একাধারে লেখক, বাগ্মী এবং কৃষক নেতা। তিনি ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।
– সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্ম বলেই তিনি তাঁর নামের সঙ্গে ‘সিরাজী’ উপাধি যুক্ত করেন।
– ইসমাইল হোসেন সিরাজী সিরাজগঞ্জে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।
– তিনি জমিদার ও মহাজন বিরোধী আন্দোলনে কৃষকদের সংগঠিত করেন।
– তিনি ১৯৩১ সালের ১৭ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।
তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ:
– অনল প্রবাহ, আকাঙ্ক্ষা, উচ্ছ্বাস, উদ্বোধন, নব উদ্দীপনা, স্পেন বিজয় কাব্য ইত্যাদি।
তাঁর রচিত উপন্যাস:
– রায়নন্দিনী, তারা-বাঈ, ফিরোজা বেগম,নূরুদ্দীন ইত্যাদি।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
(খ) সৈয়দ মুজতবা আলী: তিনি ‘দেশে বিদেশে’ নামে বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনিটি লিখেছেন। কাবুলে অবস্থানের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অন্তরঙ্গ উপলব্ধি নিয়ে লিখিত এই গ্রন্থখানি।
(গ) আবু জাফর শামসুদ্দীন: মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ‘অল্পদর্শী‘ ছদ্মনামে ‘বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা’ শিরোনামে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় কলাম লিখতেন। ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান, পদ্মা মেঘনা যমুনা, সংকর সংকীর্তন – নামক উপন্যাস লিখেছেন।
(ঘ) শামসুদ্দীন আবুল কালাম: শামসুদ্দীনের মুখ্য পরিচয় একজন কথাশিল্পী হিসেবে। তিনি অনেক গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো: গল্পগ্রন্থ অনেক দিনের আশা, ঢেউ, পথ জানা নাই, শাহের বানু, পুঁই ডালিমের কাব্য এবং উপন্যাস আলমনগরের উপকথা, কাশবনের কন্যা, কাঞ্চনমালা, কাঞ্চনগ্রাম।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; “তুরস্ক ভ্রমণ” ভ্রমণকাহিনি এবং বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ২৯. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র ‘চাঁদের অমাবস্যা‘ উপন্যাসে কোন জীবনদর্শনের রূপায়ণ ঘটেছে?
ক) মার্কসবাদ খ) বাস্তববাদ
গ) অস্তিত্ববাদ ঘ) পরাবাস্তববাদ
সঠিক উত্তর: গ) অস্তিত্ববাদ
Live MCQ Analytics: Right: 29%; Wrong: 34%; Unanswered: 35%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) অস্তিত্ববাদ (Existentialism)।
• সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘চাঁদের অমাবস্যা’ এবং অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শন:
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ‘চাঁদের অমাবস্যা’ (১৯৬৪) উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শনের রূপায়ণ ঘটেছে। এই উপন্যাসে লেখক পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দর্শন আত্মস্থ করে ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকট, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, একাকীত্ব এবং জীবনের অর্থহীনতার অনুসন্ধান তুলে ধরেছেন। চেতনাপ্রবাহ শৈলীর মাধ্যমে নায়ক আরেফ আলীর মানসিক যাত্রা এই দর্শনের প্রতিফলন ঘটায়, যেখানে ব্যক্তি সমাজের বাইরে নিজের অস্তিত্বের স্বাধীনতা ও সংকট খুঁজে পান। সমালোচকরা (যেমন: ড. আহমেদ মাওলা) এটিকে অস্তিত্ববাদী উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
মূল বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যসমূহ:
এই উপন্যাসে নায়ক আরেফ আলী, একজন স্কুল মাস্টার, যিনি একটি অপরাধমূলক কাজের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মানসিক দ্বন্দ্ব ও অস্তিত্ব সংকটের মধ্য দিয়ে যান। তাঁর মনোগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মানসিক দ্বন্দ্ব, জীবনের অর্থহীনতা, একাকীত্ব এবং স্বাধীনতার অনুসন্ধান অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল উপাদান। উপন্যাসটি সামন্ত-সমাজ প্রভাবিত গ্রামীণ জীবনের অসঙ্গতি এবং মানুষের অন্তর্জীবনের জটিলতাকেও তুলে ধরে, যা আরেফের চেতনাপ্রবাহ শৈলীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, উপন্যাসটি অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রতিফলন ঘটায়, যেখানে ব্যক্তির অস্তিত্ব, নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রশ্ন উঠে আসে।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
(ক) মার্কসবাদ: উপন্যাসে শ্রেণিবৈষম্যের কিছু ছোঁয়া থাকলেও, এটি মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রামের দর্শনের উপর কেন্দ্রীভূত নয়।
(ক) বাস্তববাদ: চাঁদের অমাবস্যায় মানসিক ও অস্তিত্বগত অনুসন্ধান প্রাধান্য পায়; বাস্তববাদ নয়।
(ক) পরাবাস্তববাদ: উপন্যাসে কিছু পরাবাস্তব উপাদান (যেমন: অদ্ভুত ঘটনা) থাকলেও, মূল দর্শন অস্তিত্ববাদী।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; ‘চাঁদের অমাবস্যা’ উপন্যাস এবং বাংলাপিডিয়া; “চাঁদের অমাবস্যা : অস্তিত্বসংকট ও চেতনাপ্রবাহ- অধ্যাপক ড. আহমেদ মাওলা, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ৩০. ‘প্রভাতফেরির মিছিল যাবে/ ছড়াও ফুলের বন্যা,/ বিষাদগীতি গাইছে পথে/ তিতুমীরের কন্যা।‘ – কার লেখা?
ক) শামসুর রাহমান খ) আল মাহমুদ
গ) আহসান হাবীব ঘ) আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী
সঠিক উত্তর: খ) আল মাহমুদ
Live MCQ Analytics: Right: 21%; Wrong: 19%; Unanswered: 58%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ‘প্রভাতফেরির মিছিল যাবে/ ছড়াও ফুলের বন্যা,/ বিষাদগীতি গাইছে পথে/ তিতুমীরের কন্যা।’ — এই চরণগুলো আল মাহমুদের ‘একুশের কবিতা’ থেকে নেওয়া।
• ‘আল মাহমুদ‘ সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
আল মাহমুদ একজন প্রথিতযশা কবি। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে তিনি এক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিভা। আধুনিক বাংলা কবিতার নগরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটে ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবনপ্রবাহ এবং নরনারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহ তাঁর কবিতার বিশেষ উপাদান।
– তাঁর প্রকৃত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ।
– ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
– স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি ‘দৈনিক গণকণ্ঠ’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।
– তাঁর প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ‘সোনালী কাবিন’ (১৯৭৩)।
• তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ:
– লোক লোকান্তর, সোনালী কাবিন, কালের কলস, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো, আরব্য রজনীর রাজহাঁস, বখতিয়ারের ঘোড়া, প্রেমের কবিতা ইত্যাদি।
• তাঁর রচিত উপন্যাস:
– কাবিলের বোন, উপমহাদেশ, ডাহুকী, কবি ও কোলাহল ইত্যাদি।
• তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ:
– পানকৌড়ির রক্ত, ময়ূরীর মুখ, সৌরভের কাছে পরাজিত।
একুশের কবিতা‘ এর অংশবিশেষ
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায় ?
বরকতের রক্ত।
হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে !
প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।
অন্যান্য অপশন সম্পর্কিত তথ্য:
(ক) শামসুর রাহমান:
• কবি, সাংবাদিক শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর পুরান ঢাকার ৪৬ নম্বর মাহুতটুলীতে জন্মগ্রহণ করেন।
• শামসুর রাহমান বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি হিসেবে খ্যাত।
• ১৯৬০ সালে তাঁর প্রথম কাব্য- “প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে”- এর প্রকাশ কবিতায় তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।
• তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা ‘স্বাধীনতা তুমি’ ও ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা’।
• যুদ্ধকালীন লেখা কবিতাগুচ্ছ মুক্তিযুদ্ধ শেষে ‘বন্দী শিবির থেকে’ নামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।
(গ) আহসান হাবীব:
– তিনি ১৯১৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
– আহসান হাবীব এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম ‘সারাদুপুর’।
– ১৯৬৪ সালে ঢাকা থেকে ‘সারা দুপুর’ প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থটিতে মোট কবিতার সংখ্যা ২৬।
(ঘ) আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী:
– ১৯৩৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর বরিশালে জন্ম গ্রহণ করেন।
– তিনি ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ গানের রচয়িতা হিসেবে পরিচিত।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, একুশে কবিতা।
প্রশ্ন ৩১. ‘হরফের ছড়া‘ কার লেখা বর্ণশিক্ষার বই?
ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ) ফররুখ আহমদ ঘ) বন্দে আলী মিয়া
সঠিক উত্তর: গ) ফররুখ আহমদ
Live MCQ Analytics: Right: 37%; Wrong: 18%; Unanswered: 43%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: গ) ফররুখ আহমদ।
ফররুখ আহমদ:
– ফররুখ আহমদ ১৯১৮ সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার মাঝাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
– তিনি ছিলেন মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি।
– ‘সাত সাগরের মাঝি’ ফররুখ আহমদ রচিত শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।
– ১৯৪৪ সালে কলকাতার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে ‘লাশ’ কবিতা লিখে তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন।
– ফররুখ আহমদ তাঁর বিখ্যাত কাহিনী কাব্য ‘হাতেমতায়ী’ এর জন্য ১৯৬৬ সালে আদমজি পুরস্কার লাভ করেন।
– ১৯৬৬ সালেই ‘পাখির বাসা’ শিশুতোষের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন।
– ‘মুহূর্তের কবিতা’ ফররুখ আহমদ রচিত একটি সনেট সংকলন।
• তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত গ্রন্থ:
– পাখির বাসা, হরফের ছড়া, নতুন লেখা, ছড়ার আসর, চিড়িয়াখানা, কিস্সা কাহিনী, মাহফিল ১ম ও ২য় খণ্ড, ফুলের জলসা।
‘হরফের ছড়া’ গ্রন্থ:
‘হরফের ছড়া’ ফররুখ আহমদের লেখা একটি বর্ণশিক্ষার বই, যা শিশুদের জন্য ছড়ার মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালা শেখানোর উদ্দেশ্যে রচিত। এটি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়।
অন্য অপশন:
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: তিনি ‘বর্ণপরিচয়’ নামে বিখ্যাত বর্ণশিক্ষার বই লিখেছেন। শিশুদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটিই প্রথম।
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘সহজ পাঠ’ নামে শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন।
(ক) বন্দে আলী মিয়া: তিনি একজন কবি ও শিশুসাহিত্যিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে শিশুদের জন্য ছড়া ও কবিতা রয়েছে। যেমন- চোর জামাই, মেঘকুমারী, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, সোনার হরিণ, শিয়াল পন্ডিতের পাঠশালা, কুঁচবরণ কন্যা, সাত রাজ্যের গল্প।
উৎস: ১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা। ২. বাংলাপিডিয়া।
৩. ‘হরফের ছড়া’ রচনা।
প্রশ্ন ৩২. ‘রক্তকরবী‘ নাটকের অন্তর্গত বিষয় কী?
ক) নতুনের জয়গান গাওয়া খ) সামন্তবাদের বিলুপ্তি দেখানো
গ) শ্রমিকদের অপ্রাপ্তি তুলে ধরা
ঘ) পুঁজিবাদের নেতিবাচক প্রভাব দেখানো
সঠিক উত্তর: ঘ) পুঁজিবাদের নেতিবাচক প্রভাব দেখানো
Live MCQ Analytics: Right: 16%; Wrong: 21%; Unanswered: 62%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: ঘ) পুঁজিবাদের নেতিবাচক প্রভাব দেখানো।
অর্থ্যাৎ,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ নাটকটি একটি — সাংকেতিক নাটক, যেখানে পুঁজিবাদের নেতিবাচক প্রভাব এবং এর ফলে মানুষের জীবনের সৌন্দর্য, স্বাভাবিকতা ও মানবিকতার ক্ষয় প্রকাশ পেয়েছে।
• ‘রক্তকরবী‘ নাটকের: সংক্ষিপ্ত কাহিনী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রক্তকরবী’ নাটকে য— ক্ষপুরীর রাজার অর্থলোভ ও প্রজাশোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে। রাজা সোনার খনির কুলিদের মানুষ হিসেবে নয়, শুধুমাত্র উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখেন। এই যান্ত্রিকতায় মানুষের প্রেম, সৌন্দর্য ও মনুষ্যত্ব পীড়িত। নন্দিনী, প্রেম ও জীবনের প্রতীক, যক্ষপুরীর শোষণের বিরুদ্ধে আনন্দের দূত হয়ে আবির্ভূত হন। তিনি সবাইকে মুক্ত জীবনের দিকে আহ্বান করেন। রাজা শক্তির জোরে নন্দিনীকে পেতে চান, কিন্তু প্রেম ও সৌন্দর্য জয় করা যায় না। রঞ্জন, নন্দিনীর প্রেমাস্পদ, যান্ত্রিকতার শিকার হয়ে নিঃশেষিত হয়। তবু নাটক জীবনের প্রাণশক্তির জয় ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে মানবিকতার সামঞ্জস্যের বার্তা দেয়।
• ‘রক্তকরবী‘ নাটক সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
– এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাংকেতিক নাটক। নাটকটি বাংলা ১৩৩০ সনের শিলং-এর শৈলবাসে রচিত।
– তখন এর নামকরণ হয়েছিল যক্ষপুরী।
– ১৩৩০ সনের আশ্বিন মাসে যখন প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় তখন এর নাম হয় রক্তকরবী।
– রক্তকরবীতে ধনের উপর ধান্যের, শক্তির উপর প্রেমের ও মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে।
নাটকটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র:
– নন্দিনী, রঞ্জন।
উল্লেখ্য,
– নাটকে ‘নন্দিনী’ চরিত্রটি নিপীড়িত মানুষের মাঝখানে দেখা দিয়েছে আনন্দের দূত রূপে।
– ‘রঞ্জন’ বিদ্রোহের বাণী বহন করে এনেছে। শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে মানুষের প্রাণশক্তি।
• রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কিছু রূপক-সাংকেতিক নাটক:
– শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্গুনী, গুরু, অরূপরতন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, তাসের দেশ।
উৎস : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; রবীন্দ্র রচনাবলী; ‘রক্তকরবী’ নাটক।
প্রশ্ন ৩৩. মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে কোন তথ্যটি যথার্থ নয়?
ক) তিন খণ্ডে ‘বিষাদ-সিন্ধু’ রচনা করেন
খ) নিজের জীবনী রচনা করেন
গ) জমিদারি দেখাশোনার কাজ করেছেন
ঘ) বিবি কুলসুম তাঁর প্রথম স্ত্রী
সঠিক উত্তর: ঘ) বিবি কুলসুম তাঁর প্রথম স্ত্রী
Live MCQ Analytics: Right: 29%; Wrong: 70%; Unanswered: 0%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: অপশন বিশ্লেষণ:
অপশন — ক) তিন খণ্ডে ‘বিষাদ-সিন্ধু‘ রচনা করেন: এটি সঠিক।
• ‘বিষাদ-সিন্ধু’ উপন্যাস সম্পর্কিত কিছু তথ্য:
– মীর মশাররফ হোসেনের খ্যাতি মূলত এ গ্রন্থটির জন্যেই।
– ‘বিষাদ-সিন্ধু’ (১৮৮৫- ‘৯১) একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস।
– হাসান ও হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ইমাম হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুকাহিনি ‘বিষাদ-সিন্ধু’ গ্রন্থে বর্ণিত মূল বিষয়।
– মূল ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা থাকলেও গ্রন্থটিতে ইতিহাসের অন্ধ অনুসরণ করা হয় নি।
– ‘বিষাদ-সিন্ধু’ উপন্যাসটি — ‘মহরম পর্ব্ব’ (১৮৮৫), ‘উদ্ধার পর্ব্ব’ (১৮৮৭) ও ‘এজিদ-বধ পর্ব্ব’ (১৮৯১) এই — তিনটি পর্বে সম্পন্ন হয়েছে।
– গ্রন্থটি উপক্রমণিকা ও উপসংহারসহ মোট তেষট্টিটি ‘প্রবাহ’ অর্থাৎ অধ্যায় নিয়ে লিখিত।
অপশন — খ) নিজের জীবনী রচনা করেন: এটি সঠিক।
• মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা:
— উদাসীন পথিকের মনের কথা, কুলসুম জীবনী,
— গাজী মিয়াঁর বস্তানী।
• উদাসীন পথিকের মনের কথা:
– ‘উদাসীন পথিক’ এই ছদ্মনামে মীর মশাররফ হোসেন ব্যক্তিগত জীবনের পটভূমিতে স্বীয় পারিবারিক ইতিহাস ও সমসাময়িক বাস্তব ঘটনার চিত্র তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।
– “উদাসীন পথিকের মনের কথা” — (১৮৯০) কে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস বা আত্মজীবনীমূলক রচনা এর কোনোটাই বলা যায় না। বরং বলতে হয়, গ্রন্থটি লেখকের আত্মজীবননির্ভর কতিপয় বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনার মিশেল উপন্যাসসুলভ সাহিত্যিক উপস্থাপনা।
– এতে লেখকের পারিবারিক ইতিবৃত্ত বর্ণনা এবং নিজের মাতা-পিতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত হতে দেখা যায়। উদাসীন পথিকের মনের কথায় হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন-কামনা আছে, তার গভীর তাৎপর্য স্বীকার করতে হয়।
• কুলসুম জীবনী:– কুলসুম জীবনী গ্রন্থটি — ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়।
– লেখক ‘আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী’ নামে অভিহিত করেছেন।
– এটি মীর মশাররফ হোসেনের — দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি কুলসুমকে কেন্দ্র করে লিখিত যা বিবি কুলসুম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।
• গাজী মিয়াঁর বস্তানী:
– ‘গাজী মিয়াঁর বস্তানী’ মীর মশাররফ হোসেনের কর্মজীবন নির্ভর — আত্মজীবনীমূলক রচনা।
– লেখক ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের অন্যায়, অনাচার, সামাজিক দুর্নীতি এবং সেই সমাজভুক্ত মানুষগুলাের নৈতিক অধঃপতন, মনুষ্যত্ব ও হৃদয়হীন আচরণ তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।
– লেখক নিজেকে — ‘ভেড়াকান্ত’ নামে উল্লেখ করেছেন।
– তাছাড়া আলকাতরা সান্যাল, কটা পেস্কার, জয়ঢাক, ছিড়িয়া খাতুন, অরাজকপুর, নচ্ছারপুর, জমদ্বারগ্রাম ইত্যাদি নামচয়নের মধ্যেও লেখকের ব্যঙ্গের তীব্রতা লক্ষ করা যায়।
অপশন — গ) জমিদারি দেখাশোনার কাজ করেছেন: এটি সঠিক।
মীর মশাররফ হোসেন নিজের — পারিবারিক জমিদারি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যা তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো।
অপশন — ঘ) বিবি কুলসুম তাঁর প্রথম স্ত্রী।- তথ্যটি সঠিক নয়।
কুলসুম প্রথম স্ত্রী নন, বরং দ্বিতীয় স্ত্রী। উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম- আজিজননেহার।
• মীর মশাররফ হোসেন ও বিবি কুলসুম : দাম্পত্য জীবনের সংক্ষিপ্তসার
মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম দাম্পত্যজীবন অশান্ত ও অসুখী ছিল। এ সময়ে বারখাদা গ্রামের দরিদ্র কৃষককন্যা বিবি কুলসুমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও প্রেম গড়ে ওঠে এবং ১২৮১ সালের পৌষ মাসে তাঁদের বিয়ে হয়। দ্বিতীয় বিয়েকে আত্মীয়স্বজন ও প্রথমা স্ত্রী মেনে নেননি; ফলে নিন্দা, বিদ্রূপ ও গৃহত্যাগের পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবু কুলসুমের আগমন মশাররফের জীবনে নতুন সুখ, অনুপ্রেরণা ও সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটায়।
তাই বলা চলে, কুলসুম প্রথম স্ত্রী নন, বরং দ্বিতীয় স্ত্রী। উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম- আজিজননেহার।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৩৪. জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর কোন কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়?
ক) ঝরাপালক খ) রূপসী বাংলা
গ) বনলতা সেন ঘ) সাতটি তারার তিমির
সঠিক উত্তর: খ) রূপসী বাংলা
Live MCQ Analytics: Right: 31%; Wrong: 34%; Unanswered: 33%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: খ) রূপসী বাংলা।
• ‘রূপসী বাংলা‘ কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ:
জীবনানন্দ দাশ — ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর —‘রূপসী বাংলা’ —কাব্যগ্রন্থটি —১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি জীবনানন্দের বাংলার প্রকৃতি, গ্রামীণ জীবন ও সৌন্দর্যের প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ, যা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসেবে বিবেচিত। এটি তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর প্রকাশিত হয়েছিল।
• কাব্যগ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য:
– কবিতাগুলির গঠন সনেটের।
– বাংলার গ্রাম-প্রকৃতি, নদীনালা, পশু-পাখি, উৎসব, অনুষ্ঠান কাব্যের বিষয়বস্তু।
– ‘আবার আসিব ফিরে’ রূপসী বাংলা কাব্যের বিখ্যাত কবিতা।
উল্লেখ্য, ‘বেলা অবেলা কালবেলা’ (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থটিও জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
• ‘ঝরা পালক‘ কাব্যগ্রন্থ:
– জীবনানন্দ দাশের কবিতায় গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যময় প্রকৃতি কাব্যময় হয়ে উঠেছে।
– জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- ঝরা পালক।
– কাব্যটি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়।
– এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণ যেমন আছে, তেমনি আছে নতুন এক ভাষারীতি ও বাকপ্রতিমা রচনার চেষ্টা।
• ‘বনলতা সেন‘ কাব্যগ্রন্থ:
– ‘বনলতা সেন’ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা গ্রন্থগুলির অন্যতম।
– ‘বনলতা সেন’ কাব্যগ্রন্থটি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
– এ কাব্যের ‘বনলতা সেন’ কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং জীবনানন্দের কবিতাগুলির মধ্যে জনপ্রিয়।
– ভারতীয় পুরাণের অন্তর্বয়নে যেমন বিদিশা, শ্রাবন্তী উঠে এসেছে, তেমনি বেতের ফলের মতো বা চোখের নীড়ের মতো উপমানগুলো নির্মাণ করেছে নতুন কাব্যমণ্ডল।
– প্রেম ও প্রকৃতি, খণ্ড জীবন ও হতাশা, ক্লান্তি ও অবসাদ, ইতিহাসের বিশাল অনুভূতি ও বর্তমানের ছিন্নভিন্ন অস্তিত্ব সমস্ত কিছুর সমাহার এই অপরূপ কাব্যে আলোছায়ার জাল রচনা করেছে।
• ‘সাতটি তারার তিমির‘ কাব্যগ্রন্থ:
– জীবনানন্দ দাশের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ সাতটি তারার তিমির।
– কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়- ১৯৪৮ সালে।
– আর এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা ‘আকাশনীলা’।
– বইটি উৎসর্গ করা হয়- হুমায়ুন কবিরকে।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৩৫. ‘তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?’ কোন উপন্যাসে আছে?
ক) বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলা’ খ) রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’
গ) শরৎচন্দ্রের ‘চরিত্রহীন’ ঘ) বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’
সঠিক উত্তর: ক) বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলা’
Live MCQ Analytics: Right: 82%; Wrong: 4%; Unanswered: 13%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ‘তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?’- লাইনটি — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের — ‘কপালকুণ্ডলা‘ উপন্যাস থেকে সংকলিত।
• ‘কপালকুণ্ডলা‘ উপন্যাসের অংশবিশেষ:
এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।
ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে – কিন্তু যত বার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম – তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?
• ‘ কপালকুণ্ডলা‘ উপন্যাস সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য:
– বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত — দ্বিতীয় সার্থক উপন্যাস ‘কপালকুণ্ডলা’।- এটি প্রকাশিত হয় — ১৮৬৬ সালে।
– অরণ্যে এক কাপালিক-পালিতা নারী কপালকুণ্ডলাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে।
– বঙ্কিমের জীবৎকালেই এই উপন্যাসের আটটি সংস্করণ হয়।
– উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র: কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক ইত্যাদি।
– ”পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ।” — কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের এই সংলাপ, বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোম্যান্টিক সংলাপ।
অন্য অপশনের বিশ্লেষণ:
• ‘গোরা‘ উপন্যাস:
– গোরা (১৯১০) — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৃহত্তম ও রাজনৈতিক উপন্যাস।
– গোরা উপন্যাসটি ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়।
– ধর্মান্দোলন, স্বদেশপ্রেম, এবং নারীমুক্তি চিন্তার পটভূমিকায় এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছে।
– উপন্যাসটির চরিত্র: গোরা, সুচরিতা, কৃষ্ণদয়াল, আনন্দময়ী।
– উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলো — ‘ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ধর্মের, ধর্মের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ও সমন্বয়’।
• ‘চরিত্রহীন‘ উপন্যাস:
– শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত — ‘চরিত্রহীন’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় — ১৯১৭ সালে।
– প্রথা বহির্ভূত প্রেম ও নারীপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এটি রচিত।
– উপন্যাসের নামকরণ তাই চরিত্রহীন। গল্পটিতে চারটি নারী চরিত্র রয়েছে।
– তার মধ্যে দুটি প্রধান চরিত্র: সাবিত্রী ও কিরণময়ী।
• ‘আরণ্যক‘ উপন্যাস:
– ‘আরণ্যক’ (১৯৩৯) রচনার আগে কর্মসূত্রে বিভূতিভূষণ কিছুকাল ভাগলপুর নিকটবর্তী এক বনাঞ্চলে থাকতেন।
– সেই বনভূমি ও তার সঙ্গে যুক্ত অরণ্যচারী অজস্র মানুষের সংস্পর্শের অভিজ্ঞতাই এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি।
– মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের টানাপোড়েন, বহু বিচিত্র মানুষের চরিত্র, তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, আশা ও আনন্দ এই কাহিনির উপজীব্য।
– উপন্যাসটি ডায়েরিরীতিতে উত্তমপুরুষের জবানিতে রচিত। অরণ্যের সৌন্দর্য ও ভয়ালতা, অরণ্যবাসীর বিশ্বাস ও সংস্কার এবং আর্যসভ্যতা এবং অনার্য সভ্যতার দ্বন্দ্বের এমন তীব্র কাহিনি বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম।
– উল্লেখযোগ্য চরিত্র: ভানুমতী, বনোয়ারী, দোবরু পান্না, বুদ্ধ সিংহ, খাম্বা ইত্যাদি। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; বাংলাপিডিয়া।
English Language and Literature
প্রশ্ন ৩৬. A speech made without any previous thought, preparation or practice is called a/an ______.
ক) free speech খ) extempore speech
গ) maiden speech ঘ) rousing speech
সঠিক উত্তর: খ) extempore speech
Live MCQ Analytics: Right: 56%; Wrong: 23%; Unanswered: 19%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – খ) extempore speech.
• Extempore:
English meaning: done or said without any preparation or thought.
Bangla meaning: পূর্বচিন্তা বা পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া (উক্ত বা রচিত বা কৃত): an extempore speech, উপস্থিত বক্তৃতা।
• An extempore speech (or extemporaneous speech) is a presentation given without a full script or memorization, where the speaker is given a topic on the spot and speaks about it with minimal immediate preparation.
– অর্থাৎ, Extempore speech হলো এমন বক্তৃতা যা হঠাৎ বা তাৎক্ষণিকভাবে, কোনো পূর্বচিন্তা, প্রস্তুতি বা অনুশীলন ছাড়াই দেওয়া হয়।
Other options,
ক) Free speech:
English meaning: the right to express your opinions publicly.
Bangla meaning: বাকস্বাধীনতা।
গ) Maiden speech:
English meaning: the first formal speech made by a British Member of Parliament in the House of Commons or by a member of the House of Lords.
Bangla meaning: পার্লামেন্টে নবাগত সদস্যের প্রথম ভাষণ।
ঘ) Rousing speech:
English meaning: A speech that excites, inspires, or strongly motivates the audience.
Bangla meaning: এমন বক্তৃতা যা মানুষকে উদ্দীপ্ত বা অনুপ্রাণিত করে।
Source: 1. Cambridge Dictionary. 2. Accessible Dictionary.
প্রশ্ন ৩৭. Which one has the identical singular and plural form?
ক) Memorandum খ) Stimulus
গ) Dice ঘ) Oasis
সঠিক উত্তর: গ) Dice
Live MCQ Analytics: Right: 68%; Wrong: 13%; Unanswered: 17%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – গ) Dice.
→ প্রচলিতভাবে singular – die, plural – dice,
– তবে আধুনিক ব্যবহারে dice singular এবং plural দুটো হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।
• Dice/ Die: [singular]
English meaning: a small cube (= object with six equal square sides) with a different number of spots on each side, used in games involving chance.
Bangla meaning: জুয়াখেলার জন্য ফুটকিচিহ্নিত ঘুঁটি; পাশা।
Plural form: Dice, dies.
– মুদ্রা বানানোর ধাতব ছাঁচ অর্থে (plural dies) [ডাইজ্] ব্যবহৃত হয়।
Other options,
ক) Memorandum: [Singular]
English meaning: a short written report prepared specially for a person or group of people that contains information about a particular matter.
Bangla meaning: স্মারক।
Plural form: Memoranda, memorandums.
খ) Stimulus: [Singular]
English Meaning: something that causes growth or activity.
Bangla Meaning: কর্মপ্রেরণাদায়ক বস্তু বা বিষয়; উদ্দীপক, (বৃক্ষ, ফল) কাঁটা, হুল বা তীক্ষ্ণ আঁশ।
Plural form: Stimuli.
ঘ) Oasis: [Singular]
English meaning: a place in a desert where there is water and therefore plants and trees and sometimes a village or town.
Bangla meaning: মরূদ্যান।
Plural form: Oases.
Source: 1. Cambridge Dictionary. 2. Accessible Dictionary.
প্রশ্ন ৩৮. Select the sentence in which ‘fast’ is an adverb:
ক) Don’t drive so fast!
খ) Technology is expanding at a fast pace.
গ) Muslims fast during Ramadan.
ঘ) Ushashi went on a 24-hour fast to detox.
সঠিক উত্তর: ক) Don’t drive so fast!
Live MCQ Analytics: Right: 71%; Wrong: 12%; Unanswered: 15%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – ক) Don’t drive so fast!
– এখানে drive হলো verb.
– fast এই verb কে modify করছে, অর্থাৎ “কত দ্রুত ড্রাইভ করবে”।
– সুতরাং এখানে fast – adverb.
• Adverb:
– যে word একটি verb, adjective, অন্য adverb বা পুরো বাক্যকে modify করে তাকে adverb বলে।
• Fast: [adverb]
English meaning: quickly.
Bangla meaning: দ্রুত; তাড়াতাড়ি।
Example:
– Don’t drive so fast!
– How fast were you going?
Other options,
খ) Technology is expanding at a fast pace.
– এখানে fast হচ্ছে adjective, কারণ এটি pace (noun) কে describe করছে।
– সেক্ষেত্রে “fast” adjective.• Adjective:
– সাধারণত noun বা pronoun এর পূর্বে বসে noun বা pronoun কে modify করে।
Fast: [adjective]
English meaning: moving or happening quickly, or able to move or happen quickly.
Bangla meaning: ক্ষিপ্র; দ্রতগামী।
গ) Muslims fast during Ramadan.
– এখানে fast হলো verb, অর্থাৎ “রোজা রাখা”।
• Fast: [verb]
English meaning: to eat little or no food for a period of time, especially for religious or medical reasons.
Banla meaning: উপবাস করা; রোজা রাখা।
ঘ) Ushashi went on a 24-hour fast to detox.
– এখানে fast হলো noun, অর্থাৎ “রোজা”।
• Fast: [noun]
English meaning: a period during which you do not eat food, especially for religious or health reasons.
Bangla meaning: (১) উপবাস: a fast of three days. (২) উপবাসের দিন বা সময়।
Source: 1. Oxford Dictionary. 2. Cambridge Dictionary.
3. Accessible Dictionary.
প্রশ্ন ৩৯. ‘It was a cowardly attack on a defenceless man.’ Here ‘cowardly’ is a/an ______.
ক) adverb খ) adjective
গ) noun ঘ) conjunction
সঠিক উত্তর: খ) adjective
Live MCQ Analytics: Right: 62%; Wrong: 23%; Unanswered: 13%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • It was a cowardly attack on a defenceless man. Here, ‘cowardly’ is an – Adjective.
– ‘Cowardly’ শব্দটি noun ‘attack’ এর আগে বসে আছে এবং এটিকে বর্ণনা করছে।
– এটি attack এর গুণ বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছে, অর্থাৎ attack কেমন? → cowardly.
– Structure: “a + adjective + noun” = “a cowardly attack”.
• Adjective:
– সাধারণত noun বা pronoun এর পূর্বে বসে noun বা pronoun কে modify করে, তাকে adjective বলে।
– এখানে cowardly শব্দটি “attack” শব্দকে describe করছে।
• Cowardly: [adjective]
– English meaning: not brave; not having the courage to do things that other people do not think are especially difficult.
– Bangla meaning: ভীরু, কাপুরুষোচিত, ভয়প্রবণ।
অন্যদিকে,
• Cowardly (adverb) [old use]
– English Meaning: in a way that shows someone is not at all brave and is too eager to avoid danger, difficulty, or pain:
– Bangla Meaning: (১) ভীরু স্বভাবের। (২) কাপুরুষোচিত।
– যেমন: We will not retreat or act cowardly.
– অর্থাৎ, এটি যখন কোনো verb-কে modify করে তখন adverb হিসেবে কাজ করে।
Source: 1. Oxford Dictionary. 2. Cambridge Dictionary.
প্রশ্ন ৪০. ‘The river flows past the village.’ Here ‘past’ is a/an-
ক) noun খ) verb
গ) adverb ঘ) preposition
সঠিক উত্তর: ঘ) preposition
Live MCQ Analytics: Right: 71%; Wrong: 13%; Unanswered: 14%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • The river flows past the village. Here ‘past’ is a – preposition.
– এই বাক্যে “past” একটি preposition হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
– past এখানে flows কে নির্দেশ করছে যে নদী কোথায় দিয়ে যাচ্ছে → “village-এর পাশ দিয়ে”।
– যেহেতু past এখানে noun phrase (the village) এর আগে বসে অবস্থান নির্দেশ করছে, তাই এটি preposition হবে।
Past: [preposition]
English meaning: on or to the other side of somebody/something.
Bangla meaning: পেরিয়ে; ছাড়িয়ে।
Example:
– We live in the house just past the church.
– He hurried past them without stopping.
– He just walked straight past us!
Source: Oxford Dictionary.
প্রশ্ন ৪১. ‘Ihana sleeps only for four hours a night.’ In this sentence the verb ‘sleeps’ is ______ .
ক) causative খ) intransitive
গ) transitive ঘ) factitive
সঠিক উত্তর: খ) intransitive
Live MCQ Analytics: Right: 58%; Wrong: 16%; Unanswered: 24%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • Ihana sleeps only for four hours a night.’ In this sentence, the verb ‘sleeps’ is – intransitive.
– Intransitive verb সেই verb যা object নেয় না।
– ‘sleeps’ এর পরে কোনো direct object নেই।
– এখানে sleeps verb টির কোনো object প্রয়োজন হয়নি। অর্থাৎ এটি কেবল subject -এর কাজ বোঝাচ্ছে।
– sleeps কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে প্রভাবিত করছে না।
– তাই এটি intransitive verb.
• Intransitive verb:
– যেসকল verb এর object বা কর্ম থাকে না তাকে Intransitive verb বলে।
– সাধারণত Intransitive verb এর পর adverb অথবা preposition ব্যবহৃত হয়।
– বাক্যে ব্যবহৃত Intransitive verb-কে কি (what?) বা কাকে (whom?) দ্বারা প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।
– উল্লেখ্য Intransitive Verb এর ক্ষেত্রে কখন(when) বা কোথায় (where) দ্বারা প্রশ্ন করতে হয়।
– Intransitive verb যুক্ত sentence-এর সাধারণ Structure হচ্ছে: Subject + verb.
Examples:
• They run every morning.
• The cat jumped onto the table.
• The leaves fall in winter.
Other options,
• Causative Verb:
– Subject যখন নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় তখন এই অর্থে causative verb ব্যবহৃত হয়।
– Help, Get, Have, Let, Make ইত্যাদি বহুল প্রচলিত causative verb.
– Make, have, get প্রভৃতি যোগে অনেক verb- কে causative verb এ পরিণত করা যায়।
– যেমন:
– I shall get the work done by him. (আমি তার দ্বারা কাজটি করিয়ে নেব।)
• Transitive verb:
– যে verb এর object আছে তাকে transitive verb বলে৷
– Transitive verbs এর সাধারণ Structure হচ্ছে: subject + verb + object.
– Object সর্বদাই Noun অথবা Pronoun হয়।
– তাই বাক্যে verb এর পরে Noun অথবা Pronoun থাকলে verb টি সাধারণত transitive verb হবে।
– আবার intransitive verb এর শেষে preposition + object যুক্ত করেও তাকে transitive verb এ পরিণত করা যায়।
– যেমন: He writes a letter. write হলো transitive verb, কারণ এর object হলো a letter.
• কিছু Transitive verb এ object এর পাশাপাশি Complement থাকে।
Complement গুলো object কে Describe করে।
→ এই ধরনের Complement কে Objective Complement বলে।
• Factitive Verb:
– যে Verb এর Object বসানোর পরও Objective Complement ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, তাকে Factitive Verb বলে।
– Factitive Verb হলো এমন ক্রিয়া যা দুটি object নেয় – একটি direct object এবং একটি object complement। এই verb direct object কে object complement হিসেবে বর্ণিত অবস্থায় পরিণত করে বা নিয়োগ দেয়।
– কিছু factitive verbs হলো: Elect, Select, Make, Appoint, Call, Name, etc.
– যেমন: The manager appointed him secretary.
– উল্লিখিত বাক্যে secretary হচ্ছে Objective Complement Factitive Object.
– “The manager appointed him” দ্বারা বাক্য সম্পন্ন হচ্ছে না, তাই Objective Complement হিসেবে secretary বসানোর পর বাক্যটি সম্পন্ন হয়েছে।
– যেহেতু Object (him) বসানোর পরও Objective Complement ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়নি তাই এটি Factitive Verb.
Source: Cambridge Dictionary. A Passage to the English Language, S.M. Zakir Hussain. Advanced Learner’s Grammar and Composition by Chowdhury and Hossain.
প্রশ্ন ৪২. ‘He started teaching Hamlet.’ Here ‘teaching’ is a/an-
ক) participle খ) infinitive
গ) verbal noun ঘ) gerund
সঠিক উত্তর: ঘ) gerund
Live MCQ Analytics: Right: 52%; Wrong: 31%; Unanswered: 15%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:• ‘He started teaching Hamlet.’
– Here, ‘teaching’ is a Gerund.
– It is the object of the verb “started” and refers to the activity of teaching.
– প্রদত্ত বাক্যে, teaching (verb+ing)- transitive verb ‘started’ -এর object হিসেবে বসে noun -এর কাজ করেছে তাই এটি gerund.
– অর্থাৎ, ‘teaching’ (শিক্ষকের কাজ) এখানে শেখানোর কাজ (profession) বুঝাচ্ছে।
– এটি participle নয়, কারণ এই বাক্যে এটি কোনো noun/pronoun কে modify করেনি।
– বিশেষ করে এখানে এটি ‘Hamlet’ কে modify কিংবা একে describe করেনি।
• Gerund:
– Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি noun -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও noun -এর কাজ করে, তখন তাকে Gerund বলে।
– সহজে → Gerund = Verb + ing = noun = Verb + noun -এর কাজ করে।
– Gerunds don’t describe action—they act as nouns.
• Functions of the Gerund:
1. As a subject of a verb: Rising early is a good habit.
2. As an object of a verb: I like reading poetry.
3. As an object of a preposition: I am tired of waiting.
4. As a complement of a verb: Seeing is believing.
5. As absolutely (part of a compound noun): This is my writing table.
অন্যদিকে,
• Present participle:
– Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি adjective -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও adjective -এর কাজ করে, তাহলে তাকে present participle বলে।
– সহজ ভাষায় → present participle হলো Verb + ing = adjective = Verb + adjective কাজ করে।
– Present participle দ্বারা চলমান sense বোঝায়।
– যেমন: A rolling Stone gathers no moss.
• Infinitive:
– Infinitive হচ্ছে verb এর base form অথবা to + base form.
– যেমন: teach, to teach.
• Infintive দুই রকম হতে পারে। যেমন:
– To -যুক্ত infinitive এবং
– To -বিহীন infinitive বা Bare Infinitive.
• Verbal Noun:
– কোন বাক্যের Verb + ing – এর পূর্বে the এবং পরে of থাকলে তাকে Verbal Noun বলে।
– The + verb+ing + of = verbal noun.
– যেমন: The writing of a good letter is difficult.
Source:
1. High School English Grammar and Composition by Wren And Martin.
2. A Passage to the English Language by S.M. Zakir Hussain.
প্রশ্ন ৪৩. Fill in the blank with the appropriate preposition: ‘She was married _______ a rich man’.
ক) with খ) to গ) of ঘ) off
সঠিক উত্তর: খ) to
Live MCQ Analytics: Right: 56%; Wrong: 24%; Unanswered: 18%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) to.
• Complete Sentence: She was married to a rich man.
– বাংলা অনুবাদ: সে একজন ধনী ব্যক্তির সাথে বিবাহিত।
• The standard preposition used with “married” is “to” when referring to the person one is married to.
– অর্থাৎ, কার সাথে বিয়ে হয়েছে তা বোঝাতে সঠিক preposition হিসেবে সাধারণত “married to” ব্যবহৃত হয়।
• Marry to
– English Meaning: to become the husband or wife of (someone).
– Bangla Meaning: বিবাহ করা/হওয়া।
অন্যদিকে,
• Marry someone off [phrasal verb ]
– English Meaning: to make certain that someone, especially a female member of your family, gets married, or that she marries the person you have chosen.
– Bangla Meaning: বিয়ে দেওয়া।
– যেমন: She was married off to the local doctor by the age of 16.
– “married off” implies arranging a marriage, but it requires “off” followed by “to” as in “married off to a rich man”.
– অর্থাৎ, কারো সাথে বিয়ে দেওয়া (passive use) বুঝাতে মূলত “Marry off” ব্যবহার করা হয়।
– কিন্তু প্রশ্নে “to” না থাকায় শুধু “Off” ব্যবহারে বাক্যের meaning change হয়ে যায়, তাই “Off” হবে না।
Option Analysis,
ক) “She was married with a rich man” – (Incorrect) “With” is not used with “married” in this context.
• Married With:
– সাধারণত Married With ব্যবহার হয় না।
– তবে কারো সাথে বিবাহিত হওয়া এবং সন্তান থাকা বুঝাতে “married with” ব্যবহার হতে পারে।
– যেমন: She is married with two children.
গ) “She was married of a rich man” – (Incorrect) “Of” is not used with “married.”
– অপশন গ) ভুল কারণ, married এর সাথে “Of” এর ব্যবহার ভুল।
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Cambridge Dictionary.
প্রশ্ন ৪৪. Which gender is the word ‘sibling”?
ক) Masculine খ) Feminine
গ) Neuter ঘ) Common
সঠিক উত্তর: ঘ) Common
Live MCQ Analytics: Right: 82%; Wrong: 5%; Unanswered: 12%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – ঘ) Common.
• Sibling (noun):
– English Meaning: a brother or sister.
– Bangla Meaning: একই মাতাপিতার সন্তান; ভাই বা বোন।
• Common gender:
– Noun টি পুংবাচক বা স্ত্রীবাচক উভয়কেই বুঝালে তা Common Gender হয়।
– যেমন: Parent, Child, Baby, Sibling, Server, Parent, Sheep, Deer, Teacher, Student, Monarch, Neighbor, etc.
• Gender:
যে সকল শব্দ দ্বারা কোন noun or pronoun এর পুরুষ, স্ত্রী বা এদের উভয়টি অথবা কোনটিই নয় বা অবচেতন পদার্থ (ক্লীব) ইত্যাদি বুঝায় তাদেরকে Gender বলে।
• Gender চার প্রকার। যথা:
– Masculine gender (পুং লিঙ্গ),
– Feminine gender (স্ত্রী লিঙ্গ),
– Common/Neutral gender (উভয় লিঙ্গ/লিঙ্গ নিরপেক্ষ),
– Neuter gender (ক্লীব লিঙ্গ).
Source: 1. Cambridge Dictionary.
2. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
প্রশ্ন ৪৫. Find out the correctly spelt word:
ক) reminiscence খ) reminescence
গ) remeniscence ঘ) reminicence
সঠিক উত্তর: ক) reminiscence
Live MCQ Analytics: Right: 56%; Wrong: 20%; Unanswered: 23%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – ক) reminiscence.
• Reminiscence:
English Meaning: the act of remembering events and experiences from the past.
Bangla Meaning: স্মৃতিচারণ, অনুস্মরণ, পূর্বস্মৃতি, স্মৃতিকথা।
• Example of Sentences:
– His reminiscences about the war were painful to hear.
– We wondered whether she could trust her reminiscence of events that happened so long ago.
Source: 1. Accessible Dictionary. 2. Cambridge Dictionary.
প্রশ্ন ৪৬. The idiom ‘smell a rat’ means to _______.
ক) detect bad smell খ) be in a bad mood
গ) suspect something wrong ঘ) see hidden meaning
সঠিক উত্তর: গ) suspect something wrong
Live MCQ Analytics: Right: 77%; Wrong: 6%; Unanswered: 16%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) suspect something wrong.
• Smell a rat
English Meaning: begin to suspect trickery or deception/ to recognize that something is not as it appears to be or that something dishonest is happening.
Bangla Meaning: অন্যায়ের বা অপকর্মের আভাস পাওয়া।
Ex. Sentence: He’s been working late with her every night this week – I smell a rat!
Bangla Meaning: সে এই সপ্তাহে প্রতিদিনই তার সাথে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করছে – আমার সন্দেহ হচ্ছে!
অপশন গুলোর অর্থ –
ক) Detect bad smell:→ দুর্গন্ধ খুঁজে পাওয়া।
খ) Be in a bad mood:→ খারাপ মেজাজে থাকা।
গ) suspect something wrong:→ কোনো কিছু ভুল বা সন্দেহজনক মনে হওয়া।
ঘ) See hidden meaning:→ লুকানো অর্থ বোঝা।
অপশন বিবেচনা করে দেখা যায়, সঠিক উত্তর – গ) suspect something wrong.
Source: 1. Cambridge Dictionary. 2. Live MCQ Lecture.
প্রশ্ন ৪৭. Select the synonym for ‘inclement’:
ক) affable খ) mild গ) rough ঘ) genial
সঠিক উত্তর: গ) rough
Live MCQ Analytics: Right: 24%; Wrong: 7%; Unanswered: 68%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – গ) rough.
• Inclement:
English meaning: Inclement weather is unpleasant, especially with cold wind and rain.
Bangla meaning: (আনুষ্ঠানিক) (আবহাওয়া বা জলবায়ু সম্বন্ধে) কঠোর, রুক্ষ, নির্মম; ঠাণ্ডা ও ঝোড়ো।
Options,
ক) Affable: [adjective]
English meaning: friendly and easy to talk to.
Bangla meaning: শিষ্টাচারী ও বন্ধুভাবাপন্ন; অমায়িক।
খ) Mild: [adjective]
English meaning: not severe or strong.
Bangla meaning: নরম; শান্তপ্রকৃতির; কোমল; মৃদু বা লঘু।
গ) Rough: [adjective]
English meaning: not even or smooth, often because of being in bad condition.
Bangla meaning: অসমতল; এবড়োখেবড়ো; বন্ধুর; অমসৃণ; খসখসে।
ঘ) Genial: [adjective]
English meaning: friendly and cheerful.
Bangla meaning: সদয়; সহানুভূতিশীল; মিশুক।
সাধারণত আবহাওয়া বা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়, যেমন “inclement weather” → তীব্র বা খারাপ আবহাওয়া।
– Inclement শব্দ এর সমার্থক হলো – Rough [যখন আবহাওয়া প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়।]
অপশন বিবেচনা করে দেখা যায়, the synonym for ‘Inclement’ – Rough.
Source: 1. Oxford Dictionary. 2. Cambridge Dictionary.
3. Accessible Dictionary.
প্রশ্ন ৪৮. Tell me frankly why you did this. the underlined part is a/an-
ক) adjective clause খ) noun clause
গ) adverbial clause ঘ) adverbial phrase
সঠিক উত্তর: খ) noun clause
Live MCQ Analytics: Right: 45%; Wrong: 33%; Unanswered: 21%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: Tell me frankly why you did this. The underlined part is – Noun clause.
– এটি বাক্যের মধ্যে object হিসেবে কাজ করছে (tell me what/why/how…), তাই এটি noun clause.
– “why you did this” এখানে verb ‘tell’ এর direct object হিসেবে কাজ করছে।
• Noun clause:
– যে সব subordinate clause noun এর কাজ করে থাকে অর্থাৎ, subject, object, compliment, বা case in apposition- এর কাজ করে থাকে তাদেরকে বলে noun clause.
– Noun clauses are used when a single word isn’t enough.
• একটি বাক্যের যেসব স্থানে Noun clause বসতে পারে –
1. Verb এর subject হিসেবে।
Example: That he has much money is known to all.
2. Verb এর object হিসেবে।
Example: I know that he has done it.
3. Verb এর complement হিসেবে।
Example: This is what I said.
4. Preposition এর object হিসেবে;
Example: I cannot understand the meaning of what he said.
5. Noun/ pronoun – এর apposition হিসেবে।
Example: The fact that he is a thief is clear to all.
Other options, ক) Adjective clause:
– যে sub-ordinate clause কোনো noun/pronoun এর পরে বসে ঐ noun/pronoun কে modify করে তাকে Adjective Clause বলে।
– অর্থাৎ noun এর post modifier হিসাবে adjective clause বসে।
গ) Adverbial clause:
– যে subordinate clause একটি বাক্যে একটি adverb হিসেবে কাজ করে এবং একটি verb,বা একটি adjective-clause বা অন্য একটি adverbial clause-কে modify করে তাকে Adverbial Clause বলে।
– Adverb এর মতো এরা – time, place, cause, effect, purpose ইত্যাদি বুঝায়।
ঘ) Adverbial phrase:
– যে phrase বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে adverb এর মত কাজ করে তাকে Adverbial Phrase বলে ৷
– সাধারণত বাক্যকে কখন ( when), কোথায় ( where), কেন( why) ও কিভাবে (how) দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর হিসেবে যে phrase পাওয়া যায় সেটি Adverbial phrase.
Source:- A Passage to the English Language, S.M. Zakir Hussain. Advanced Learner’s Grammar and Composition by Chowdhury and Hossain.
প্রশ্ন ৪৯. The prefix ‘non’ can be added to ______.
ক) office খ) regular গ) partisan ঘ) obey
সঠিক উত্তর: গ) partisan
Live MCQ Analytics: Right: 69%; Wrong: 11%; Unanswered: 19%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:• The prefix ‘non’ can be added to partisan.
• Prefix:
– Word এর মূল (root) অংশের এর বাম পাশে বা প্রথমে যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয় তাকে Prefix বলে।
– Im-, Un-, -Non, In-, Over-, Dis-, Re- ইত্যাদি Prefix হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
• Nonpartisan (adjective)
– English Meaning: not partisan, especially: free from party affiliation, bias, or designation.
– Bangla Meaning: নির্দলীয়।
• অন্যদিকে,
ক) Office:
– এর সাথে সাধারণত prefix ‘non’ ব্যবহৃত হয় না।
– তবে “Non-office hours” ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু এটি less common.
– Note: office এর adjective form official -এর সাথে prefix হিসেবে ‘non’/’un’ ব্যবহৃত হয়।
– যেমন: nonofficial/unofficial.
খ) Regular
– এর সাথে সাধারণত prefix ‘non’ ব্যবহৃত হয় না।
– তবে Oxford English Dictionary অনুযায়ী non-regular (meaning not regular) ব্যবহৃত হলেও তা common নয়।
– regular -এর সাথে prefix হিসেবে সাধারণত ‘ir’ ব্যবহৃত হয়।
– যেমন: irregular (unregular অপ্রচলিত) – বিধিবিরুদ্ধ; নিয়মবহির্ভূত; অনিয়মিত।
ঘ) Obey
– এর সাথে সাধারণত prefix ‘non’ ব্যবহৃত হয় না।
– obey এর সাথে সঠিক prefix হিসেবে ‘dis’ ব্যবহৃত হয়।
– যেমন: disobey (আদেশ অমান্য করা; কোনো ব্যক্তি বা আইন অগ্রাহ্য করা।).
– সুতরাং, অপশন বিবেচনা করে দেখা যায় যে, খুব common এবং বহুল ব্যবহৃত হিসেব partisan -ই সঠিক উত্তর।
– বিশেষ করে political contexts -এ খুব common word হলো Nonpartisan (নির্দলীয়)।
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.
প্রশ্ন ৫০. Identify the correct passive form: ‘I heard her sing.’
ক) She was heard sing by me.
খ) She was heard to be sung by me.
গ) She was heard sung by me.
ঘ) She was heard to sing by me.
সঠিক উত্তর: ঘ) She was heard to sing by me.
Live MCQ Analytics: Right: 36%; Wrong: 49%; Unanswered: 13%; [Total: 27960]
ব্যাখ্যা: Active: I heard her sing.
Passive: She was heard to sing by me.
• Active voice থেকে passive voice করার নিয়ম:
– Active voice এর object টি passive voice এর subject হয়।
– Tense অনুযায়ী auxiliary verb বসে।
– তারপর মূল verb এর past participle হয়।
– preposition (by, with, at, to, in) বসে।
– Active voice এর subject টি passive voice এর object হয়।
Passive voice-এ perception verbs এর sentence গঠনের নিয়ম:
Active: Subject + verb + object + bare infinitive.
Passive: Object + be + past participle + full infinitive + by + subject.
• Need, bid, dare, see, hear, make, help, feel, let, know, behold, watch প্রভৃতি verb গুলোর পর Active Voice-এ to উহ্য থাকে।
– তবে passive করার সময় তাদের পরে to বসে।
– যখন active sentence এ bare infinitive (to ছাড়া infinitive) থাকে, passive এ সেটি full infinitive (to সহ) হয়ে যায়।
অন্যান্য অপশন ভুল কারণ:
ক) She was heard sing by me.
→ এখানে “to” বাদ দেওয়া হয়েছে।
– Passive voice-এ bare infinitive (sing) আর থাকে না, বরং to + infinitive (to sing) হয়।
– তাই এটি ব্যাকরণগতভাবে ভুল।
খ) She was heard to be sung by me.
→ ভুল, কারণ এখানে to be sung passive infinitive ব্যবহার করা হয়েছে। মূল বাক্যের অর্থ পাল্টে যাচ্ছে।
গ) She was heard sung by me.
→ grammatically ভুল, sung past participle, যা এখানে উপযুক্ত নয়।
– তাছাড়া এটি অর্থগত ভাবে ঠিক হয়নি।
Source: Advancer Learner’s HSC Communicative English by Chowdhury & Hussain.
প্রশ্ন ৫১. Which sentence is correct?
ক) One of my sisters are a nurse.
খ) One of my sister is a nurse.
গ) One of my sisters is a nurse.
ঘ) One of my sister’s are a nurse.
সঠিক উত্তর: গ) One of my sisters is a nurse.
Live MCQ Analytics: Right: 80%; Wrong: 7%; Unanswered: 12%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • Correct sentence: One of my sisters is a nurse.
– আমার বোনদের মধ্যে একজন হলো নার্স।
• Subject-verb agreement অনুসারে,
– One of এর পরে plural noun + singular verb বসে।
– কারণ “one of” মানে হলো “অনেকের মধ্যে একজন”।
– অর্থাৎ, এই বাক্যের subject হলো “One” (singular) not “sisters”.
– “of my sisters” is a prepositional phrase that modifies “one”, এই phrase টি verb এর উপর কোনো প্রভাব ফেলে না।
– প্রদত্ত বাক্যে One of এর পরে plural noun ‘sisters’ আছে এবং এর পরে singular verb ‘is’ বসেছে।
– সুতরাং, subject-verb agreement অনুসারে সঠিক বাক্যটি হলো- One of my sisters is a nurse.
• Other options:
ক) One of my sisters are a nurse.
– ভুল, কারণ verb হিসেবে “are” নয়, “is” ব্যবহার করতে হবে।
খ) One of my sister is a nurse.
– ভুল, কারণ “sister” হলো singular noun, কিন্তু নিয়মানুযায়ী plural noun ‘sisters’ হবে।
ঘ) One of my sister’s are a nurse.
– possessive form “sister’s” use করা হয়েছে যা ভুল,এবং verb হিসেবে “are” ব্যবহার করা হয়েছে যা grammatically ভুল।
Source: A Passage to the English Language, S.M. Zakir Hussain.
প্রশ্ন ৫২. Select the right determiner: ‘She works as ______ FBI analyst.’
ক) a খ) an
গ) the ঘ) none of the above
সঠিক উত্তর: খ) an
Live MCQ Analytics: Right: 72%; Wrong: 13%; Unanswered: 14%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) an.
• Article:
– Articles মূলত Noun, Pronoun এর আগে বসে তাদের সংখ্যা এবং নির্দিষ্টতা, অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে।
– Articles কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করে যায়।
• Indefinite Articles: A, An-এরা Indefinite Article. (এরা নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা কোনো বিষয়কে নির্দেশ করে না)।
• Definite Articles: The হলো Definite Article (এটি কোনো বিশেষ ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়কে নির্দিষ্টভাবে বোঝাতে বা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে)।
• Article এর ব্যবহার সাধারণত pronunciation বা উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল।
– কোনো word এর শুরুতে যদি consonant letter থাকে তবে তার পূর্বে article হিসেবে a বসে।
– কিন্তু Consonant এর উচ্চারণ vowel এর মত হলে a না হয়ে an হবে। যেমন: an FBI.
– শব্দটি হলো FBI, যেটি উচ্চারণে শুরু হয় ‘a’ vowel sound দিয়ে শুরু।
– ইংরেজিতে vowel sound দিয়ে শুরু হওয়া শব্দের আগে “an” ব্যবহার করা হয়।
Complete sentence: She works as an FBI analyst.
Source: Advanced Learner’s Communicative English Grammar & Composition By Chowdhury & Hossain.
প্রশ্ন ৫৩. ‘We met Medha carrying a bouquet of red roses.’ Here ‘carrying’ is a/an ______.
ক) gerund খ) infinitive
গ) verbal noun ঘ) participle
সঠিক উত্তর: ঘ) participle
Live MCQ Analytics: Right: 54%; Wrong: 25%; Unanswered: 20%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
• ‘We met Medha carrying a bouquet of red roses.’
– Here, ‘carrying’ is a participle.
– Here, “carrying” functions as a present participle (adjective) that modifies the noun “Medha”.
– It describes the action that Medha was performing at the time of the meeting.
– অর্থাৎ, verb+ing যখন noun/pronoun কে modify করে তখন তা adjective হিসেবে কাজ করে।
– এখানে বলা হয়েছে Medha -এর সাথে দেখা হওয়ার সময় সে ‘a bouquet of red roses’ carry (বহন করার কাজ) করতেছিল।
• Participle:
– A participle is a verb that ends in -ing (present participle) or -ed, -d, -t, -en, -n (past participle).
– Participles may function as adjectives, describing or modifying nouns/pronouns.
– Participle একই সাথে Verb ও Adjective এর কাজ করে।
• Participle মূলত তিন প্রকার। যথা:
1. Present participle:
– Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি adjective -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও adjective -এর কাজ করে, তাহলে তাকে present participle বলে।
– সহজ ভাষায় → present participle হলো Verb + ing = adjective = Verb + adjective কাজ করে।
– Present participle দ্বারা চলমান sense বোঝায়।
– যেমন: I saw a flying bird.
2. Past participle:
– সাধারণত verb এর সাথে -ed যোগ করে তৈরি হয় (যেমন: played, walked), তবে অপ্রচলিত verb এর আলাদা রূপ থাকে (যেমন: eaten, driven, seen)।
– এটি perfect tense এবং passive voice তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, এবং adjective হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।
– যেমন: The broken window needs fixing.
3. Perfect participle:
– এটি having + past participle দ্বারা তৈরি হয় (যেমন: having eaten, having seen)। এটি এমন বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যে, একটি কাজ অন্য কাজের আগে সম্পন্ন হয়েছিল।
– যেমন: Having finished the work, he left.
অন্যদিকে,
• Gerund:
– Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি noun -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও noun -এর কাজ করে, তখন তাকে Gerund বলে।
– সহজে → Gerund = Verb + ing = noun = Verb + noun -এর কাজ করে।
– Gerunds don’t describe action—they act as nouns.
– যেমন: I like reading.
• Infinitive:
– Infinitive হচ্ছে verb এর base form অথবা to + base form.
– যেমন: carry, to carry.
• Infintive দুই রকম হতে পারে। যেমন:
– To -যুক্ত infinitive এবং
– To -বিহীন infinitive বা Bare Infinitive.
• Verbal Noun:
– কোন বাক্যের Verb + ing – এর পূর্বে the এবং পরে of থাকলে তাকে Verbal Noun বলে।
– The + verb+ing + of = verbal noun.
– যেমন: The writing of a good letter is difficult.
Source: 1. High School English Grammar and Composition by Wren And Martin. 2. A Passage to the English Language by S.M. Zakir Hussain.
প্রশ্ন ৫৪. ‘Five years have passed since his father died’. Identify the correct simple form of the sentence from the following options:
ক) His father has died five years ago.
খ) His father died five years ago.
গ) His father has died for five years.
ঘ) His father died since five years.
সঠিক উত্তর: খ) His father died five years ago.
Live MCQ Analytics: Right: 57%; Wrong: 25%; Unanswered: 16%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:– Complex: Five years have passed since his father died.
– Simple: His father died five years ago.
• প্রদত্ত বাক্যটি একটি Complex sentence.
– কারণ sentence টিতে একটি independent clause “Five years have passed” এবং একটি Subordinate clause “since his father died” আছে।
– এটিকে Simple sentence -এ পরিবর্তন করতে হলে, একটি subject এবং Finite verb যুক্ত sentence -এ রূপান্তর করতে হবে এবং বাক্যের অর্থ ঠিক রাখতে হবে।
– কারণ সাধারণত একটি clause-এর মধ্যে একটি subject এবং একটি finite verb নিয়ে simple sentence গঠিত হয়।
• Option Analysis:
ক) “His father has died five years ago.”
– এটি ভুল, কারণ Present perfect tense (“has died”) cannot be used with a specific past time reference like “five years ago.”
খ) “His father died five years ago.”
– এই বাক্যটি correct simple form, কারণ এই বাক্যে past time expression “five years ago” -এর সাথে সঠিকভাবে simple past tense ব্যবহার হয়েছে, যা original sentence এর same meaning বহন করে।
গ) “His father has died for five years.”
– এটি ভুল, কারণ The verb “die” is a momentary action (not continuous), আর duration (“for five years”) এর সাথে “has died” ব্যবহার করা যায় না।
– এর বদলে “His father has been dead for five years.” ব্যবহার করা যায় কিন্তু তখন অর্থ বদলে যাবে।
ঘ) “His father died since five years.”
– এটি correct simple sentence নয়, কারণ “Since” requires present perfect tense, and “since five years” is grammatically wrong (should be “since five years ago”).
– সুতরাং, প্রদত্ত অপশন অনুযায়ী দেখা যায় যে, correct simple sentence টি হলো- খ) His father died five years ago.
প্রশ্ন ৫৫. Choose the antonym of ‘controversy’:
ক) contention খ) bickering
গ) unanimity ঘ) dispute
সঠিক উত্তর: গ) unanimity
Live MCQ Analytics: Right: 49%; Wrong: 15%; Unanswered: 34%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • The antonym of ‘controversy’ is – unanimity.
• Controversy (noun)
– English Meaning: a discussion marked especially by the expression of opposing views: dispute; a disagreement, quarrel, strife.
– Bangla Meaning: বিতর্ক; বিরোধ; মতান্তর; কোনো সামাজিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী বাদানুবাদ।
• Given options:
ক) Contention
– English Meaning: a point advanced or maintained in a debate or argument.
– Bangla Meaning: তর্ক; যুক্তিপ্রদর্শন; কলহ।
খ) Bickering
– English Meaning: petty and petulant quarreling especially when prolonged or habitual.
– Bangla Meaning: খুঁটিনাটি বা গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা
গ) Unanimity
– English Meaning: agreement by all people involved; consensus; the quality or state of being unanimous.
– Bangla Meaning: ঐকমত্য; মতৈক্য।
ঘ) Dispute
– English Meaning: to engage in argument: debate.
– Bangla Meaning: বিতর্ক; বিরোধ; যুক্তি।
• সুতরাং, অপশনের অর্থ বিবেচনা করে দেখা যায় যে, The antonym of ‘controversy’ is – unanimity.
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.
প্রশ্ন ৫৬. ‘For God’s sake hold your tongue, and let me love.’ This line is taken from the poem ______.
ক) To His Coy Mistress খ) The Canonization
গ) The Definition of Love ঘ) The Sun Rising
সঠিক উত্তর: খ) The Canonization
Live MCQ Analytics: Right: 57%; Wrong: 19%; Unanswered: 23%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ‘For God’s sake hold your tongue and let me love’ এই লাইনটি John Donne এর লেখা বিখ্যাত কবিতা “The Canonization” থেকে নেওয়া হয়েছে।
• The Canonization:
– এটি John Donne লিখিত একটি কবিতা।
– এটি 1590 সালে লিখিত ও 1633 সালে প্রকাশিত হয়।
– এটি Songs and Sonnets এর প্রথম edition এ প্রকাশিত।
– The poem’s speaker uses religious terms to attempt to prove that his love affair is an elevated bond that approaches saintliness.
Famous Quotation from Canonization:
• “For God’s sake hold your tongue, and let me love”
• “As well a well-wrought urn becomes
The greatest ashes, as half-acre tombs.”
John Donne:
– John Donne (1572-1631) Renaissance যুগের একজন কবি।
– Metaphysical poetry এর জনক বলা হয় John Donne কে।
– তিনি আধ্যাত্বিক কবিতার সূচনা করেছিলেন তাই তাকে Father of Metaphysical poetry বলা হয়।
– এছাড়াও তিনি Poet of Love and Religious হিসেবেও পরিচিত।
• তাঁর বিখ্যাত কিছু কবিতা হচ্ছে:
– Good Morrow,
– The Canonization,
– The Flea,
– The Sun Rising,
– A Valediction: Forbidding Mourning.
Source: Britannica.
প্রশ্ন ৫৭. The one-act play ‘Riders to the Sea’ was written by ______.
ক) G. B. Shaw খ) Oscar Wilde
গ) J. M. Synge ঘ) John Galsworthy
সঠিক উত্তর: গ) J. M. Synge
Live MCQ Analytics: Right: 43%; Wrong: 18%; Unanswered: 38%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • Riders to the Sea:
– এটি ইংরেজি সাহিত্যর একটি পরিচিত নাটক, যা Irish নাট্যকার John Millington Synge রচনা করেছেন।
– ১৯০৩ সালে এই play টি প্রকাশিত হয়।
– Riders to the Sea is set in the Aran Islands off the west coast of Ireland and is based on a tale Synge heard there.
– It won critical acclaim as one of dramatic literature’s greatest one-act plays.
– Riders to the Sea is set in the Aran Islands off the west coast of Ireland.
– Synge মুলত আরান দ্বীপপুঞ্জে শোনা একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে তার এই play টি রচনা করেছিলেন।
• Maurya নামক একজন বৃদ্ধ মহিলার জীবনের কঠিন দুঃখ -দুর্দশা এবং বেদনার চিত্র বর্ণিত হয়েছে এই নাটকে , যিনি তার ছোট ছেলে Bartley ছাড়া, পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যদের কে সাগরের ঝড়ের মাঝে বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে ফেলেছেন.
– কিন্তু শেষ সময়ে দেখা যায় তার ছোট ছেলেটিও সাগরে ডুবেই মারা যায়।
– এই Maurya চরিত্রটিকে সাহিত্য জগতের অন্যতম most ill- fated character হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
• John Millington Synge
– তিনি ছিলেন আইরিশ সাহিত্যের নবজাগরণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, মহান একজন কাব্যিক নাট্যকার যিনি আরান দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম আইরিশ সমুদ্র তীরের কঠোর গ্রামীণ অবস্থাকে পরিশীলিত কারুকার্যের সাথে চিত্রিত করেছেন।
– প্রথমে তিনি একজন ‘musician’ হবার ইচ্ছা করলেও 1894 সালে তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ হওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং এর পরিবর্তে English Literature এ মনোনিবেশ করেন।
• Notable works:
– In the Shadow of the Glen, Riders to the Sea, The Well of the Saints, The Tinker’s Wedding, The Playboy of the Western World, Deirdre of the Sorrows.
Source: An ABC of English Literature – Dr M Mofizar Rahman and Britannica.
প্রশ্ন ৫৮. ‘Neither a borrower nor a lender be,
For loan oft loses both itself and friend.’
This extract is taken from Shakespeare’s play _______ .
ক) Macbeth খ) King Lear
গ) Measure for Measure ঘ) Hamlet
সঠিক উত্তর: ঘ) Hamlet
Live MCQ Analytics: Right: 47%; Wrong: 22%; Unanswered: 30%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
Neither a borrower nor a lender be; For loan oft loses both itself and friend.
– এই উক্তিটি নেওয়া হয়েছে William Shakespeare-এর Hamlet নাটক থেকে।
– Polonius, Laertes কে উপদেশ দিচ্ছেন।
– অর্থ: ঋণ নেওয়া বা দেওয়া উভয়ই ঝুঁকিপূর্ণ; ঋণ বন্ধু এবং অর্থ দুটোই হারাতে পারে।
• Hamlet:
– William Shakespeare রচিত tragedy গুলোর মধ্যে Hamlet is one of the most celebrated tragedies in English literature.
– 5acts বিশিষ্ট এই tragedy টি ১৫৯৯-১৬০১ সালের মধ্যে লেখা এবং প্রকাশিত হয় ১৬০৩ সালে।
– Hamlet in Shakespeare’s Hamlet is a prince of Denmark.
– হ্যামলেট জার্মানি থেকে নিজ দেশে ফিরে আসে তাঁর বাবার শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করতে এবং জানতে পারে যে তার চাচা Claudius তার মা Gertrude কে বিয়ে করেছে এবং এই চাচাই তার বাবার খুনী।
– এরপর দেখা যায় প্রিন্স হ্যামলেট তার বাবার খুনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন এবং বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে tragedy এর কাহিনি সামনে এগিয়ে যায়।
– এই নাটকে antagonist অর্থাৎ ভিলেন হিসেবে দেখানো হয়েছে Claudius কে।
– শেষাংশে Hamlet এর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে।
• Famous quotations of Hamlet:
– Neither a borrower nor a lender be; For loan oft loses both itself and friend.
– To be or not to be that is the question.
– Frailty, thy name is woman.
– Brevity is the soul of wit.
– Listen to many, speak to a few.
– Though this be madness, yet there is method in’t.
– Conscience doth make cowards of us all.
– ‘There is divinity that shapes our end’.
• William Shakespeare:
– তার জন্মস্থান Stratford Avon.
– তিনি একাধারে একজন English poet, dramatist এবং actor.
– তাকে English national poet বলা হয়।
– তাকে ‘Bard of Avon’ বলা হয়।
– He is considered by many to be the greatest dramatist of all time.
• Notable works:
• Tragedy:
– Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Julius Caesar.
• Comedy:
– As You Like It, The Tempest, Twelfth Night, A Midsummer Night’s Dream etc.
• Famous poem:
– Shall I Compare Thee to a Summer Day/Sonnet 18,
– The Rape of Lucrece,
– Venus and Adonis.
Source: Britannica and An ABC of English Literature by Dr M Mofizar Rahman.
প্রশ্ন ৫৯. Who composed the elegiac poem ‘Thyrsis’?
ক) Thomas Gray খ) Matthew Arnold
গ) John Milton ঘ) P. B. Shelley
সঠিক উত্তর: খ) Matthew Arnold
Live MCQ Analytics: Right: 38%; Wrong: 14%; Unanswered: 47%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • The composer of the elegiac poem ‘Thyrsis’ is Matthew Arnold.
• Thyrsis:
– Matthew Arnold -এর লিখা “Thyrsis” হলো একটি elegy কবিতা।
– এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে ম্যাকমিলান’স ম্যাগাজিনে।পরবর্তীতে ১৮৬৭ সালে এটি আর্নল্ডের New Poems -এ অন্তর্ভুক্ত হয়।
– এটি Arnold -এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসেবে বিবেচিত।
– “Thyrsis” কবিতায় আর্নল্ড এক জটিল দশ-পঙ্ক্তির স্তবক ছন্দে দক্ষতা দেখিয়েছেন।
– ২৪ পঙ্ক্তির এই কবিতাটি Arnold তার বন্ধু ও কবি Arthur Hugh Clough এর প্রশংসা করে লিখেন, যিনি ১৮৬১ সালে মারা যান।
– কবিতায় Arnold, Clough-কে উপস্থাপন করেছেন “Thyrsis” রূপে—যা প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে রাখাল-কবির নাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
– সমৃদ্ধ pastoral (গ্রামীণ/রাখালজীবনের) চিত্রকল্পের মাধ্যমে আর্নল্ড স্মরণ করেছেন অক্সফোর্ডের সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেখানে তারা দুজন ছাত্রজীবনে (১৮৪০-এর দশকে) একসাথে ঘুরে বেড়াতেন। একইসঙ্গে তিনি ফিরে দেখেছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসার পর তাঁদের তরুণ বয়সের আদর্শগুলোর পরিণতি।
• Matthew Arnold (1822-1888):
– তিনি একজন বিখ্যাত English Victorian poet এবং literary ও social critic.
– তিনি সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির রুচি ও আচরণের সমালোচনার জন্য পরিচিত।
– তিনি শুরুতে inspector of schools হিসেবে কাজ করেন, পরে তিনি professor of poetry হিসেবে যোগ দান করেন Oxford -এ।
– তিনি সংস্কৃতির একজন প্রচারক হিসেবে খ্যাত, বিশেষ করে তাঁর বিখ্যাত criticism রচনা Culture and Anarchy (1869)-এর জন্য।
– Matthew was the eldest son of the renowned Thomas Arnold.
• Notable Works:
• Famous elegies:
– Thyrsis,
– Rugby Chapel.
• Famous poems:
– Dover Beach, The scholar gypsy (lyric poem), Sohrab and Rustom, The Forsaken Merman, Empedocles on Etna, Cromwell.
• Famous books:
– Culture and Anarchy, The Study of Poetry, Literature and Dogma, Essays in Criticism, On Translating Homer (lectures), On the Study of Celtic Literature (lectures), etc.
Source: Britannica.
প্রশ্ন ৬০. Who is the writer of the famous essay ‘Tradition and the Individual Talent’?
ক) George Orwell খ) Aldous Leonard Huxley
গ) T. S. Eliot ঘ) Francis Bacon
সঠিক উত্তর: গ) T. S. Eliot
Live MCQ Analytics: Right: 12%; Wrong: 18%; Unanswered: 68%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • T. S. Eliot is the writer of the famous essay ‘Tradition and the Individual Talent’.
• Tradition and the Individual Talent:
– টি.এস. এলিয়টের সমালোচনামূলক প্রবন্ধের বই “The Sacred Wood”, যা ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে, এলিয়ট সেই সময়ের আধুনিকতাবাদী লেখার বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।
– ‘Tradition and the Individual Talent’ হলো এই সংকলনের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রবন্ধ, যা এলিয়টের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের তত্ত্বকে উপস্থাপন করে।
– এতে হোমার থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্য এবং সেই ঐতিহ্যের সাথে প্রত্যেক Individual Talent -এর সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেন।
– Tradition বা ঐতিহ্য বলতে কেবল অতীতের কবিদের কাজ অনুকরণ করা বোঝায় না। বরং তিনি বলেন— “novelty is better than repetition”.
– এই সম্পর্কে এলিয়ট বলেন, একজন কবির সৃষ্টিকে বোঝার জন্য কেবল তার ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়, পুরো সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে বিবেচনা করতে হবে।
– আর Individual Talent বা ব্যক্তিগত প্রতিভা বলতে বুঝানো হয়েছে কবির কাজ হলো নিজের আবেগকে সরাসরি ব্যক্ত করা নয়, বরং তা শিল্পে রূপান্তর করা।
• মূল বক্তব্য:
– কবি কেবল নিজের অনুভূতির কণ্ঠস্বর নন, তিনি সমগ্র ঐতিহ্যের অংশ।
– কবিতার মূল্য নির্ভর করে তার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত প্রতিভার সমন্বয়ের উপর।
– কবিতায় ঐতিহ্য মানে পুরোনো কিছুকে হুবহু নকল করা নয়, বরং অতীতকে আত্মস্থ করে তার ভেতর থেকে নতুন সৃজনশীলতা বের করে আনা।
– উল্লেখ্য যে, এই সংকলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো “Hamlet and His Problems” যেখানে এলিয়ট তার “objective correlative” তত্ত্ব প্রকাশ করেন, এই শব্দটি তিনি George Santayana or Washington Allston -এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।
• T. S. Eliot (1888-1965):
– তার পুরো নাম Thomas Stearns Eliot.
– T.S. Eliot ছিলেন একজন প্রখ্যাত আমেরিকান কবি, নাট্যকার, এবং সাহিত্য সমালোচক, যিনি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অভিনব রচনা এবং গুরত্বপূর্ণ চিন্তাধারার জন্য পরিচিত।
– Eliot -কে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিবেচেনা করা হয়।
– তিনি ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
– তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জনকারী একজন কবি, যিনি আধুনিক কবিতার ধারায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।
• His famous plays:
– Murder in the Cathedral, The Cocktail Party, The Confidential Clerk, The Family Reunion, The Elder Statesman, Sweeney Agonistes (a poetic drama in two scenes), etc.
• Poems:
– The Love Song of J. Alfred Prufrock (dramatic monologue), The Waste Land, Ash Wednesday, Four Quartets, East Coker, Little Gidding, Burnt Norton, The Dry Salvages, etc.
• The Sacred Wood (Collection of Essays):
– T. S. Eliot এর The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism (১৯২০) হলো তাঁর প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ। এখানে প্রায় ২০টি প্রবন্ধ আছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হলো-
– The Perfect Critic,
– Imperfect Critics,
– Tradition and the Individual Talent,
– Hamlet and His Problems,
– The Possibility of a Poetic Drama,
– Rhetoric and Poetic Drama,
– Notes on the Blank Verse of Christopher Marlowe, etc.
Source: Britannica.
প্রশ্ন ৬১. ‘Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.’ -This oft-quoted line occurs in Shelley’s notable poem _____ .
ক) To a Skylark খ) Ode to the West Wind
গ) Adonais ঘ) The Cloud
সঠিক উত্তর: ক) To a Skylark
Live MCQ Analytics: Right: 33%; Wrong: 33%; Unanswered: 33%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • “Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.” – এই বিখ্যাত লাইনটি P.B. Shelley-এর “To a Skylark” কবিতা থেকে এসেছে।
– কবি Skylark-কে আনন্দ, স্বাধীনতা ও স্বর্গীয় সঙ্গীতের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।
– তিনি বলেন, মানুষের গানগুলো প্রায়ই দুঃখভরা স্মৃতি বা অনুভূতি থেকে আসে, তাই “Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.”
• To a Skylark:
– এটি একটি lyric poem.
– কবি একে চাঁদ এর আলোর সাথে তুলনা করেন।
– কবির মনে এটি joyous spirit of the divine এর প্রতিক।
– তিনি skylark হবার ইচ্ছা পোষণ করেন।
– এর গান থেকে তিনি আত্মার প্রেরণা খুঁজে পান। তিনি মনে করে এর গান স্বর্গীয়।
Some of his famous quotations are:
• “Our sweetest songs are those that tell of saddest thought” (To A Skylark).
• “If Winter comes, can spring be far behind?” (Ode to the West Wind).
• “The more we study, the more we discover our ignorance” (Queen Mab).
• P.B. Shelley:
– তিনি একজন English Romantic poet.
– Her passionate search for personal love and social justice was gradually channeled from overt actions into poems that rank with the greatest in the English language.
Best works:
Poem:
– Ode to the West Wind, Queen Mab, Alastor, Adonais, Ozymandias, To a Skylark.
Drama:
– Prometheus Unbound, The Cenci.
Source: Britannica.
প্রশ্ন ৬২. Who authored the futuristic novel ‘Brave New World’?
ক) E. M. Forster খ) Virginia Woolf
গ) Aldous Leonard Huxley ঘ) Graham Greene
সঠিক উত্তর: গ) Aldous Leonard Huxley
Live MCQ Analytics: Right: 22%; Wrong: 12%; Unanswered: 65%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • Brave New World:
– এটি Aldous Leonard Huxley রচিত একটি science fiction.
– এটি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।
– The book presents a nightmarish vision of a future society.
– It is also known as a dystopian novel.
– এটিকে dystopian novel বলা হয় কারণ এই বইটি ভবিষ্যতের একটি দুঃস্বপ্নময় সমাজের চিত্র উপস্থাপন করে।
– Brave New World উপন্যাসটি ২৫৪০ খ্রিস্টাব্দে অবস্থিত, যা উপন্যাসে AF 632 বছর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
• Aldous Huxley
– In full, Aldous Leonard Huxley.
– তিনি একজন ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও সমালোচক, যিনি প্রখর ও বিস্তৃত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন।
– যার রচনাগুলো তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নিরাশাবাদী ব্যঙ্গের জন্য পরিচিত।
– তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত তার উপন্যাস Brave New World (1932)-এর জন্য, যা পরবর্তী বহু ডিস্টোপিয়ান বিজ্ঞান কল্পকাহিনির আদর্শ হয়ে উঠেছে।
• Other notable works,
– After Many a Summer Dies the Swan,
– Antic Hay,
– Crome Yellow,
– Eyeless in Gaza,
– Point Counter Point,
– The Devils of Loudun,
– The Doors of Perception,
– Those Barren Leaves, etc.
Source: Britannica.
প্রশ্ন ৬৩. ‘Good fences make good neighbors’. -The line was written by _______ .
ক) Robert Graves খ) Robert Frost
গ) Ezra Pound ঘ) Carl Sandburg
সঠিক উত্তর: খ) Robert Frost
Live MCQ Analytics: Right: 40%; Wrong: 5%; Unanswered: 54%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
“Good fences make good neighbors.” — এই বিখ্যাত উক্তিটি Robert Frost-এর লেখা কবিতা “Mending Wall” থেকে নেওয়া হয়েছে।
• Mending Wall
– এই কবিতাটি লিখেন Robert Frost.
– এটি Blank verse (অমিত্রাক্ষর ছন্দ)- এ রচিত।
– Mending Wall কবিতাটি তার ‘North of Boston’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
– কীভাবে বক্তা এবং তার প্রতিবেশী তাদের সম্পত্তির মধ্যে একটি পাথরের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের জন্য মিলিত হয় তা নিয়ে কবিতাটি রচিত।
– কবিতাটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।
• Robert Frost
– Robert Frost একজন আমেরিকান কবি।
– তিনি ‘Nature poet’, ‘Regional poet’ নামে পরিচিত।
– তিনি চারবার পুলিতজার পুরস্কার লাভ করেন।
– তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে: A Boy’s Will, North of Boston, From Mountain Interval etc.
– Mending Wall কবিতাটি তার ‘North of Boston’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত
• Poems:
– Fire and Ice, Mending Wall, Birches, Out Out, Nothing Gold Can Stay, Home Burial, etc.
Source: Britannica and litcharts.com
প্রশ্ন ৬৪. ‘Cowards die many times before their deaths:
The valiant never taste of death but once’.
In which play of Shakespeare do you find this quote?
ক) Julius Caesar খ) Romeo and Juliet
গ) The Tempest ঘ) Twelfth Night
সঠিক উত্তর: ক) Julius Caesar
Live MCQ Analytics: Right: 75%; Wrong: 4%; Unanswered: 20%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • “Cowards die many times before their deaths; the valiant never taste of death but once”. —
– এই বিখ্যাত লাইনটি নেওয়া হয়েছে William Shakespeare-এর নাটক Julius Caesar থেকে।
– নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র Julius Caesar এর করা এই উক্তিটি একটি metaphor এর উদাহরণ।
– তিনি বোঝাতে চান, ভীতুরা অনেকবার মৃত্যুর ভয় অনুভব করে, কিন্তু সাহসীরা শুধু একবারই মৃত্যু স্বাদ পায়।
• Julius Caesar:
– এটি William Shakespeare এর একটি Historical Play এবং Tragedy.
– ১৫৯৯-১৬০০ সালের মধ্যে এই নাটকটি লেখা হয় এবং ১৬২৩ সালে Shakespeare এর First Folio এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।
– Julius Caesar Rome এর ruler ছিলেন।
– Caesar এর betrayer এর নাম হলো Brutus.
– নাটকটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে ঘিরে আবর্তিত হয় যা Julius Caesar, একজন রোমান রাষ্ট্রনায়ক এবং সামরিক জেনারেলকে হত্যার দিকে নিয়ে যায়।
– ঈর্ষান্বিত ষড়যন্ত্রকারীরা সিজারের বন্ধু Brutus কে Caesar এর বিরুদ্ধে তাদের হত্যার ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজি করায়।
– Caesar কে অত্যধিক ক্ষমতা অর্জন থেকে বিরত রাখতে, Brutus এবং ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে March এর Ides এ হত্যা করে।
– Mark Antony ষড়যন্ত্রকারীদের রোম থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং একটি যুদ্ধে তাদের সাথে লড়াই করে।
এই tragedy এর কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে –
• ‘Cowards die many times before death; The valiant never taste of death but once.’
• ‘Veni, Vidi, Vici (I came, I saw, I conquered)
• ‘Et tu, Brute? (‘You too, Brutus?’)’ (last words of Julius Caesar)
• William Shakespeare:
– William Shakespeare was born on 23 April 1564 AD and died on 23 April 1616 AD.
– তার জন্মস্থান Stratford Avon.
– তিনি একাধারে একজন English poet, dramatist এবং actor.
– তাকে English national poet বলা হয়।
– তাকে ‘Bard of Avon’ বা Swan of Avon বলা হয়।
– Shakespeare wrote a total of 37 plays and 154 sonnets.
• Notable works:
• Tragedy:
– Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Julius Caesar, Antony and Cleopatra.
• Comedy:
– As You Like It, The Tempest, Twelfth Night, A Midsummer Night’s Dream etc.
• Famous poem:
– Shall I Compare Thee to a Summer Day/Sonnet 18,
– The Rape of Lucrece,
– Venus and Adonis.
Source: britannica.com
প্রশ্ন ৬৫. ‘Knowledge comes, but wisdom lingers.’ This quote is extracted from Tennyson’s poem titled ______ .
ক) Morte d’ Arthur খ) The Lotos-Eaters
গ) Tithonus ঘ) Locksley Hall
সঠিক উত্তর: ঘ) Locksley Hall
Live MCQ Analytics: Right: 11%; Wrong: 31%; Unanswered: 56%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • “Knowledge comes, but wisdom lingers” উক্তিটি নেওয়া হয়েছে Alfred Lord Tennyson-এর কবিতা Locksley Hall থেকে।
– এখানে Tennyson বোঝাতে চেয়েছেন, জ্ঞান (Knowledge) সহজে অর্জন করা যায়, কিন্তু প্রজ্ঞা বা জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা (Wisdom) দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সময়ের সাথে আসে।
• Locksley Hall:
– এটি Alfred Lord Tennyson রচিত।
– এটি একটি কবিতা।
– Poems (1842) collection এ এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়।
– বক্তা এখানে বস্তুগত লাভ এবং পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য করা বিবাহের বিরোধিতা করেন।
• Lord Alfred Tennyson:
– তিনি একজন English poet.
– তিনি একজন Victorian poet.
– English poet often regarded as the chief representative of the Victorian age in poetry.
• Notable works:
• Poems:
– Crossing the Bar,
– Enoch Arden,
– Locksley Hall,
– In memoriam.
Source: Britannica.com and Poetry Foundation.
প্রশ্ন ৬৬. The tragedy ‘Samson Agonistes’ was penned by ______.
ক) Christopher Marlowe খ) Henrick Ibsen
গ) John Milton ঘ) Arthur Miller
সঠিক উত্তর: গ) John Milton
Live MCQ Analytics: Right: 36%; Wrong: 12%; Unanswered: 50%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • Samson Agonistes:
– এটি John Milton রচিত।
– It is also known as closet tragedy.
– ১৬৭১ সালে এই Poetic drama টি প্রকাশিত হয়।
– এটিকে বলা হয় ‘greatest English drama’ based on Greek Model.
– It is also known as a closet tragedy.
– এই ধরনের নাটক গুলো সাধারণত পড়ার উপযোগী করে লেখা হয়, মঞ্চে উপস্থাপনার জন্য নয়।
– The work deals with the final phase of Samson’s life and recounts the story as told in the biblical Book of Judges.
• John Milton:
– He was born in London, England in 1608.
– তিনি ছিলেন একজন English poet, pamphleteer এবং historian.
– তিনি William Shakespeare এর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ English author হিসেবে বিবেচিত।
– মূলত কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও মিল্টন কিছু উচ্চমানের রাজনৈতিক প্রবন্ধও লিখেছিলেন।
– তাকে বলা হয় the Epic Poet.
– এছাড়া great master of Blank Verse ও বলা হয়।
• Some notable works:
– Paradise Lost (Epic),
– Paradise Regained (Epic),
– Of Education (Prose),
– Lycidas (Elegy).
Source: Britannica.
প্রশ্ন ৬৭. Who is the playwright of the absurd drama ‘Waiting for Godot’?
ক) Jean Genet খ) Samuel Beckett
গ) Harold Pinter ঘ) Tom Stoppard
সঠিক উত্তর: খ) Samuel Beckett
Live MCQ Analytics: Right: 58%; Wrong: 4%; Unanswered: 36%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • Waiting for Godot:
– এটি রচনা করেন Irish writer Samuel Beckett.
– It is an Absurd play.
– এটি একটি two-act বিশিষ্ট tragic-comedy too.
– Waiting for Godot is Beckett’s translation of his own original French-language play, En attendant Godot.
– ১৯৫২ সালে এটি প্রকাশিত হয়।
– Waiting for Godot was a true innovation in drama and the Theatre of the Absurd’s first theatrical success.
• নাটকের গল্প দুটি প্রধান চরিত্র, Vladimir এবং Estragon কে নিয়ে, যারা একটি গাছের নিচে বসে অপেক্ষা করে একজন ব্যক্তি “Godot”-এর জন্য। তারা বিশ্বাস করে যে Godot তাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করবে, কিন্তু Godot আসে না। নাটকে দেখা যায়, Vladimir ও Estragon এর জীবনের একঘেয়েমি, হতাশা, এবং সমাজের অস্থিরতা উঠে আসে। তারা অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু Godot আসবে কিনা তা জানে না।
– “Waiting for Godot” মানবজীবনের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, এবং অস্তিত্বের মানে খোঁজার একটি প্রতীকী কাহিনী।
• Samuel Beckett (1906- 1989):
– Samuel Beckett একজন আইরিশ নাট্যকার, লেখক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন।
– তিনি ১৯৬৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
– বেকেট ফরাসি ও ইংরেজি—এই দুই ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করতেন।
– তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত সৃষ্টি হল “Waiting for Godot” (১৯৫২), যা একটি অস্তিত্ববাদী নাটক এবং আধুনিক থিয়েটারে এক যুগান্তকারী কাজ হিসেবে বিবেচিত।
Best Works: (play)
– Waiting for Godot,
– Endgame,
– Happy Days.
Source: An ABC of English Literature by Dr. M Mofizar Rahman & Britannica.
প্রশ্ন ৬৮. ‘It’s strange – but true; for truth is always strange; Stranger than fiction.
This quote is taken from a poem of _____.
[Correct: Tis strange,- but true…..]
ক) Mark Twain খ) Robert Herrick
গ) Lord Byron ঘ) Franz Kafka
সঠিক উত্তর: গ) Lord Byron
Live MCQ Analytics: Right: 8%; Wrong: 9%; Unanswered: 82%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: “It’s strange – but true; for truth is always strange; Stranger than fiction.”
— উদ্ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে Lord Byron-এর রচিত ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্যিক কবিতা Don Juan থেকে।
– Byron এখানে বলেছেন, সত্য ঘটনা প্রায়ই কল্পনার চেয়েও অদ্ভুত।
– উদ্ধৃত লাইনটি কবিতার Canto XIV-তে পাওয়া যায়।
সঠিক ও সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিটি হলো —
“Tis strange,-but true; for truth is always strange;
Stranger than fiction: if it could be told,
How much would novels gain by the exchange!
How differently the world would men behold!”• Don Juan:
– Romantic period এর অন্যতম poet and satirist Lord Byron এর অনবদ্য সৃষ্টি Don Juan হচ্ছে a satire in the form of a picaresque verse tale.
– এটি Lord Byron রচিত একটি unfinished satirical epic poem.
– তার জন্ম স্পেনের সেভিল শহরে।
– এই কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে Don Juan যাকে ঘিরে কবিতার মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে এবং তার নামেই কবিতাটির নামকরণ করা।
– Don Juan কে এখানে চিত্রায়িত করা হয়েছে womanizer এবং easily seduced by women হিসেবে।
– কবিতাটি প্রায় পাঁচ হাজার লাইন বিশিষ্ট।
এই poem এর কিছু বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে –
• “Sweet is revenge—especially to women.”
• “Pleasure’s a sin, and sometimes sin’s a pleasure.”
• “Man’s love is of man’s life a thing apart, Tis woman’s whole existence.”
• “Tis strange,-but true; for truth is always strange;
Stranger than fiction: if it could be told,
How much would novels gain by the exchange!
How differently the world would men behold!”
Lord Byron:
– Lord Byron-র পুরো নাম George Gordon Byron.
– George Gordon Byron একজন British Romantic Poet এবং Satirist ছিলেন।
Best Works:
Poetry:
– Childe Harold’s Pilgrimage,
– Don Juan,
– English Bards and Scotch Reviewers,
– Hours of Idleness,
– Heaven and Earth.
Poem:
– She walks in Beauty,
– The Vision of Judgement.
Source: Britannica.
প্রশ্ন ৬৯. Who wrote the novella ‘Heart of Darkness’?
ক) Joseph Conrad খ) Doris Lessing
গ) John Osborne ঘ) Thomas Hardy
সঠিক উত্তর: ক) Joseph Conrad
Live MCQ Analytics: Right: 42%; Wrong: 10%; Unanswered: 46%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
• Heart of Darkness:
– Novella টি রচনা করেন Joseph Conrad.
– ১৮৯৯ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
– Heart of Darkness পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতার বিভীষিকাগুলো বিশ্লেষণ করে, যা এটিকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে চিত্রিত করে যা শুধুমাত্র যেসব ভূখণ্ড ও জনগণকে শোষণ করে তাদেরকেই কলুষিত করে না, বরং পশ্চিমাদের—যারা এই শোষণকে চালিত করে—তাদেরকেও নৈতিকভাবে কলুষিত করে তোলে।
– এটি Western colonialism এর ভয়াবহতা নিয়ে বর্ণিত একটি novella.
– The novella begins with a group of passengers aboard a boat floating on the river Thames.
• Joseph Conrad: [born December 3, 1857 – died August 3, 1924]
– Also known as: Jozef Teodor Konrad Korzeniowski.- তিনি ছিলেন একজন English novelist ও short-story writer.
• তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম গুলো হচ্ছে –
– Heart of Darkness, Lord Jim, Nostromo, The Secret Agent, Typhoon, Under Western Eyes, Victory, Youth, ইত্যাদি।
Source: Britannica.
প্রশ্ন ৭০. Who was the writer of the autobiographical as well as political essay ‘Shooting and Elephant’? [Correct: Shooting an Elephant]
ক) Francis Bacon খ) George Orwell
গ) Joseph Addison ঘ) Charles Lamb
সঠিক উত্তর: খ) George Orwell
Live MCQ Analytics: Right: 45%; Wrong: 6%; Unanswered: 48%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: পরীক্ষার প্রশ্নে সাহিত্যকর্মটির নাম “Shooting and Elephant” ভুল ভাবে দেওয়া হয়েছে, এর সঠিক নাম হলো – Shooting an Elephant.
• Shooting an Elephant:
– এই essay টি রচনা করেন English writer George Orwell.
– এটি একটি autobiographical ও political essay.
• George Orwell বার্মায় পুলিশ অফিসার থাকাকালে একটি হাতিকে গুলি করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। হাতিটি বাজারে হাঙ্গামা করলেও পরে শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় মানুষের চাপ ও প্রত্যাশার কারণে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতিটিকে গুলি করেন। হাতিটির ধীর ও বেদনাদায়ক মৃত্যু তাকে গভীর অনুশোচনায় ফেলে। এ ঘটনায় বোঝা যায়, উপনিবেশবাদ শুধু শোষিতদের নয়, শোষককেও নিজের স্বাধীনতা ও নৈতিকতা থেকে বঞ্চিত করে।
• George Orwell
– তার আসল নাম হলো Eric Arthur Blair.
– তিনি ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রদেশের মতিহারি -তে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৪৬ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।
– তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ উপন্যাসক, প্রবন্ধকার, এবং সমালোচক।
– তিনি দুটি বিখ্যাত উপন্যাস Animal Farm (১৯৪৫) এবং Nineteen Eighty-Four (১৯৪৯) -এর জন্য পরিচিত।
– এই দুটি উপন্যাসই বিশ্ব সাহিত্যে অমর হয়ে আছে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণার প্রতি গভীর সমালোচনা প্রদর্শন করেছে।
• Famous Works:
• Novels:
– Animal Farm,
– Nineteen Eighty-Four / ‘1984’,
– Burmese Days,
– Coming up for Air.
• Story/Essay:
– Shooting an Elephant,
– A Hanging.
Source: Britannica.
বাংলাদেশ বিষয়াবলি
প্রশ্ন ৭১. কোন মুসলিম চিন্তাবিদ প্রথম ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব‘ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন?
ক) আল্লামা ইকবাল খ) সৈয়দ আহমদ খান
গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) মওলানা আকরম খাঁ
সঠিক উত্তর: খ) সৈয়দ আহমদ খান
Live MCQ Analytics: Right: 4%; Wrong: 71%; Unanswered: 24%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে সৈয়দ আহমদ খান প্রথম ‘দ্বি-জাতি তত্ত্ব‘ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব:
→ দ্বি-জাতি তত্ত্ব হলো একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন, যার মতে হিন্দু ও মুসলমানরা ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন জীবনাচার ও ভিন্ন ঐতিহ্যের কারণে একই জাতি নয়; তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতি। তাই তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র থাকা আবশ্যক।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও সৈয়দ আহমদ খান এর ভূমিকা:
→ সৈয়দ সায়্যদ আহমদ খান মীরাটে ১৬ মার্চ ১৮৮৮ সালের এক বক্তৃতায় হিন্দু ও মুসলিমকে আলাদা করে ‘two nations’ উল্লেখ করেন; এই মীরাট-বক্তৃতাই আধুনিক ‘দ্বি-জাতি’ ধারণার সবচেয়ে প্রাথমিক স্পষ্ট রূপগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত।
→ মীরাটে দেওয়া বক্তৃতায় সৈয়দ আহমদ খান স্পষ্টভাবে বলেন: ‘হিন্দু এবং মুসলমান দুটি পৃথক সম্প্রদায়, যাদের ধর্ম, ঐতিহ্য এবং জীবনধারা ভিন্ন। একটি যৌথ রাষ্ট্রে তাদের একসঙ্গে শাসন করা কঠিন হবে।’
→ মীরাট বক্তব্যে সৈয়দ সরাসরি আলাদা রাষ্ট্র দাবি করেননি; তিনি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দিয়ে সম্ভাব্য ক্ষমতা-অসাম্য তুলে ধরেছিলেন।
→ তিনি মনে করতেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ আলাদা।
→ এই বক্তৃতা এবং তাঁর অন্যান্য লেখনীতে তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তাঁর এই ধারণা দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও আল্লামা ইকবাল এর ভূমিকা:
→ ১৯৩০ সালে আল্লামা ইকবাল এলাহাবাদে All India Muslim Legue-এর বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং এতে সমর্থন ব্যক্ত করেন।
→ এই ভাষণে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে একত্র করে স্বশাসিত মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন।
→ তাঁর কবিতা ও রচনা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আত্মপরিচয় জাগ্রত করতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।
→ ইতিহাসবিদদের মতে, স্যার সাইয়্যদের বপন করা বীজকে ইকবাল দার্শনিক ভিত্তি ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দেন, যা পরবর্তীতে জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনের রূপ নেয়।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর ভূমিকা:
→ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বকে রাজনৈতিক বাস্তবতায় রূপ দেন; তিনি মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলিমদের জন্য স্বশাসিত রাষ্ট্র দাবির নেতৃত্ব দেন।
→ তিনি ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ভারতীয় মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব দেন। এটি ছিল আনুষ্ঠানিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব।
→ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-এর রাজনৈতিক নেতৃত্বই দ্বি-জাতি তত্ত্বকে কার্যকর বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও মাওলানা আকরম খাঁ এর ভূমিকা:
→ মাওলানা আকরম খাঁ ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে যোগদান করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
→ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি মুসলিম লীগের অবস্থানকে দৃঢ় করেন।
→ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া, ব্রিটানিকা ও কয়েকটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট।
– ব্রিটানিকা: [লিঙ্ক]
– Banglapedia: [লিঙ্ক]
– আল্লামা ইকবালের অফিসিয়াল সাইট: [লিঙ্ক]
– দ্বিজাতি তত্ত্ব নিয়ে গবেষণাপত্র: [লিঙ্ক]
– Dwan ওয়েবসাইট: [লিঙ্ক]
– Thesis Paper Link: [লিঙ্ক]
প্রশ্ন ৭২. কোন বছর পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
ক) ১৯৫২ খ) ১৯৫৪ গ) ১৯৫৬ ঘ) ১৯৬৯
সঠিক উত্তর: গ) ১৯৫৬
Live MCQ Analytics: Right: 54%; Wrong: 31%; Unanswered: 14%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, গণপরিষদে স্বীকৃতি প্রদান করে। তবে এটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি ছিল না।
♦ ভাষা আন্দোলন:
→ ভাষা আন্দোলন ছিলো বাঙালি সংস্কৃতির স্বাধিকার আন্দোলন।
→ ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় উর্দু বনাম বাংলা বিতর্ক প্রথম ওঠে।
→ ১৯৩৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করার প্রস্তাব করলে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর বিরোধিতা করেন।
→ ১৯৪৮ সালে গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন।
→ ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ঘোষণা করেন ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু’; এই ঘোষণার পরেই ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।
→ ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহষ্পতিবার, ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
→ ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা অমান্য করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ছাত্ররা মিছিল করে।
→ এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই আব্দুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমদ শহীদ হন। ১৭ জনের মত গুরুতর আহত হয়। তাদের মধ্যে রাত আটটায় আবুল বরকত শহীদ হন।
→ এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সংবিধান উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
♦ ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:
→ প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।
→ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব পাস হয়।
→ ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে পৃথিবীর ১৮৮টি দেশে এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন শুরু হয়।
→ ২০০৭ সালের ১৬ মে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন হয় যেখানে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের আহবান জানানো হয় এবং একই প্রস্তাবে ২০০৮ সালকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বর্ষ ঘোষণা করা হয়।
→ পরবর্তীতে ২০১০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব পাস হয়।
তথ্যসূত্র – ইউনেস্কো ও জাতিসংঘ ওয়েবসাইট, বাংলাপিডিয়া ও ইতিহাস ১ম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ৭৩. ‘তমদ্দুন মজলিস‘-এর নেতা জনাব আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন?
ক) রসায়ন বিজ্ঞান খ) গণিত
গ) ইতিহাস ঘ) পদার্থ বিজ্ঞান
সঠিক উত্তর: ঘ) পদার্থ বিজ্ঞান
Live MCQ Analytics: Right: 58%; Wrong: 17%; Unanswered: 23%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ ‘তমদ্দুন মজলিস‘-এর নেতা জনাব আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
♦ তমদ্দুন মজলিশ:
→ তমদ্দুন মজলিশ ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন।
→ তমদ্দুন মজলিশ ইসলামী আদর্শাশ্রয়ী একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।
→ ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।
→ অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।
→ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
→ মদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠায় অধ্যাপক আবুল কাশেমের অগ্রণী সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক এ.এস.এম নূরুল হক ভূঁইয়া, শাহেদ আলী, আবদুল গফুর, বদরুদ্দীন উমর, হাসান ইকবাল
→ অধ্যাপক আবুল কাশেম ছিলেন পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তমদ্দুন মজলিশের সভাপতি নির্বাচিত হন।
→ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে বস্ত্তত তমদ্দুন মজলিশই প্রথম প্রতিবাদ উত্থাপন করে।
→ এই সংগঠন ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।
→ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে তমদ্দুন মজলিশের প্রকাশিত পুস্তিকাটির নাম ছিল ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’।
→ তমদ্দুন মজলিশ ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।
→ ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বহু প্রখ্যাত এবং অখ্যাত লেখক বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন।
→ পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিষয়তালিকা থেকে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলাকে বাদ দেয়া হয়।
→ এমনকি পাকিস্তানের গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়। ফলে বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
তথ্যসূত্র – বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৭৪. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘জল্লাদের দরবার‘ এর রচয়িতা কে ছিলেন?
ক) কল্যাণ মিত্র খ) রাজু আহমেদ
গ) এম আর আকতার মুকুল ঘ) নারায়ণ ঘোষ (মিতা)
সঠিক উত্তর: ক) কল্যাণ মিত্র
Live MCQ Analytics: Right: 9%; Wrong: 60%; Unanswered: 30%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘জল্লাদের দরবার‘ এর রচয়িতা ছিলেন কল্যাণ মিত্র।
♦ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র:
→ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র।
→ বস্ত্তত, চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে এর প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়।
→ এই কেন্দ্র থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল।
→ স্বাধীন বাংলা বেতারের অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল:
• ‘চরমপত্র‘,
• ‘জল্লাদের দরবার’,
• মীর জাফরের রোজনামচা।
♦ ‘জল্লাদের দরবার’:
→ জল্লাদের দরবার-এ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অমানবিক চরিত্র ও পাশবিক আচরণকে তুলে ধরা হতো।
→ এই ব্যঙ্গাত্মক সিরিজে তাকে ‘কেল্লা ফতেহ খান’ চরিত্রে চিত্রিত করা হয় এবং এই ভূমিকায় অভিনয় করেন রাজু আহমেদ। এটি মূলত ছিল রূপকধর্মী সিরিজ নাটক।
• ‘জল্লাদের দরবার‘ নাটক রচনা ও প্রযোজনা করেন – কল্যাণ মিত্র।
→ এছাড়াও তিনি ‘মীর জাফরের রোজনামচা’ নামক আরেকটি নাটক রচনা করেন।
♦ ‘চরমপত্র’:
→ চরমপত্র ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান।
→ এটি ছিল ব্যঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্মক মন্তব্যে ভরপুর একটি অনুষ্ঠান, যা মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
→ রচনা ও উপস্থাপনা: এম আর আখতার মুকুল।
→ চরমপত্র প্রচারের পরিকল্পনা করেছিলেন: এমএ মান্নান [গণপরিষদ সদস্য]
তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া ও পত্রিকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রিপোর্ট।
প্রশ্ন ৭৫. কোন তারিখে আসাদুজ্জামান আসাদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন?
ক) ১৮ জানুয়ারি ১৯৬৯ খ) ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯
গ) ২২ জানুয়ারি ১৯৬৯ ঘ) ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯
সঠিক উত্তর: খ) ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯
Live MCQ Analytics: Right: 68%; Wrong: 11%; Unanswered: 20%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ আসাদুজ্জামান আসাদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি।
♦ ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান:
→ আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তা ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে তুঙ্গে ওঠে এবং মধ্য জানুয়ারিতে গণআন্দোলনের রূপ নেয়।
→ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ দেশের সকল মৌলিক গণতন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান জানালে অনেকেই সে আহ্বানে সাড়া দেন।
→ ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের সংগে একাত্মতা ঘোষণা করেন।
→ আইয়ুব পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী দিয়ে ঐ আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করেন।
→ ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
→ আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে যখন প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করার সময় ১৮ ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলি ও বেয়নেট চার্জের ফলে মৃত্যুবরণ করেন।
♦ উল্লেখ্য:
→ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে ‘এগারো দফা’ প্রণীত হয়।
→ এ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন ঘটে।
তথ্যসূত্র – বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ৭৬. ‘ঢাকা প্রকাশ‘ সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক কে?
ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার খ) সিকান্দর আবু জাফর
গ) শামসুর রাহমান ঘ) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সঠিক উত্তর: ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
Live MCQ Analytics: Right: 70%; Wrong: 5%; Unanswered: 24%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ ‘ঢাকা প্রকাশ‘ সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
♦ ‘ঢাকা প্রকাশ‘ পত্রিকা:
→ ঢাকা প্রকাশ ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।
→ এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ বাবুবাজারের ‘বাঙ্গালা যন্ত্র’ থেকে।
→ পত্রিকার শিরোনামের নিচে একটি সংস্কৃত শ্লোকাংশ ‘সিদ্ধিঃ সাধ্যে সমামন্ত্র’ (সাধ্য অনুযায়ী সিদ্ধিলাভ হোক) মুদ্রিত হতো।
→ ঢাকা প্রকাশের প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
→ পরিচালকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, চন্দ্রকান্ত বসু প্রমুখ।
→ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পর দীননাথ সেনের পরিচালনায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
তথ্যসূত্র – বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৭৭. সেরিকালচার বলতে বোঝায়-
ক) তুলা চাষ খ) নীল চাষ
গ) রেশম পোকা চাষ ঘ) তামাক চাষ
সঠিক উত্তর: গ) রেশম পোকা চাষ
Live MCQ Analytics: Right: 85%; Wrong: 1%; Unanswered: 12%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সেরিকালচার (Sericulture):
– রেশম পোকার বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে।
– এদের মধ্যে Bombyx mori রেশম চাষে বেশি ব্যবহার করা হয়। এ পোকা তুঁত গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে বিধায় রেশম চাষীকে তুঁত গাছ চাষ করতে হয়।
– রেশম চাষ এর ইংরেজি হলো সেরিকালচার (Sericulture)। ল্যাটিন শব্দ ‘Serio’ থেকে Sericulture শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ‘Serio’ শব্দের অর্থ Silk বা রেশম।
– রেশম পোকার খাদ্যের জন্য তুঁত গাছ চাষ করে এই পোকার লার্ভা পালন করে তাদের সৃষ্ট গুটি বা কোকুন থেকে রেশম সুতা আহরণ করার পদ্ধতিকে রেশম চাষ বলা হয়।
– তুঁত গাছ চাষ ও রেশম পোকার লার্ভা পালন ছাড়াও এ পোকার বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে অধিক উৎপাদনশীল রেশম পোকা উদ্ভাবন করা আধুনিক রেশম চাষের অন্তর্ভুক্ত।
– এই দেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু রেশম চাষের জন্য বেশ উপযোগী।
গুরুত্বপূর্ণ আরোও কিছু আধুনিক চাষ পদ্ধতি:
– বাণিজ্যিকভাবে উদ্যান বিষয়ক বিদ্যাকে বলে হর্টিকালচার।
– বাণিজ্যিকভাবে মৌমাছি চাষ করাকে এপিকালচার বলে।
– বাণিজ্যিকভাবে পাখি পালন বিষয়ক বিদ্যাকে বলে এভিকালচার।
– বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য চাষ বিষয়ক বিদ্যাকে বলে পিসিকালচার।
– বাণিজ্যিকভাবে চিংড়ি চাষ বিষয়ক বিদ্যাকে বলে প্রণকালচার।
– বাণিজ্যিকভাবে সামুদ্রিক মৎস্য পালন বিষয়ক বিদ্যাকে বলে মেরিকালচার।
উৎস: কৃষি শিক্ষা প্রথমপত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ও বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৭৮. ছায়া প্রেমী (shadow loving) অর্থনৈতিক ফসল কোনটি?
ক) আখ খ) তামাক গ) ধান ঘ) চা
সঠিক উত্তর: ঘ) চা
Live MCQ Analytics: Right: 64%; Wrong: 11%; Unanswered: 23%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:⇒ ‘ছায়া প্রেমী‘ অর্থনৈতিক ফসল বলতে চা গাছকে বোঝানো হয়। চা গাছের জন্য অতিরিক্ত তাপ ও সরাসরি সূর্যালোক থেকে রক্ষা পেতে ছায়াযুক্ত পরিবেশে ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়। এ কারণে চা গাছকে ছায়া প্রেমী ফসল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
♦ চা চাষ:
→ চা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু বিশেষ উপযোগী।
→ সাধারণত যেসব স্থানে ২৬০-২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকে সেসব স্থান চা চাষের উপযুক্ত।
→ গাছের বৃদ্ধিকালীন সময়ে ২০° সেলসিয়াস এর অধিক তাপমাত্রা প্রয়োজন।
→ চা চাষের জন্য ১৭৫ – ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৭০-৯০% আবশ্যক।
→ বাংলাদেশে চা চাষের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো ছায়া গাছ।
→ চা বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশ পরিবর্তন, মাটির উর্বরতা সমৃদ্ধকরণ, তাপমাত্রা এবং বাষ্পীভবন ক্ষমতা হ্রাস, মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ এবং কিছু পোকামাকড় ও রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য ছায়া গাছ অপরিহার্য, যা ইতিবাচকভাবে তাপীয়ভাবে প্রভাবিত করে।
→ ছায়া গাছ চা গাছগুলিকে আংশিক ছায়া প্রদান করে, যা চা পাতার মান উন্নত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
→ সঠিক ধরণের ছায়া গাছ এবং তাদের সঠিক ব্যবস্থাপনা সফল চা ফসল চাষের পূর্বশর্ত।
→ অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি বা খরা কোনোটিই চা গাছের জন্য উপযুক্ত নয়।
→ চা গাছের জন্য যেমন প্রচুর পানি প্রয়োজন তেমনি উপযুক্ত নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও থাকতে হয়।
তথ্যসূত্র – বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাপিডিয়া ও ভূগোল ২য় পত্র, এইচএসসি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ৭৯. বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশে কোন ফসলের চাষ তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে?
ক) ভূট্টা খ) পাট গ) ধান ঘ) গোল আলু
সঠিক উত্তর: ক) ভূট্টা
Live MCQ Analytics: Right: 12%; Wrong: 48%; Unanswered: 39%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশে ভুট্টা চাষ তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
♦ ভূট্টা উৎপাদন:
– বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের কৃষিতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ভূট্টা (মেইজ) চাষে।
– ১৯৭১ সালে দেশের ভূট্টার উৎপাদন ছিল মাত্র ২,০০০ মেট্রিক টন এবং চাষের পরিমাণ ছিল মাত্র ২,৬৫৪ হেক্টর।
– ২০১৯–২০২০ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৪ লাখ মেট্রিক টনে, এবং চাষের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১,৬৫,৫১০ হেক্টর।
– প্রতি হেক্টরে ফলনও বেড়েছে ০.৮৫ টন থেকে ৬.১৫ টনে।
– অন্য ফসল যেমন ধান, পাট ও আলুর চাষও বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তুলনামূলকভাবে ভূট্টার বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি।
কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) অনুসারে,
স্বাধীনতার পর থেকে এ নাগাদ চালের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চারগুণ, গম দুইগুণ, ভুট্টা ১০ গুণ ও সবজির উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ।
উল্লেখ্য:
– ধান ১৯৭১ সালে ৯.৬৭ মিলিয়ন টন থেকে ২০১৯ সালে ৩৮.৭০ মিলিয়ন টনে বৃদ্ধি পেয়েছে।
– ১৯৭১ সালে পাটের উৎপাদন ছিল প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন বেল এবং চাষের পরিমাণ ছিল ৮০০,০০০ হেক্টর। ২০২০ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ মিলিয়ন বেল এবং চাষের পরিমাণ প্রায় ৮২০,০০০ হেক্টর, প্রতি হেক্টরে ফলন কিছুটা বেড়েছে।
– গোল আলুর ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে উৎপাদন ছিল ৪.৫ লাখ মেট্রিক টন এবং চাষের পরিমাণ ৮৫,০০০ হেক্টর। ২০২০ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৯ লাখ মেট্রিক টনে, চাষের পরিমাণ ১,২০,০০০ হেক্টর এবং প্রতি হেক্টরে ফলন বেড়ে ৭.৪ টন হয়েছে।
তথ্যসূত্র – ডেইলী সান পত্রিকার রিপোর্ট (লিংক) ও কৃষি তথ্য সার্ভিস। (লিংক)
প্রশ্ন ৮০. ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা-
ক) প্রায় উনিশ কোটি খ) প্রায় সাড়ে ষোলো কোটি
গ) প্রায় আঠারো কোটি ঘ) প্রায় সতেরো কোটি
সঠিক উত্তর: ঘ) প্রায় সতেরো কোটি
Live MCQ Analytics: Right: 51%; Wrong: 31%; Unanswered: 16%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় সতেরো কোটি।
♦ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২:
→ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) জনশুমারি পরিচালনা করে।
→ ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুষ্ঠিত হয় : ১৫-২১ জুন ২০২২ সালে।
→ এটি দেশের প্রথম ডিজিটাল শুমারি।
→ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর তথ্য সংগ্রহে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে – CAPI.
→ CAPI এর পূর্ণরূপ – Computer Assisted Personal Interviewing.
→ গণনায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে- মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো (Modified De-facto) পদ্ধতি।
→ মোট জনসংখ্যা: ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন।
→ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১.১২%।
→ জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১১৯ জন।
♦ উল্লেখ্য:
⇒ সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা- ঢাকা (১০০৬৭ জন)।
⇒ সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ জেলা- রাঙ্গামাটি (১০৬ জন)।
⇒ জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে। (২১৫৬ জন)।
⇒ জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম বরিশাল বিভাগে। (৬৮৮ জন)।
তথ্যসূত্র – পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ৮১. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রধানত-
ক) দারিদ্র হ্রাস করে খ) ভিক্ষাবৃত্তি হ্রাস করে
গ) নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে ঘ) নারীর অংশগ্রহণ হ্রাস করে
সঠিক উত্তর: গ) নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে
Live MCQ Analytics: Right: 47%; Wrong: 38%; Unanswered: 14%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম:
– দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক ঋণ প্রদানের একটি কর্মসূচি হিসেবে প্রথমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। – বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক-এর মতো বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৮০০-এর অধিক এনজিও দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
• ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:
১। উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ। ২। উদ্যোক্তা সৃষ্টি।
৩। নারীর ক্ষমতায়ন।
⇒ এখানে অপশন বিবেচনায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি অধিক গ্রহণযোগ্য। তার যৌক্তিকতা হল –
• গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মূলত নারীদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়।
• এ কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করে।
• স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে।
• এর ফলে সমাজে নারীর দৃঢ় অবস্থান প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।
⇒ তাই বলা যায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য।
উৎস: জাতীয় তথ্য বাতায়ণ এবং অর্থনীতি, নবম-দশম শ্রেণি। [লিংক]
প্রশ্ন ৮২. বর্তমানে পৃথিবীর কোন্ দেশে বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছে?
ক) সৌদি আরব খ) মালয়েশিয়া
গ) সংযুক্ত আরব আমিরাত ঘ) ইতালি
সঠিক উত্তর: ক) সৌদি আরব
Live MCQ Analytics: Right: 74%; Wrong: 10%; Unanswered: 14%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশি অভিবাসন (২০২৪):
– মোট বিদেশে প্রেরিত কর্মী: ১০ লাখ ১১,৮৬৯ জন (BMET অনুযায়ী)
– মূল গন্তব্য দেশসমূহ: সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কাতার, সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত
– মোট কর্মীর ৯৫% এই পাঁচটি দেশে গিয়েছেন।
• শীর্ষ গন্তব্য: সৌদি আরব
– মোট অভিবাসনের ৬২.১৭% (প্রায় ৬ লাখ ২৭ হাজার কর্মী) সৌদি আরবে গেছেন।
– সেখানে অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন খাতে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা অব্যাহত আছে।
• দ্বিতীয় বৃহত্তম গন্তব্য: মালয়েশিয়া।
– ২০২৪ সালে মাত্র ৯৩ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় গেছেন।
উৎস – প্রথম আলো পত্রিকা রিপোর্ট এবং বিএমইটি রিপোর্ট।
প্রশ্ন ৮৩. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির সহনশীল মাত্রা হলো-
ক) ০৬-০৮ শতাংশ খ) ০১-০৫ শতাংশ
গ) ০৯-১২ শতাংশ ঘ) ১৩-১৫ শতাংশ
সঠিক উত্তর: ক) ০৬-০৮ শতাংশ
Live MCQ Analytics: Right: 30%; Wrong: 15%; Unanswered: 53%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
• মুদ্রাস্ফীতি:
– যদি পণ্যের তুলনায় মুদ্রার সরবরাহ অনেক বেড়ে যায় অর্থাৎ দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক অতিরিক্ত মাত্রায় টাকা ছাপায় তখনই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।
– বাজারে উৎপাদনের তুলনায় মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে গেলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি হলো মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি।
– এতে করে টাকা তথা মুদ্রার মান হ্রাস পায়, পক্ষান্তরে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়।
– একই পরিমাণ পণ্য ক্রয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় হয়।
– উৎপাদনের তুলনায় বাজারে মুদ্রার সরবরাহ কমে গেলে মুদ্রা সংকোচন ঘটে।
– উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মুদ্রাস্ফীতির জন্য সর্বজনীনভাবে নির্ধারিত সহনীয় স্তর নেই।
– তবে, উন্নয়নশীল দেশের জন্য মূল্যস্ফীতির সহনশীল মাত্রা ধরা হয় ৬-৮%।
– মুদ্রাস্ফীতি ৬-৮% এর বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মূল্য স্থিতিশীলতা এবং দারিদ্র্যের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
এছাড়াও,
⇒ অতি মুদ্রাস্ফীতি নিম্নলিখিত প্রভাব সৃষ্টি করে:
• সঞ্চয় হ্রাস করে
• বিনিয়োগ হ্রাস করে।
• অর্থনৈতিক পছন্দগুলিকে বিকৃত করে।
• আয়ের বৈষম্য আরও বাড়ায়।
উৎস: অর্থনীতি ২য় পত্র, এইচএসসি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং IMF ওয়েবসাইট।[লিংক]
প্রশ্ন ৮৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি করা অর্থ পাচার করা হয়-
ক) যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্দোনেশিয়ায় খ) যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে
গ) যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপাইনে ঘ) শ্রীলংকা ও ফিলিপাইনে
সঠিক উত্তর: ঘ) শ্রীলংকা ও ফিলিপাইনে
Live MCQ Analytics: Right: 27%; Wrong: 38%; Unanswered: 34%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি:
– ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০ কোটি ১০ লাখ ১ হাজার ৬২৩ ডলার চুরি হয়।
– এর মধ্যে ৮১ মিলিয়ন ডলার ফিলিপাইনের আরসিবিসি ব্যাংকে থাকা চারটি অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয় এবং বাকি ২০ মিলিয়ন ডলার শ্রীলঙ্কার একটি ব্যাংকে পাঠানো হয়।
এছাড়াও,
– বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে হলিউড তথ্যচিত্র ‘বিলিয়ন ডলার হাইস্ট’।
– তথ্যচিত্রটি যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন ড্যানিয়েল গর্ডন, ব্রেন্ডন ডনোভান ও ব্রায়ান ইভানস।
উৎস – প্রথম আলো এবং বাসস পত্রিকা রিপোর্ট।
প্রশ্ন ৮৫. অর্থ পাচারের কারণ নয় কোনটি?
ক) অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ গোপন করা
খ) কর ফাঁকি না দেয়া
গ) কোম্পানির মুনাফা লুকানো
ঘ) দেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি না থাকা
সঠিক উত্তর: খ) কর ফাঁকি না দেয়া
Live MCQ Analytics: Right: 63%; Wrong: 19%; Unanswered: 17%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: অর্থ পাচার:
– অর্থ পাচার হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অপরাধীরা তাদের বেআইনি উপার্জনের উৎস ও মালিকানা লুকানোর চেষ্টা করে।
– এটি প্রত্যেক দেশের জন্যই একটি ক্ষরণ-জাতীয় জটিল সমস্যা হিসেবে বিবেচিত করা হয়।
– অর্থ পাচারের (মানি লন্ডারিং) পেছনে প্রধান কারণসমূহ:
• দেশে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিস্থিতি না থাকা।
• ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতার চাপের মধ্যে টিকে থাকতে না পারা।
• বাংলাদেশের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা না থাকা।
• অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ গোপন করার চেষ্টা।
⇒ উক্ত অপশনগুলোর মধ্যে একমাত্র ‘কর ফাঁকি না দেওয়া‘ সঠিক উত্তর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
উৎস – বণিক বার্তা পত্রিকা রিপোর্ট ও সিপিডি ওয়েবসাইট ।
প্রশ্ন ৮৬. বাংলাদেশ কোন্ দুটি দেশ হতে সিংহভাগ সয়াবিন তেল আমদানী করে?
ক) মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া খ) ভারত ও চীন
গ) জার্মানি ও ভিয়েতনাম ঘ) আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল
সঠিক উত্তর: ঘ) আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল
Live MCQ Analytics: Right: 16%; Wrong: 37%; Unanswered: 46%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: সয়াবিন তেল আমদানি:
– বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ সয়াবিন তেল আমদানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত।
– দেশের সয়াবিন তেলের চাহিদার বড় অংশই আমদানি দ্বারা পূরণ হয়।
– বাংলাদেশ তার সয়াবিন তেলের অধিকাংশ আমদানি করে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
– এই তিনটি দেশ প্রধান সয়াবিন উৎপাদক ও সরবরাহকারী হিসেবে বাংলাদেশের বার্ষিক চাহিদার বড় অংশ পূরণ করে।
এছাড়াও,
– জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ সাত দেশের আট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় সোয়া ১৪ লাখ টন পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে।
সূত্র: মার্কিন কৃষি বিভাগের (USDA) ফরেন এগ্রিকালচারাল সার্ভিস এবং প্রথম আলো পত্রিকা রিপোর্ট [লিংক] [লিংক]
প্রশ্ন ৮৭. বিশ্বব্যাংকের মতে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি বাড়ার কারণ নয় কোনটি?
ক) বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধি পাওয়া খ) অভ্যন্তরীণ জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধি
গ) দুর্বল মুদ্রানীতি ঘ) টাকার অবমূল্যায়ন
সঠিক উত্তর: ক) বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধি পাওয়া
Live MCQ Analytics: Right: 55%; Wrong: 17%; Unanswered: 27%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: মুদ্রাস্ফীতি:
– মুদ্রাস্ফীতি বলতে বোঝায় পণ্য ও সেবার দাম বেড়ে যাওয়া, যার ফলে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়।
বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণসমূহ –
⇒ জ্বালানির দাম বৃদ্ধি: জ্বালানি ও বিদ্যুতের খরচ বৃদ্ধি ব্যবসার উৎপাদন খরচ বাড়ায়। এর ফলে ভোক্তা মূল্যে সরাসরি প্রভাব পড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়।
⇒ দুর্বল মুদ্রানীতি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না, তখন অতিরিক্ত অর্থ চলাচল করে দাম বাড়ায়।
⇒ মুদ্রার অবমূল্যায়ন: বাংলাদেশি টাকার দুর্বলতা আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়ায়।
⇒ বিশ্বব্যাংকের মতে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি বাড়ার কারণ নয় – বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধি পাওয়া।
অর্থাৎ, বৈদেশিক মুদ্রার মান বৃদ্ধি সরাসরি বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতিতে বড় ভূমিকা রাখে না।
উৎস: আইএমএফ ওয়েবসাইট এবং বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইট। [লিংক] [লিংক]
প্রশ্ন ৮৮. বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানার নাম-
ক) ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড
খ) যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড
গ) পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড
ঘ) ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড
সঠিক উত্তর: গ) পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড
Live MCQ Analytics: Right: 35%; Wrong: 44%; Unanswered: 20%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানার নাম পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড।
♦ ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা:
→ দেশের বৃহত্তম সার কারখানা ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা।
→ এটি নরসিংদীতে অবস্থিত।
→ দেশের ইউরিয়া সারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় বার্ষিক ৩,৪০,০০০ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ এবং ১৯৮৫ সালে বার্ষিক ৯৫,০০০ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপিত হয়।
♦ উল্লেখ্য:
→ ১২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পরিবেশবান্ধব, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক এ কারখানার উদ্বোধন করা হয়।
→ সার উৎপাদনের ক্ষমতা: বার্ষিক ৯ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন।
→ এটি বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা, যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্লু গ্যাস থেকে পরিবেশদূষণকারী আহরণ করা হবে এবং ক্যাপচার করা কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে ইউরিয়া সারের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে (প্রায় ১০ শতাংশ)।
→ এটি দেশে ‘অত্যাধুনিক, শক্তি সাশ্রয়ী ও সবুজ’ সার কারখানা, যা ইউরিয়া সারের আমদানি কমিয়ে দেবে এবং কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে।
তথ্যসূত্র – বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ওয়েবসাইট ও পত্রিকার রিপোর্ট।
প্রশ্ন ৮৯. কোন অনুচ্ছেদ মূলে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি পরিবর্তনযোগ্য নয়?
ক) অনুচ্ছেদ ৭ খ) অনুচ্ছেদ ৮
গ) অনুচ্ছেদ ৭(ক) ঘ) অনুচ্ছেদ ৭(খ)
সঠিক উত্তর: ঘ) অনুচ্ছেদ ৭(খ)
Live MCQ Analytics: Right: 49%; Wrong: 26%; Unanswered: 24%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ অনুচ্ছেদ ৭(খ) মূলে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলি পরিবর্তনযোগ্য নয়।
→ অনুচ্ছেদ ৭(খ) সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমুহের বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোন পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে।]
♦ অনুচ্ছেদ:
– অনুচ্ছেদ ১ – প্রজাতন্ত্র।
– অনুচ্ছেদ ২ – প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা।
– অনুচ্ছেদ ৩ – রাষ্ট্রভাষা।
– অনুচ্ছেদ ৪ – জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক।
– অনুচ্ছেদ ৫(১) – অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ঢাকা।
– অনুচ্ছেদ ৫(২) – অনুযায়ী রাজধানীর সীমানা আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে।
– অনুচ্ছেদ ৬ – নাগরিকত্ব।
– অনুচ্ছেদ ৭ – সংবিধানের প্রাধান্য।
– অনুচ্ছেদ ৭ক। সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ।
– অনুচ্ছেদ ৭খ। সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য।
– অনুচ্ছেদ ৮ – রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।
– অনুচ্ছেদ ৯ – জাতীয়তাবাদ।
– অনুচ্ছেদ ১০ – সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি।
তথ্যসূত্র – বাংলাদেশের সংবিধান।
প্রশ্ন ৯০. বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষাকর্তা-
ক) প্রেসিডেন্ট খ) জাতীয় সংসদ
গ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ঘ) হাই কোর্ট
সঠিক উত্তর: গ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
Live MCQ Analytics: Right: 74%; Wrong: 12%; Unanswered: 13%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষাকর্তা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।
♦ সংবিধানের রক্ষক:
→ বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক সুপ্রিম কোর্ট।
→ সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক।
→ তাই এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী অপরিসীম।
→ সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট দেশের সকল আদালতের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
→ সংবিধান বহির্ভূত সব কিছুকেই সুপ্রীম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করতে পারে।
→ সুপ্রীম কোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক ও সংবিধানের রক্ষক।
♦ উল্লেখ্য:
→ বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় গণপরিষদের মাধ্যমে।
→ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয়।
→ সংবিধান কার্যকর হয় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
→ সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল একটি কমিটি গঠন করা হয়।
→ এই কমিটির মোট সদস্য ছিল ৩৪ জন।
→ এই কমিটির প্রধান বা সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন।
→ সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু।
তথ্যসূত্র – বাংলাদেশের সংবিধান ও বিবিএস প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ স্টাডিজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ৯১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য সংবিধানের যে সংশোধন বাতিল করতে হবে-
ক) পঞ্চদশ খ) দ্বাদশ গ) একাদশ ঘ) ত্রয়োদশ
সঠিক উত্তর: ক) পঞ্চদশ
Live MCQ Analytics: Right: 67%; Wrong: 16%; Unanswered: 16%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছিল।
→ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধন বাতিল করতে হবে।
♦ পঞ্চদশ সংশোধনী:
→ ২০১১ সালের ৩০ জুন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।
→ রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সংযোজন করা হয়।
♦ পঞ্চদশ (১৫তম) সংশোধনী এর বিষয়বস্তু:
• তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল;
• দলীয় সরকারের অধীন মেয়াদ শেষ হবার আগের ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান;
• সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ থেকে ৫০ করা;
• ৪৭ এর ৩ অনুচ্ছেদে যুদ্ধাপরাধ বা মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য “অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি বা সংগঠন” এর বিচার করার বিধান সংযুক্ত করা;
• জরুরী অবস্থার মেয়াদ অনধিক ১২০ দিন করা হয়;
• সংবিধানে নতুন তিনটি তফসিল যুক্ত করা হয়- যথা পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম।
⇒ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলসংক্রান্ত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আংশিক অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।
→ বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ও গণভোট পদ্ধতি বাতিল করে সংবিধানের যে পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয়েছিলো সেটিকে আংশিক বাতিল করেছে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ।
→ এই সংশোধনীতে ৫৪টি পরিবর্তন আনা হয়েছিলো।
→ আদালত পঞ্চদশ সংশোধনীর মোট ছয়টি বিধান বাতিল করেছে।
তথ্যসূত্র – ১৯ ডিসেম্বর ২০২১, বিবিসি বাংলা ও ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪, বিবিসি বাংলা।
প্রশ্ন ৯২. জুলাই শহিদ দিবস কোনটি?
ক) ০১ জুলাই খ) ২৯ জুলাই
গ) ০৫ আগস্ট ঘ) ১৬ জুলাই
সঠিক উত্তর: ঘ) ১৬ জুলাই
Live MCQ Analytics: Right: 75%; Wrong: 11%; Unanswered: 12%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ♦ জুলাই শহীদ দিবস:
→ ১৬ জুলাইকে ‘জুলাই শহীদ দিবস‘ হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
→ ২ জুলাই, ২০২৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক পরিপত্রে এ ঘোষণা দেয়া হয়।
→ ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে রংপুরে পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদের নিহত হওয়ার দিনটি স্মরণে এ দিবস ঘোষণা করা হয়।
→ দিনটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসের তালিকায় ‘খ’ শ্রেণিভুক্ত দিবস -হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
♦ উল্লেখ্য:
→ গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন ৫ আগস্টকে ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস’ ঘোষণা করা হয়েছে।
→ ৫ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস ‘ক’ শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।
তথ্যসূত্র – মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ৯৩. বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কবে শপথ গ্রহণ করেন?
ক) ২০২৪ সালের ০৫ আগস্ট খ) ২০২৪ সালের ০৮ আগস্ট
গ) ২০২৪ সালের ০৬ আগস্ট ঘ) ২০২৪ সালের ০৯ আগস্ট
সঠিক উত্তর: খ) ২০২৪ সালের ০৮ আগস্ট
Live MCQ Analytics: Right: 83%; Wrong: 3%; Unanswered: 12%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন ০৮ আগস্ট, ২০২৪ সাল।
♦ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার:
→ ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে।
→ ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার শপথ গ্রহণ করে।
→ এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস।
→ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে শপথ বাক্য পাঠ করান: রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।
→ শপথ গ্রহণের স্থান: বঙ্গভবন।
তথ্যসূত্র – মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পত্রিকা রিপোর্ট।
প্রশ্ন ৯৪. বাংলাদেশে মোট কতবার জরুরি অবস্থা জারী করা হয়েছে?
ক) ৫ বার খ) ৩ বার গ) ৪ বার ঘ) ৭ বার
সঠিক উত্তর: ক) ৫ বার
Live MCQ Analytics: Right: 21%; Wrong: 28%; Unanswered: 49%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ বাংলাদেশে মোট ৫ বার জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।
♦ জরুরি অবস্থা:
→ সাধারণভাবে বলা যায় জরুরি অবস্থা বলতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থে কোনো আকস্মিক সংকটকালীন অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য কতিপয় মৌলিক অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা বোঝায়।
→ ১৯৭৩ সালে ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরী অবস্থার বিধান সংযুক্ত করা হয় ।
→ এ সংবিধানের ১৪১(ক), ১৪১(খ) ও ১৪১(গ) অনুচ্ছেদের আওতায় দেশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবনে হুমকির কারণে জরুরি অবস্থা (সর্বাধিক ১২০ দিনের জন্য) ঘোষিত হতে পারে।
→ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫ বার জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছে। যথা
১. ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা মোকাবেলা করার জন্য জরুরী অবস্থা জারি করা হয়।
২. জিয়াউর রহমান খুন হলে উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি হয়ে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে জরুরী অবস্থা জারি করেন।
৩. ১৯৮৭ সালের ২৭শে নভেম্বর জেনারেল এরশাদ জরুরী অবস্থা জারি করেন।
৪. ১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর জেনারেল এরশাদ দ্বিতীয়বার জরুরী অবস্থা জারি করেন।
৫. ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দীন আহম্মেদ জরুরী অবস্থা জারি করেন। এই দিনটি ১/১১ নামে পরিচিত।
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, এসএসএইচএল, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ৯৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল কত সালে আইনে পরিণত হয়?
ক) ০৭ মার্চ ১৯১৭ খ) ১৮ মার্চ ১৯২০
গ) ২১ মার্চ ১৯১৯ ঘ) ১১ মার্চ ১৯১৮
সঠিক উত্তর: খ) ১৮ মার্চ ১৯২০
Live MCQ Analytics: Right: 20%; Wrong: 7%; Unanswered: 72%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল আইনে পরিণত হয় ১৮ মার্চ, ১৯২০ সালে।
♦ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:
→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রাচীনতম, সর্ববৃহৎ এবং উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান।
→ ১৯২১ সালের ১ জুলাই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।
→ ঢাকার রমনা এলাকার প্রায় ৬০০ একর জমি নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।
→ এর প্রাথমিক অবকাঠামোর বড় একটি অংশ গড়ে উঠে ঢাকা কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কলেজ ভবনের (বর্তমান কার্জন হল) উপর ভিত্তি করে।
→ ৩টি অনুষদ (কলা, বিজ্ঞান ও আইন), ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক, ৮৪৭ জন ছাত্রছাত্রী এবং ৩টি আবাসিক হল নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে।
♦ উপাচার্যগণ:
→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন স্যার ফিলিপ জোসেফ হার্টগ।
→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী উপাচার্য ছিলেন স্যার এ.এফ রহমান।
→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। (সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
তথ্যসূত্র – ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট ও বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ৯৬. একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক দুটোই পেয়েছেন-
ক) ভাস্কর শামীম শিকদার খ) ভাস্কর হামিদুর রহমান
গ) ভাস্কর নিতুন কুণ্ডু ঘ) ভাস্কর নভেরা আহমেদ
সঠিক উত্তর: ঘ) ভাস্কর নভেরা আহমেদ
Live MCQ Analytics: Right: 32%; Wrong: 18%; Unanswered: 48%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ নভেরা আহমেদ ১৯৯৭ সালে একুশে পদক ও ২০২৫ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক লাভ করেন ।
♦ নভেরা আহমেদ:
→ নভেরা আহমেদ ছিলেন বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান ভাস্কর।
→ বিংশ শতাব্দীর প্রথম বাংলাদেশী আধুনিক ভাস্কর হিসেবে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেন।
→ ১৯৯৫ সালে তিনি ‘হিউমানিটি’ শিরোনামে একটি প্রশংসিত শিল্পকর্ম তৈরি করেন।
→ তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি ‘নিঃসঙ্গ’-১৯৮৯ সালে নির্মিত এটি বাংলাদেশের প্রথম নগ্ন নারী অবয়ব ভাস্কর্য বলে বিবেচিত।
→ ২০১২ সালে আঁকা তার অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে ‘আত্মা’, ‘স্নান’ এবং ‘কক্সবাজার’।
→ তার অসামান্য শিল্পকর্ম ও অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে তাকে একুশে পদ এবং ২০২৫ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করে।
উল্লেখ্য:
→ ভাস্কর শামীম শিকদার একুশে পদক লাভ করেন ২০০০ সালে।
→ ভাস্কর নিতুন কুণ্ডু একুশে পদক লাভ করেন ১৯৯৭ সালে।
তথ্যসূত্র – প্রথম আলো ও বণিক বার্তা পত্রিকা রিপোর্ট।
প্রশ্ন ৯৭. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো-
ক) বিকেন্দ্রীভূত খ) ফেডারেল
গ) রাজতান্ত্রিক ঘ) কেন্দ্রীভূত
সঠিক উত্তর: ঘ) কেন্দ্রীভূত
Live MCQ Analytics: Right: 53%; Wrong: 25%; Unanswered: 20%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো:
– বাংলাদেশে প্রশাসনিক কাঠামো মূলত কেন্দ্রীভূত।
– অধিকাংশ ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে।
– স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা হলেও কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্প্রসারিত অঙ্গ হিসেবেই পরিচালিত হয়।
– এর ফলে স্থানীয় সরকারের স্বতন্ত্রতা ও কার্যক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে।
• বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর দুইটি স্তর রয়েছে।এগুলো হলো-
ক) কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো এবং
খ) মাঠ পর্যায় প্রশাসনিক কাঠামো।
এই কাঠামোর প্রশাসনিক ইউনিটগুলো হচ্ছে
– বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা।
এছাড়াও,
বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো:
– বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর প্রথম স্তর হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো (সচিবালয়) যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর নিয়ে গঠিত।
– সচিবালয় হলো প্রশাসনিক কার্যাবলি এবং সমস্ত সরকারি কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র।
– সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত Rules of Business এর নিয়ম অনুসারে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের কার্যাদি নির্ধারণ করা হয়।
– এছাড়াও সচিবালয়ের নির্দেশাবলী (Secretariate Instructions) নামে আলাদা একটি ডকুমেন্টও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কার্যাবলি নির্ধারণ করে থাকে।
– সচিব একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হন এবং তিনিই এর শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন।
অন্যদিকে,
বাংলাদেশের মাঠ পর্যায় প্রশাসনিক কাঠামো (স্থানীয় সরকার):
– বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর হলো মাঠ প্রশাসন।
– মাঠ প্রশাসনের প্রধান দু’টি ক্ষেত্র হচ্ছে জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন।
– জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয় এবং নেতৃত্বে রয়েছে বিভাগীয় প্রশাসন।
– এটি মূলত প্রশাসন বা আমলাতন্ত্রের বিন্যাস।
– অন্যদিকে সরকারের কাঠামোগত বিন্যাসে মাঠ পর্যায়ে রয়েছে স্থানীয় সরকার।
– স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ।
– রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও নাগরিকসেবা নিশ্চিতকরণ এবং কল্যাণমুখী সমাজ গঠনে স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনের যুগপৎ এবং সমন্বিত কর্মসূচির বিকল্প নেই।
উৎস: বাংলাদেশ স্টাডিজ, বিবিএ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।[লিংক]
প্রশ্ন ৯৮. টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরি করেন-
ক) সাকিব-আল-হাসান খ) মমিনুল হক
গ) নাজমুল হোসেন শান্ত ঘ) মুশফিকুর রহিম
সঠিক উত্তর: ঘ) মুশফিকুর রহিম
Live MCQ Analytics: Right: 74%; Wrong: 8%; Unanswered: 17%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:⇒ টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন মুশফিকুর রহিম।
টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল:
– টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে: ২০০০ সালে।
– সর্বপ্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে ২০০০ সালের ১০ই নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে।
– প্রথম টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন নাইমুর রহমান।
– প্রথম টেস্ট জয় পায় ২০০৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চট্টগ্রামে।
– টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরি করেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
– টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন মুশফিকুর রহিম।
– টেস্টে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ব্যক্তিগত হাজার রান সংগ্রাহক হাবিবুল বাশার।
– বাংলাদেশ তার শততম টেস্ট খেলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
– ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়।
– শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করেন বাংলাদেশের সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।
অন্যদিকে,
– মোহাম্মদ আশরাফুল টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেন।
– ২০০১ সালে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার টেস্টের তৃতীয় দিনে আশরাফুল সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড করেন।
উৎস: ESPNcricinfo.com এবং The Business Standard পত্রিকা রিপোর্ট।
প্রশ্ন ৯৯. ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় কোন পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ছিল?
ক) দৈনিক ইত্তেফাক খ) বাংলাদেশ অবজার্ভার
গ) দৈনিক গণকণ্ঠ ঘ) বাংলাদেশ টাইমস
সঠিক উত্তর: গ) দৈনিক গণকণ্ঠ
Live MCQ Analytics: Right: 23%; Wrong: 22%; Unanswered: 53%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ⇒ ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ছিল।
♦ সংবাদপত্র নিষিদ্ধকরণ:→ ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়।
→ বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
→ বাকশাল সরকার সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নেয়।
→ ৪টি সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা ‘দ্য অভজারভার, দ্য বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক রেখে দেশের ২৯টি দৈনিক ও ১৩৮টি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
→ এই নিষেধাজ্ঞা গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বড় আঘাত হানে।
→ এর ফলে সংবাদপত্র হয়ে ওঠে সরকারি প্রচারণার মাধ্যম মাত্র।
তথ্যসূত্র – পত্রিকার রিপোর্ট।
প্রশ্ন ১০০. ওয়াসফিয়া নাজরীন বিখ্যাত-
ক) অ্যাথলেট হিসেবে খ) ক্রিকেটার হিসেবে
গ) এভারেস্টজয়ী হিসেবে ঘ) নারী উদ্যোক্তা হিসেবে
সঠিক উত্তর: গ) এভারেস্টজয়ী হিসেবে
Live MCQ Analytics: Right: 76%; Wrong: 5%; Unanswered: 18%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ওয়াসফিয়া নাজরীন:
– এভারেস্ট বিজয়ী পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাজরীন।
– বাংলাদেশের পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাজরীন ‘সেভেন সামিট’-এর কৃতিত্ব অর্জন করেন।
– বাংলাদেশের প্রথম পর্বতারোহী হিসেবে সাত মহাদেশের সাতটি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় (সেভেন সামিট) করেন ওয়াসফিয়া নাজরীন।
– ২০১২ সালের ২৬ মে তিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন।
– এর আগে তিনি আফ্রিকার মাউন্ট কিলিমানজারো, এশিয়ার মাউন্ট এভারেস্ট, অ্যান্টার্কটিকার মাউন্ট ভিনসন, ইউরোপের এলব্রুস, উত্তর আমেরিকার মাউন্ট ডেনালি, দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাকোংকাগুয়া পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন।
– আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী গ্রুপ কেয়ার (CARE) এর হয়ে ওয়াসফিয়া নাজরীন কাজ করেছেন।
– তিনি ২০১৪ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির বর্ষসেরা অভিযাত্রীর খেতাব পেয়েছেন।
এছাড়াও,
– এখন পর্যন্ত ছয়জন বাংলাদেশি এভারেস্ট জয় করেছেন। তাঁরা হলেন মুসা ইব্রাহীম, এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার, ওয়াসফিয়া নাজরীন, মো. খালেদ হোসাইন, বাবর আলী।
– ১ম বাংলাদেশি: মুসা ইব্রাহিম, ২০১০ সালের ২৩ মে।
– ২য় বাংলাদেশি: এম এ মুহিত, ২০১১ সালের ২১ মে।
– ৩য় বাংলাদেশি: নিশাত মজুমদার, ২০১২ সালের ১৯ মে।
– ৪র্থ বাংলাদেশি: ওয়াসফিয়া নাজরিন, ২০১২ সালের ২৬ মে।
– ৫ম বাংলাদেশি: বাবর আলী, ২০২৪ সালের ১৯ মে।
অন্যদিকে,
– মো. খালেদ হোসেন, ২০১৩ সালের ২০ মে মাউন্ট এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেন।
– তবে চূড়া থেকে নামার পথে দুর্ঘটনায় মারা যান তিনি।
– তাই এভারেস্ট জয়ী হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারেননি।
উৎস: প্রথম আলো এবং BBC পত্রিকা রিপোর্ট।
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি
প্রশ্ন ১০১. সম্প্রতি পেরুতে খুঁজে পাওয়া ৩৫০০ বছরের পুরোনো শহরের নাম কী?
ক) মাচুপিচু খ) কোরাল গ) পেনিকো ঘ) কুস্কো
সঠিক উত্তর: গ) পেনিকো
Live MCQ Analytics: Right: 16%; Wrong: 33%; Unanswered: 50%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:◉ সম্প্রতি পেরুতে খুঁজে পাওয়া ৩৫০০ বছরের পুরোনো শহরের নাম পেনিকো।
পেরুতে ৩৫০০ বছরের পুরোনো প্রাচীন নগরী পেনিকো:
– জুলাই, ২০২৫- এ পেরুতে ৩ হাজার ৫০০ বছরের বেশি আগে সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা একটি প্রাচীন শহরের খোঁজ পাওয়া গেছে।
– পেনিকো নামের এই প্রাচীন শহরের খোঁজ দিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা।
– আট বছর ধরে খনন ও সংরক্ষণের পর এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় স্থানটির বিস্তারিত বিবরণ জানানো হয়।
⇒ পেনিকো নগরটি পেরুর রাজধানী লিমার উত্তরে হুয়াওরা প্রদেশে অবস্থিত।
– আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০০ সালে পেনিকো শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
– শহরটি রাজধানী লিমা থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উত্তর দিকে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ মিটার (প্রায় ২০০০ ফুট) উঁচুতে অবস্থিত।
– এই নগরকেন্দ্রটি কারাল সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। কারাল শহরে রয়েছে ৩২টি স্মৃতিস্তম্ভ, যার মধ্যে রয়েছে বিশাল পিরামিড আকৃতির স্থাপনা, উন্নত সেচব্যবস্থা এবং প্রাচীন নগর জীবনযাপন। বিশ্বাস করা হয়, এই সভ্যতা ভারত, মিসর, সুমের এবং চীনের মতো প্রাচীন সভ্যতাগুলোর সঙ্গে কোনো সংযোগ ছাড়াই নিজস্বভাবে গড়ে উঠেছিল।
→ কৌশলগত অবস্থানের কারণে এটি সুপে ও হুয়াওরার উপকূল, পার্বত্য শহরগুলোসহ আন্দিজ-অ্যামাজনীয় এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদেরও সংযুক্ত করত।’
– পেনিকোতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৮টি কাঠামো চিহ্নিত করা হয়েছে। যার মধ্যে উপাসনালয়, বসবাসযোগ্য ঘরবাড়ি এবং ধর্মীয় কেন্দ্রও রয়েছে।
– যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা কারালের পতনের পর পেনিকোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রঙিন লোহা আকরিক হেমাটাইট বাণিজ্যের কারণে পেনিকোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই রঙিন লোহা আন্দিজদের প্রতীকী রং হিসেবে বিবেচিত হতো।
উল্লেখ্য,
– পেরুতে এর আগেও বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে। যেমন আন্দিজ পর্বতের ইনকা দুর্গ ‘মাচু পিচু’ এবং উপকূলীয় মরুভূমির ‘নাজকা রেখা’।
উৎস: i) প্রথম আলো। ii) BBC.
প্রশ্ন ১০২. ১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইনকে বিভাজনের পরিকল্পনা জাতিসংঘের কোন প্রস্তাবের মাধ্যমে গৃহীত হয়?
ক) ১৮০ নং প্রস্তাব খ) ১৮১ নং প্রস্তাব
গ) ১৬০ নং প্রস্তাব ঘ) ১৬১ নং প্রস্তাব
সঠিক উত্তর: খ) ১৮১ নং প্রস্তাব
Live MCQ Analytics: Right: 15%; Wrong: 6%; Unanswered: 77%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ ১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইনকে বিভাজনের পরিকল্পনা জাতিসংঘের ১৮১ নং প্রস্তাবের মাধ্যমে গৃহীত হয়।
জাতিসংঘের রেজ্যুলেশন ১৮১ (UN Resolution 181):
– জাতিসংঘের রেজ্যুলেশন ১৮১ “Partition Plan for Palestine” নামে পরিচিত।
– ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রেজুলেশন-১৮১ এর আওতায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে ভাগ করে একটি ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল ও একটি আরব রাষ্ট্র ফিলিস্তিন করার প্রস্তাব করা হয়।
– গৃহীত হয়: ২৯ নভেম্বর, ১৯৪৭।
⇒ ফিলিস্তিনের আরব জনগণ এই পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এটি ফিলিস্তিনের আরব জনগণের জন্য একটি বড় বিপর্যয় ছিল।
– ফলাফল: ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়, যা ইসরায়েলী বাহিনী এবং আরব দেশগুলির মধ্যে সংঘর্ষে পরিণত হয়। যুদ্ধের ফলে প্রায় ৭ লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী হয়ে যায়, এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষের ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়। ফিলিস্তিনিরা এই ঘটনার পর থেকেই তাদের “স্বাধীনতা সংগ্রাম” শুরু করে যা আজও চলমান।
উল্লেখ্য,
→ ফিলিস্তিন মুক্তি সংগঠন (PLO) প্রতিষ্ঠা:
– ১৯৬৪ সালে আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলন চলার সময় ফিলিস্তিনিরা একত্র হয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠন করে। এর নাম দেওয়া হয় প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)।
– ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েল বিজয়ী হওয়ার পর সামরিক নেতা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীন সংগঠন ফাতাহ পিএলওতে যুক্ত হয় এবং সংগঠনটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে শুরু করে।
– ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা দখল করে নেয়। এরপর বছরের পর বছর ধরে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘাত থামাতে ১৯৯৩ সালে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন অসলো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
– অসলো চুক্তির মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ (পিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। চুক্তির আওতায় ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার কিছু অংশের ওপর সীমিত কর্তৃত্ব দেওয়া হয়।
উৎস: i) UN ওয়েবসাইট। ii) Britannica.
প্রশ্ন ১০৩. নিম্নের কোন দেশটি ‘গোলান হাইটস্‘ বিরোধের একটি পক্ষ?
ক) লেবানন খ) জর্ডান
গ) সিরিয়া ঘ) সৌদি আরব
সঠিক উত্তর: গ) সিরিয়া
Live MCQ Analytics: Right: 53%; Wrong: 7%; Unanswered: 39%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ সিরিয়া ‘গোলান হাইটস্‘ বিরোধের একটি পক্ষ।
গোলান মালভূমি:
– গোলান মালভূমি সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত প্রায় ১৮০০ বর্গকিলোমিটার (প্রায় ১০০০ বর্গমাইল) আয়তনের এক পাথুরে মালভূমি।
– সিরিয়া ও ইসরায়েলের মাঝখানে বাফার জোন (সংঘাতমুক্ত বিশেষ অঞ্চল) বলা হতো গোলান মালভূমিকে।
– এর উত্তরে লেবানন এবং দক্ষিণে জর্ডান অবস্থিত।
– গোলান মালভূমি নিয়ে সিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।
⇒ ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত গোলান মালভূমি সিরিয়ার একটি অংশ ছিল।
– ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধের সময় গোলান মালভূমিজুড়ে ইসরায়েলের ওপর হামলা চালায় সিরিয়া। কিন্তু ইসরায়েল পাল্টা প্রতিরোধ নেয় এবং গোলানের ১২০০ বর্গকিলোমিটার (৪৬০ বর্গমাইল) এলাকা দখল করে নেয়।
– ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের (যা ইয়োম কিপুর যুদ্ধ নামেও পরিচিত) সিরিয়া গোলানের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।
– ১৯৭৪ সালে দুই দেশই অস্ত্রবিরতিতে সই করে। চুক্তির শর্ত মেনে দুই পক্ষকেই মালভূমির ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি লম্বালম্বি এলাকা ছেড়ে নিজ নিজ বাহিনীকে সরিয়ে নিতে হয়। এই এলাকাটি পরিচিত ‘এরিয়া অব সেপারেশন’ নামে। এরপর সেখানে জাতিসংঘ নিয়োজিত ‘ডিজএনগেজমেন্ট অবজারভার ফোর্স’ মোতায়েন করা হয় অস্ত্রবিরতির বিষয়টিতে নজর রাখার জন্য।
– ১৯৮১ সালে ইসরায়েলি সরকার ঘোষণা করে যে গোলান মালভূমি এলাকাটি ইসরায়েলের একটি অংশ।
⇒ এই এলাকায় ইসরায়েলের সার্বভৌমত্বে কখনও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলেনি।
– তবে মার্কিন নীতি ভঙ্গ করে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই দখলদারিত্বে স্বীকৃতি দেন।
এছাড়াও,
– গোলান মালভূমিতে সিরিয়া-ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি রেখা ‘পার্পল লাইন’ নামে পরিচিত।
উৎস: i) Britannica. ii) BBC.
প্রশ্ন ১০৪. নিচের কোন সভ্যতার সময়কালে ওজন পরিমাপ ও দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল?
ক) সিন্ধু সভ্যতা খ) মিশরীয় সভ্যতা
গ) গ্রিক সভ্যতা ঘ) অ্যাসেরীয় সভ্যতা
সঠিক উত্তর: ক) সিন্ধু সভ্যতা
Live MCQ Analytics: Right: 39%; Wrong: 24%; Unanswered: 35%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ সিন্ধু সভ্যতার সময়কালে ওজন পরিমাপ ও দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল।
সিন্ধু সভ্যতার পরিমাপ পদ্ধতি:
– সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা।
– সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা দ্রব্যের ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিল। তাদের এই পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে বিবেচিত। তারা বিভিন্ন দ্রব্য ওজনের জন্য নানা মাপের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বাটখারা ব্যবহার করত। দাগ কাটা স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল।
– মহেঞ্জোদারো নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বাণিজ্যের অবস্থা যে ভাল ছিল তা এই সভ্যতায় পাওয়া নিদর্শন থেকে জানা যায়। ওজনের জন্য নগরবাসীরা বিভিন্ন পরিমাপের বাটখারা ব্যবহার করতো। ছোট বাটখারাগুলোর আকৃতি ছিল চারকোণা। আর বড়গুলো ছিল গোলাকার। কোন কোনটি ছিল কিছুটা কৌণিক। সাধারণত পাথর দিয়ে বাটখারা তৈরি করা হতো। বাটখারাগুলোর ওজন সমান থাকায় ধারণা করা হয় ওজনের ব্যাপারে সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা সতর্ক ছিল। বড় বড় এবং ভারি জিনিস ওজন করার জন্য মহেঞ্জোদারোর নগরবাসীরা ব্রোঞ্জের স্কেল ব্যবহার করতো। ভারি বস্তু ওজন করার জন্য কাঠখণ্ড ব্যবহার করা হতো। কাঠখন্ডের এক প্রান্তে দ্রব্য বেঁধে ওজন করা হতো। কোন জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপার জন্য মহেঞ্জোদারোর মানুষেরা স্কেল ব্যবহার করত। তাদের স্কেলের দৈর্ঘ্য ছিল ২০.৬২ ইঞ্চির সমান। পরিমাপদন্ডে নির্দিষ্ট ঘর কাটা হতো।
⇒ সিন্ধু সভ্যতা:
– পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদারোতে এবং পাঞ্জাবের হরপ্পায় এই সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়।
– সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতিকে অনেক সময়ে হরপ্পা সংস্কৃতি বা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়ে থাকে।
– সিন্ধু সভ্যতার প্রকৃত নির্মাতা হচ্ছে দ্রাবিড়রা। এই সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল দ্রাবিড়, অস্ট্রোলয়েড, ভূ-মধ্যসাগরীয় মঙ্গোলীয় এবং আলপানীয় গোত্রভুক্ত। এ কারণেই সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতি দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতি নামে পরিচিত।
– প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেন ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয়েছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো প্লাবিত হয় এই বন্যায়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর এভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, ক্রমাগত বন্যায় শহর দু’টি ধীরে ধীরে মাটির নীচে চাপা পড়েছে।
উৎস: i) বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ii) Britannica. iii) ইতিহাস ১ম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ১০৫. ন্যাটো (NATO) চার্টারের কোন ধারায় সম্মিলিত প্রতিরক্ষার কথা উল্লেখ আছে?
ক) আর্টিকেল-২ খ) আর্টিকেল-৩
গ) আর্টিকেল-৫ ঘ) আর্টিকেল-৬
সঠিক উত্তর: গ) আর্টিকেল-৫
Live MCQ Analytics: Right: 58%; Wrong: 6%; Unanswered: 35%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ ন্যাটো (NATO) চার্টারের আর্টিকেল-৫-এ সম্মিলিত প্রতিরক্ষার কথা উল্লেখ আছে।
• অনুচ্ছেদ ৫: সম্মিলিত প্রতিরক্ষা
– NATO র অনুচ্ছেদ ৫- “যদি একটি ন্যাটো মিত্র সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হয়, তবে জোটের প্রতিটি সদস্য এই সহিংসতার কাজটিকে সমস্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ হিসাবে বিবেচনা করবে এবং মিত্রদের আক্রমণে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।”
– অর্থাৎ সদস্যদেশগুলো সম্মিলিতভাবে একে অপরকে সুরক্ষা দেবে। ন্যাটোর মূল ভিত্তি ধরা হয় এ ধারাকে।
উল্লেখ্য,
– ন্যাটোর ইতিহাসে একবার মাত্র ন্যাটোর আর্টিকেল-৫ কার্যকর করা হয়েছে। নাইন ইলেভেনে টুইন টাওয়ার হামলার পর ২০০১ সালে এই আর্টিকেল অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এটির ভিত্তিতেই সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আফগানিস্তানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।
⇒ ন্যাটোর অনুচ্ছেদ: ন্যাটো প্রতিষ্ঠার চুক্তিটি ছোট। মাত্র ১৪টি ধারার। এগুলো হলো:
– অনুচ্ছেদ ১: শান্তিপূর্ণ সমাধান,
– অনুচ্ছেদ ২: বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক,
– অনুচ্ছেদ ৩: প্রতিরক্ষা সক্ষমতা,
– অনুচ্ছেদ ৪: পরামর্শ,
– অনুচ্ছেদ ৫: সম্মিলিত প্রতিরক্ষা,
– অনুচ্ছেদ ৬: আক্রমণের সংজ্ঞা ,
– অনুচ্ছেদ ৭: জাতিসংঘ সনদের বাধ্যবাধকতা,
– অনুচ্ছেদ ৮: অ-দ্বন্দ্বমূলক সম্পৃক্ততা,
– অনুচ্ছেদ ৯: বাস্তবায়ন পরিষদ,
– অনুচ্ছেদ ১০: অতিরিক্ত পক্ষসমূহ,
– অনুচ্ছেদ.১১: চুক্তি অনুমোদন এবং প্রয়োগ,
– অনুচ্ছেদ ১২: চুক্তি পর্যালোচনা,
– অনুচ্ছেদ ১৩: জোটের সদস্যতা ত্যাগ,
– অনুচ্ছেদ ১৪: চুক্তির অন্যান্য সংস্করণের গ্রহণযোগ্যতা।
⇒ NATO:
– NATO-এর পূর্ণরূপ:North Atlantic Treaty Organisation অথবা উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট।
– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে গঠন করা হয় সামরিক জোট NATO।
– প্রতিষ্ঠিত হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯।
– প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: ১২টি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে ও পর্তুগাল)।
– বর্তমান সদস্য: ৩২টি।
– সদর দপ্তর: ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
– বর্তমান মহাসচিব: মার্ক রুট্টে।
– মুসলিম দেশ: আলবেনিয়া ও তুরস্ক।
– সর্বশেষ ৩২তম সদস্য হলো সুইডেন।
উৎস: NATO ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১০৬. রোম সংবিধি (Rome Statute) এর ফলে কোন সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) International Court of Justice (ICJ)
খ) International Criminal Court (ICC)
গ) International Atomic Energy Agency (IAEA)
ঘ) European Union (EU)
সঠিক উত্তর: খ) International Criminal Court (ICC)
Live MCQ Analytics: Right: 32%; Wrong: 34%; Unanswered: 32%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ রোম সংবিধি (Rome Statute) এর ফলে International Criminal Court (ICC) প্রতিষ্ঠিত হয়।
রোম সংবিধি (Rome Statute):
– রোম সংবিধি হলো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (International Criminal Court – ICC) প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। – ১৯৯৮ সালে রোম সংবিধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় আইসিসি।
– ১৯৯৮ সালের ১৫ জুন – ১৭ জুলাই ইতালির রোমে বিশ্বের ১২০টি দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কূটনীতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১২০-৭ ভোটের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালত সংবিধি বা রোম সংবিধি গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।
– পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাষ্ট্র কর্তৃক সংবিধিটি অনুমোদিত হওয়ায় ২০০২ সালের ১ জুলাই থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কার্যকারিতা লাভ করে।
– মূলত আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারে দেশীয় বিচারব্যবস্থার সমর্থনে বা এটার পরিপূরক (কমপ্লিমেন্টারি) হিসেবে কাজ করার জন্য আইসিসি তৈরি হয়েছিল (রোম সংবিধির প্রস্তাবনা এবং অনুচ্ছেদ ১ ও ১৭)।
– রোম সংবিধিতে মোট ১৩টি অধ্যায় এবং ১২৮টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।
⇒ ICC:
– ICC-এর পূর্ণরূপ: International Criminal Court.
– ICC বা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত।
– প্রতিষ্ঠিত হয়: ১৭ জুলাই, ১৯৯৮ (রোম সংবিধির মাধ্যমে)।
– কার্যক্রম শুরু করে: ১ জুলাই, ২০০২।
– সদরদপ্তর: দ্য হেগ, নেদারল্যান্ডস।
– এর সদস্য: ১২৫টি [১২৫তম সদস্য: ইউক্রেন]।
– বর্তমান প্রেসিডেন্ট: তোমোকো আকানেকে (২০২৪-২০২৭ সাল)। প্রেসিডেন্সির সদস্যরা অবিলম্বে তিন বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হন।
উল্লেখ্য,
– ICC-এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী, ICCতে চার ধরনের অপরাধের বিচার করা যায়: জেনোসাইড, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ, আগ্রাসনের অপরাধ।
– ১৯৯৮ সালের মূল আইনে প্রথম তিনটি অপরাধের কথা বলা ছিল। ২০১০ সালে রোম সংবিধিতে সংশোধনীর মাধ্যমে ক্রাইম অব অ্যাগ্রেশন বা আগ্রাসনের অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। এই অপরাধগুলো আদালতে প্রমাণের জন্য এলিমেন্টস অব ক্রাইমস নামে একটা সহয়িকা আছে, যেখানে প্রতিটা অপরাধ প্রমাণের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক উপাদানের কথা বলা আছে। আর বিচারের পদ্ধতিগত দিকগুলো বিষয়ে বিস্তারিত বলা আছে রুলস অব প্রসিডিউর অ্যান্ড এভিডেন্সে।
অন্যদিকে,
– সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনের মাধ্যমে ১৯৪৫ সালে International Court of Justice (ICJ) বা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কাজ বিভিন্ন দেশের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করা।
– ১৯৫৭ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় International Atomic Energy Agency (IAEA) প্রতিষ্ঠিত হয়।
– ১৯৯২ সালে স্বাক্ষরিত ‘ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি’র ভিত্তিতে ইউরোপীয় কমিশন রূপান্তরিত হয়ে ১৯৯৩ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন European Union (EU) হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।
উৎস: International Criminal Court ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১০৭. কোন দেশগুলো মেডিসিন লাইন/সীমানা দ্বারা বিভক্ত?
ক) ব্রাজিল ও বলিভিয়া খ) যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা
গ) জার্মানি ও পোল্যান্ড ঘ) মিশর ও সুদান
সঠিক উত্তর: খ) যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা
Live MCQ Analytics: Right: 11%; Wrong: 22%; Unanswered: 66%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা মেডিসিন লাইন দ্বারা বিভক্ত।
মেডিসিন লাইন/সীমানা (Medicine Line):
– মেডিসিন লাইন (Medicine Line) হলো যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যকার সীমানা।
– বিশেষ করে ৪৯° উত্তর অক্ষরেখা (49th parallel) বরাবর টানা সীমারেখাকে বোঝাতে মেডিসিন লাইন ব্যবহার করা হয়।
– ৪৯° উত্তর অক্ষরেখা (49° N latitude) হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মধ্যে দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক সীমান্তের একটি অংশ যা প্রধানত সোজা রেখা।
– এটি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ অরক্ষিত (unfortified) সীমান্ত হিসেবে পরিচিত।
– এটি প্রায় ৫,৫২৫ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত।
– এই সীমান্ত ১৮৪৬ সালের ওরেগন ট্রিটি (Oregon Treaty) দিয়ে নির্ধারিত হয়।
উল্লেখ্য,
– কানাডার স্থানীয়রা এই লাইনটিকে মেডিসিন লাইন হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন।
অন্যদিকে,
– ওডার-নীস লাইন হলো জার্মানি এবং পোল্যান্ডের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সীমানা।
– ২২° উত্তর অক্ষরেখা (22°N parallel) মিশর এবং সুদানের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সীমানা। এটি হালায়েব ত্রিভুজ (Hala’ib Triangle) নামেও পরিচিত।
উৎস: i) Americas.org, ii) History.com
প্রশ্ন ১০৮. বাংলাদেশ কখন নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য (CEDAW) দূরীকরণ সনদে সম্মতি জানায়?
ক) ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৪ খ) ৬ নভেম্বর ১৯৮৪
গ) ৫ আগস্ট ১৯৮৫ ঘ) ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
সঠিক উত্তর: খ) ৬ নভেম্বর ১৯৮৪
Live MCQ Analytics: Right: 9%; Wrong: 21%; Unanswered: 69%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ ৬ নভেম্বর ১৯৮৪ তারিখে বাংলাদেশ নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য (CEDAW) দূরীকরণ সনদে সম্মতি জানায়।
CEDAW:
– CEDAW-এর পূর্ণরূপ: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women বা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য প্রতিরোধ কনভেনশন।
– গৃহীত হয়: ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে।
– সনদ স্বাক্ষর শুরু হয়: ১ মার্চ, ১৯৮০।
– কার্যকর হয়: ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।
– বর্তমান চেয়ারপারসন: আনা পেলেজ নারভেজ।
– এই সনদে মোট ৩০টি অনুচ্ছেদ আছে। এই অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ৩-১৬ পর্যন্ত মোট ১৪টি নারীর অধিকার সংক্রান্ত এবং বাকীগুলো এব কর্মপন্থা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত।
⇒ CEDAW সনদে মোট ৩০টি অনুচ্ছেদ আছে। অনুচ্ছেদ ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা:
– প্রথম ভাগ (১-১৬): নারী পুরুষের সমতা সর্ম্পকিত,
– দ্বিতীয় ভাগ (১৭-২২): এর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক,
– তৃতীয় ভাগ (২৩-৩০): প্রশাসনিক বিষয়।
⇒ CEDAW কমিটিতে সারা বিশ্ব থেকে নারী অধিকার সংক্রান্ত ২৩ জন বিশেষজ্ঞ রয়েছে। কমিটি সদস্যগণ ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।
– এই কনভেনশন গৃহ নির্যাতন, প্রজনন, আইনগত, রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের সমমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে থাকে।
– কনভেনশনের শর্তানুযায়ী রাষ্ট্রপক্ষসমূহের প্রতি নারীর মৌলিক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; নারী পাচার ও পতিতাবৃত্তিতে নারীর শোষণ রোধ নিশ্চিত করা; রাজনৈতিক ও লোকজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসান; জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন বা বহাল রাখার সমান অধিকার নিশ্চিত করা; শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।
– অন্যান্য ধারায় গ্রামীণ নারীর সমস্যা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং বিবাহ ও পারিবারিক জীবনে নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত বিষয়গুলো রয়েছে।
– কনভেনশনে নারীর নিজ নিজ দেশে রাজনৈতিক ও লোকজীবনে অংশগ্রহণ এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সকল কাজ করার অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য,
– বাংলাদেশ CEDAW অনুমোদন করে ৬ নভেম্বর, ১৯৮৪ সালে।
– বাংলাদেশ সাক্ষরের সময় সনদের অনুচ্ছেদ ২ ও ১৩ (ক) ও অনুঃ ১৬ (১) (গ) (চ) সংরক্ষণ রেখেছিল। পরবর্তীতে ২ এবং ১৬ (১) (গ) সংরক্ষিত রেখে বাকী অনুচ্ছেদগুলো থেকে সংরক্ষণ তুলে নেয়া হয়।
– CEDAW সনদের ২ নম্বর ধারার মূল নির্যাস হচ্ছে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতার নীতি রাষ্ট্রের সংবিধানে অথবা অন্য কোনো আইনে এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকলে তার অন্তর্ভুক্তি এবং আইনের মাধ্যমে এই নীতির বাস্তবায়ন। প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, তা বাতিল বা পরিবর্তন করা এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন এ ক্ষেত্রে দরকার। অর্থাৎ সমতার আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এবং আদালত ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা কার্যকর করা।
– CEDAW সনদের ১৬(১)-এর (গ) ধারায় বলা হয়েছে বিবাহ, বিবাহে পছন্দ-অপছন্দ, বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অধিকার ও দায়দায়িত্বের কথা।
এছাড়াও,
– ৩ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক CEDAW দিবস।
উৎস: i) UN ওয়েবসাইট। ii) CEDAW South Asia ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১০৯. যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত ‘অপারেশন মিডনাইট হ্যামার‘ ইরানে কবে হামলা করে?
ক) ২০ জুন ২০২৫ খ) ২১ জুন ২০২৫
গ) ২২ জুন ২০২৫ ঘ) ২৩ জুন ২০২৫
সঠিক উত্তর: গ) ২২ জুন ২০২৫
Live MCQ Analytics: Right: 27%; Wrong: 28%; Unanswered: 44%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ ২২ জুন ২০২৫ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত ‘অপারেশন মিডনাইট হ্যামার‘ ইরানে হামলা করে।
অপারেশন মিডনাইট হ্যামার (Operation Midnight Hammer):
– ২২ জুন, ২০২৫ তারিখে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় ‘অপারেশন মিডনাইট হ্যামার’ নামে অভিযান পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্র।
– ‘অপারেশন মিডনাইট হ্যামার’ নামে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।
– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, শনিবার (রবিবার তেহরানের সময় ০২:৪০-০৩:০৫) ২২:৪০ GMT থেকে ২৩:০৫ GMT এর মধ্যে তাদের উপর হামলা চালানো হয়েছিল।
– অর্থাৎ ইরানের স্থানীয় সময় রবিবার ২২ জুন, ২০২৫ রাত ০২:৪০ থেকে ০৩:০৫ সময়ে এই হামলা চালানো হয়েছিল।
⇒ প্রায় ২৫ মিনিট দীর্ঘ এই অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের ১২৫টি যুদ্ধবিমান অংশ নিয়েছে।
– যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি থেকে উড্ডয়নের প্রায় ৩৭ ঘণ্টা উড়ে অপারেশন মিডনাইট হ্যামারে অংশ সাতটি বি-২ বোমারু বিমান।
– এই বিমানগুলো ইরানের ৩টি পরমাণু স্থাপনা ফর্দো, ইস্ফাহান এবং নাতাঞ্জ লক্ষ্য করে ১৪টি বাংকার বাস্টার বোমা ছোড়ে।
– প্রতিটি বি-২ বোমারু বিমান দুটি করে বাংকার বিধ্বংসী বোমা বহনে সক্ষম। প্রতিটি বোমার ওজন ৩০ হাজার পাউন্ড।
– এ ছাড়া এই অভিযানে অংশ নেয় জ্বালানি ভরার ট্যাংকার ও নজরদারি বিমান।
উল্লেখ্য,
– যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিটার হেগসেথ বলেছেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি নির্মূল করাই ছিল এই মিশনের লক্ষ্য।
এছাড়াও,
– ১৩ জুন, ২০২৫ তারিখে ইসরায়েল ইরানের কয়েক ডজন পারমাণবিক ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আকস্মিক আক্রমণ চালায়। এই অভিযানের নাম ছিল অপারেশন রাইজিং লায়ন (Operation Rising Lion)।
– ১৩ জুন, ২০২৫ তারিখে ইরানে ইসরাইলের পরিচালিত অভিযান ‘অপারেশন রাইজিং লায়ন’-এর বিপরীতে অপারেশন ট্রু প্রমিজ থ্রি অভিযান পরিচালনা করছে ইরান।
– তারপর থেকে উভয় দেশের মধ্যে বিমান যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।
উৎস: i) CSIS. ii) CNN পত্রিকা।
প্রশ্ন ১১০. ইরানের ফর্দো (Fordow) পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রটি কোন প্রদেশে অবস্থিত?
ক) ইসফাহান খ) ইলাম
গ) বুমেহর ঘ) আলবোজ
সঠিক উত্তর: “বাতিল করা হয়েছে”
Live MCQ Analytics: Right: 0%; Wrong: 0%; Unanswered: 0%; [Total: 0]
ব্যাখ্যা: ◉ ইরানের ফর্দো (Fordow) পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রটি কোম (Qom) প্রদেশে অবস্থিত।
→ ইরানে মোট ৩১টি প্রদেশ রয়েছে। ইরানের ফর্দো পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রটি কোম (Qom) প্রদেশে অবস্থিত।
→ উল্লেখ্য ইস্ফাহান, ইলাম, আলবোজ, বুশেহর প্রদেশগুলো ফর্দো (Fordow) পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্রের নিকটে অবস্থিত নয় তথা এগুলো অন্য প্রদেশ।
♦ উল্লিখিত অপশনগুলোর মধ্যে সঠিক উত্তর না থাকায় প্রশ্নটি বাতিল করা হলো।
ফর্দো (Fordow) পারমাণবিক সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র:
– এই স্থাপনাটি তেহরান থেকে প্রায় ১৬০ কিমি দক্ষিণে কোম শহরের কাছে অবস্থিত পাহাড়ের নিচে নির্মিত সুরক্ষিত স্থাপনা।
– স্থাপনাটির প্রধান কক্ষগুলো মাটির প্রায় ৮০ থেকে ৯০ মিটার নিচে।
– এই কেন্দ্রেও ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করা হয় এবং বলা হয়, এই প্লান্টটি বিমান হামলার বিরুদ্ধে অত্যন্ত সুরক্ষিত।
⇒ ২০০৯ সালের অক্টোবরে ইরান এক চিঠিতে IAEA’কে ব্যাখ্যা দেয় যে, ইরানে সম্ভাব্য সামরিক হামলার হুমকির কারণে তারা স্থাপনাটিকে ভূগর্ভে নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইরানের অন্যান্য লক্ষ্যবস্তুর সঙ্গে সম্ভাব্য হামলার আওতায় থাকা নাতাঞ্জ পারমাণবিক কেন্দ্রের বিকল্প হিসেবেই তৈরি করা হয়েছে ফোর্দো। এখানেও অন্তত ৩০০০ সেন্ট্রিফিউজ রাখার ব্যবস্থা আছে, যা ইউরেনিয়ামকে অস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রায় উন্নত করতে পারে। সেন্ট্রিফিউজ এমন যন্ত্র যা ইউরেনিয়ামকে সমৃদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করা হয়।
এছাড়াও ইরানের আরও কিছু পারমাণবিক কেন্দ্র –
• নাতাঞ্জ ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র:
– নাতাঞ্জ ফুয়েল এনরিচমেন্ট প্লান্ট (এফইপি) হচ্ছে ইরানের সবচেয়ে বড় ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কেন্দ্র, যা ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে চালু হয়। এখানে ‘সেন্ট্রিফিউজ’ নামের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। এই প্লান্টের দুটি ইউনিট রয়েছে। এই দুটি ইউনিটেরই অবস্থান মাটির নিচে বিশেষ সুরক্ষা দিয়ে তৈরি, যাতে বিমান হামলার আঘাত থেকে বাঁচানো যায়।
• খােনদাব হেভি ওয়াটার রিঅ্যাক্টর:
– খোনদাব রিঅ্যাক্টর আগে আরাক হেভি ওয়াটার রিঅ্যাক্টর নামে পরিচিত ছিল। এই পারমাণবিক কেন্দ্রটি ইরানের মারকাজি প্রদেশের খোনদাব শহরের কাছে অবস্থিত। এই রিঅ্যাক্টরটি শুরুতে তৈরি করা হয়েছিল গবেষণার জন্য। তবে, এই রিঅ্যাক্টরটি প্লুটোনিয়াম উৎপাদন করতে পারে, যা পারমাণবিক বোমা বানানোর উপাদান। এই রিঅ্যাক্টরের ভবিষ্যৎ নিয়ে আন্তর্জাতিক মহল বেশ উদ্বিগ্ন।
• ইস্পাহান পারমাণবিক প্রযুক্তি কেন্দ্র:
– ইস্পাহান পারমাণবিক প্রযুক্তি কেন্দ্র ইউরেনিয়ামকে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করে ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুরাইড (ইউএফ৬) তৈরি করে। ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুরাইড হলো রিঅ্যাক্টরের জ্বালানি, যা পরে নাতাঞ্জ বা ফোর্দোতে পাঠানো হয় সমৃদ্ধ করতে। এ ছাড়া এখানেই তৈরি হয় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানি, যার মধ্যে বুশেহর বিদ্যুৎকেন্দ্রও পড়ে।
• বুশেহর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র:
– বুশেহর হলো, ইরানের একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র, যা বুশেহর শহরের দক্ষিণে পারস্য উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এর নির্মাণকাজ শুরু হয় ১৯৭৫ সালে জার্মানির সহায়তায়। এখানে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম রাশিয়া থেকে আনা হয়, আর ব্যবহৃত জ্বালানি আবার রাশিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়। যাতে তা প্রক্রিয়াজাত করে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির উপাদান বানানো না যায়।
উৎস: i) The Nuclear Threat Initiative. ii) The Business Standard. iii) BBC.
প্রশ্ন ১১১. আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম রাষ্ট্র কোনটি?
ক) ইরাক খ) চীন
গ) রাশিয়া ঘ) পাকিস্তান
সঠিক উত্তর: গ) রাশিয়া
Live MCQ Analytics: Right: 64%; Wrong: 10%; Unanswered: 24%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম রাষ্ট্র রাশিয়া।
তালেবান সরকারকে বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি:
– বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে তালেবান সরকারকে বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে রাশিয়া।
– ৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে রাশিয়া তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।
– এর মধ্য দিয়ে রাশিয়া তালেবান সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে।
– ২০২৪ সালের জুলাই মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তালেবানকে ‘সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের মিত্র’ বলে আখ্যা দেন।
– এপ্রিল মাসে রাশিয়ার সর্বোচ্চ আদালত তালেবানের ওপর থেকে ‘সন্ত্রাসী’ আখ্যা তুলে নেন।
⇒ আফগানিস্তানের সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে জন্ম হয়েছিল তালেবান বাহিনীর। ১৯৯৬ সালে তালেবান গোষ্ঠী কাবুলের দখল নেয়।
– ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর সন্ত্রাসী হামলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং ২০০১-এর শেষে তালেবানদের উৎখাত করে। এক বিধ্বংসী সামরিক অভিযানে ২০০১ সালে তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর গত ২০ বছর ধরে আফগানিস্তানের সামরিক নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও তার ন্যাটো মিত্ররা।
– ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারীতে যুক্তরাষ্ট্র এবং তালেবানের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। ২০২১ সালে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের পর তালেবানরা কাবুল পুনরায় দখল করে।
– ২০ বছর পর ২০২১ সালে তালেবানরা আবারও আফগানিস্তানে ক্ষমতায় আসে।
– ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সালের সোভিয়েত আগ্রাসন থেকে চার দশকের যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিনিয়োগের জন্য আগ্রহী দেশটির তালেবান সরকার।
উল্লেখ্য যে,
– ২০২১ সালের অগাস্টে তালেবানরা আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার পর, কোনো দেশই তাদের সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে এই সময়ের মধ্যে রাশিয়া ধীরে ধীরে তালেবানদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।
অন্যদিকে,
– স্বীকৃতি না দিলেও ইতোমধ্যে চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান ও পাকিস্তান কাবুলে তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছে, যা স্বীকৃতি দেওয়ার অন্যতম ধাপ।
উৎস: i) Britannica. ii) BBC.
প্রশ্ন ১১২. ‘The One Big Beautifull Bill Act’ এ USA হতে remittance প্রেরণ করতে কী পরিমাণ কর ধার্য করা হয়েছে?
ক) ৫% খ) ৩% গ) ১% ঘ) ২%
সঠিক উত্তর: গ) ১%
Live MCQ Analytics: Right: 4%; Wrong: 21%; Unanswered: 73%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ ‘The One Big Beautifull Bill Act’ এ USA হতে remittance প্রেরণ করতে ১% কর ধার্য করা হয়েছে।
One Big Beautiful Bill Act (বিগ বিউটিফুল বিল):
– ২০২৫ সালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পরে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টে পাশ হওয়া বিতর্কিত বিলটির নাম One Big Beautiful Bill Ac।
⇒ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত নতুন কর ও ব্যয় বিল (The One Big Beautifull Bill Act) পাস করেছে।
– প্রতিনিধি পরিষদে ২১৮-২১৪ ভোটের ব্যবধানে বিলটি পাস হয়েছে।
– এটি ২০২৫ সালের ৪ জুলাই স্বাক্ষরিত হয়।
⇒ বিগ বিউটিফুল বিলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অন্যান্য দেশে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছিল।
– তারপর তা কমিয়ে ৩.৫% রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।
– সর্বশেষ তা ১% করা হয়েছে।
উল্লেখ্য,
– স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা খাতে ব্যয় সংকোচ করার পাশাপাশি এই বিলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং অভিবাবসনপ্রত্যাশীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর ব্যাপারেও এই বিলে বিপুল অর্থ ধার্ষ করা হয়েছে। পাশাপাশি সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে এই বিলে।
– অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধের যে প্রকল্প ট্রাম্প গ্রহণ করেছেন, তাতে ব্যয় করা হবে ১৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মেক্সিকোয় সীমান্ত পাঁচিল তৈরিতেও এই অর্থ খরচ হবে বলে জানানো হয়েছে। সীমান্তে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলেও জানিয়েছেন ট্রাম্প। সামরিক খাতে ব্যয় করা হবে ১৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে মিসাইল এবং যুদ্ধ জাহাজ তৈরিতে। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতেও বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করা হবে বলে জানা গেছে।
– তবে পরিবেশবিদেরা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে। প্রচারে ট্রাম্প একটি কথা বারবার বলেছেন, ‘ড্রিল বেবি ড্রিল’। অর্থাৎ, নতুন করে খনিজ তেল উত্তোলন শুরু করতে হবে। এই বিলে সেই খাতে ব্যয় ধার্য করা হয়েছে। তোলা হবে প্রাকৃতিক গ্যাসও। এর আগে বিকল্প শক্তির জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছিল, তা বদলে দেওয়ার নীতি নিয়েছেন ট্রাম্প। ইলেকট্রিক গাড়িতে ছাড় বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।
উৎস: i) The White House (.gov). ii) BBC.
প্রশ্ন ১১৩. কিয়োটো প্রটোকলের বিষয়বস্তু কী?
ক) ওজোনস্তরের ক্ষয় হ্রাস খ) জৈব নিরাপত্তা
গ) জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা ঘ) গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস
সঠিক উত্তর: ঘ) গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস
Live MCQ Analytics: Right: 57%; Wrong: 26%; Unanswered: 16%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ কিয়োটো প্রটোকলের বিষয়বস্তু গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস।
কিয়োটো প্রটোকল:
– গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য প্রথম আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরি করে কিয়োটো প্রোটোকল।
– এই প্রোটোকলটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (UNFCCC) অধীনে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি।
– কিয়োটো প্রোটোকল শিল্পোন্নত দেশগুলোকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়।
⇒ স্বাক্ষরিত হয়: ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।
– কার্যকর হয়: ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।
– স্বাক্ষরের স্থান: কিয়োটো, জাপান।
– স্বাক্ষরিত দেশ: ৮৩টি।
– অনুমোদনকারী দেশ: ১৯২টি।
⇒ বিশ্বের উষ্ণতা রোধে কিয়েটো প্রটোকলকে কার্বন সনদ হিসেবে মনে করা হতো। এই প্রটোকলের প্রধান লক্ষ্য ছিল গ্রীনহাউস গ্যাস, বিশেষ করে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) নির্গমন কমানো। কারণ, কার্বন ডাই অক্সাইড প্রধান গ্রীনহাউস গ্যাস এবং এটি বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধির (গ্লোবাল ওয়ার্মিং) জন্য দায়ী প্রধান উপাদান।
– কিয়োটো প্রটোকল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের নির্গমন কমানোর জন্য ‘কার্বন ক্রেডিট’ ব্যবস্থাও চালু করেছিল, যার মাধ্যমে এক দেশ অন্য দেশের নির্গমন কমানোর প্রচেষ্টা কিনতে পারে বা বিক্রি করতে পারে। এর মাধ্যমে একটি বৈশ্বিক বাজার তৈরি হয়েছিল, যা ‘কার্বন সনদ’ বা ‘কার্বন ক্রেডিট’ নামে পরিচিত।
উল্লেখ্য,
– কিয়োটো চুক্তির ভিত্তিতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ২০১২ সালের মধ্যে ৫.২ শতাংশ কমানোর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
– চুক্তি বাস্তবায়নের শর্ত অনুযায়ী বিশ্বের মোট গ্রিনহাউস গ্যাসের ৫৫ শতাংশ উৎপাদনকারী দেশগুলোর স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল।
– প্রাথমিক পর্যায়ে নিজ নিজ দেশে উৎপন্ন গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।
– চুক্তিভুক্ত দেশগুলো যে ছয়টি গ্যাস নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ নেয় সেগুলো হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোফ্লোরোকার্বন, পারফ্লোরোকার্বন ও সালফার।
⇒ কিয়োটো প্রটোকলের অংশ হিসেবে অনেক উন্নত দেশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসকরণের জন্য নৈতিকভাবে দুটি পর্যায়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।
– প্রথম প্রতিশ্রুতির সময় ২০০৮-২০১২ এবং দ্বিতীয়টি ২০১৩-২০২০ সাল পর্যন্ত।
– প্রথম চুক্তির মেয়াদ ২০১২ সালে শেষ হলে দ্বিতীয় দফায় সেই চুক্তি সংশোধন করে ২০২০ সাল নাগাদ বর্ধিত করা হলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়নি।
অন্যদিকে,
– ওজোনস্তরের ক্ষয় সাধনকারী পদার্থের নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি মন্ট্রিল প্রটোকল।
– জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বিষয়ক ও জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক প্রটোকল হলো কার্টাগেনা প্রটোকল।
উৎস: UNFCCC ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১১৪. বিশ্ব পরিবেশ দিবস কোনটি?
ক) ৫ জুন খ) ২২ এপ্রিল
গ) ৬ জুলাই ঘ) ৫ জুলাই
সঠিক উত্তর: ক) ৫ জুন
Live MCQ Analytics: Right: 85%; Wrong: 1%; Unanswered: 13%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন।
বিশ্ব পরিবেশ দিবস:
– বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় ৫ জুন।
– জাতিসংঘ ৫ জুনকে পরিবেশ দিবস হিসেবে ঘোষনা করে।
– ২০২৫ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য – ‘প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়’।
⇒ ১৯৬৮ সালে জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদের কাছে একটি চিঠি পাঠায় সুইডেন সরকার। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে তাদের গভীর উদ্বেগের কথা। সে বছরই জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি সাধারণ অধিবেশনের আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
– সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন বিশ্বের প্রথম পরিবেশ সম্মেলন United Nations Conference on the Environment অনুষ্ঠিত হয়।
– ১৯৭২ সালের ৫ জুন এই সম্মেলন থেকে United Nations Environment Program গঠিত হয়।
– ১৯৭৩ সালের ৫ জুন প্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়।
উল্লেখ্য,
UNEP:
– জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি United Nations Environment Programme (UNEP).
– প্রতিষ্ঠিত হয়: ১৯৭২ সালের ৫ জুন।
– সদরদপ্তর: নাইরোবি, কেনিয়া।
– বর্তমান সদস্য: ১৯৩টি।
– UNEP এর প্রধানের পদবী: নির্বাহী পরিচালক।
– বর্তমান নির্বাহী পরিচালক: ইনগার অ্যান্ডারসেন।
– জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন সুইডেনের স্টকহোম শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম পরিবেশ সম্মেলন United Nations Conference on the Environment এর প্রেক্ষিতে UNEP প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎস: UNEP ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১১৫. Climate Vulnerable Form (CVF) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক) ২০০৮ খ) ২০০৯ গ) ২০১১ ঘ) ২০১০
সঠিক উত্তর: খ) ২০০৯
Live MCQ Analytics: Right: 21%; Wrong: 26%; Unanswered: 51%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:Climate Vulnerable Form (CVF) ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
Climate Vulnerable Forum (CVF):
– Climate Vulnerable Forum হলো জলবায়ু জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।
– প্রতিষ্ঠিত হয়: ২০০৯ সালে।
– প্রতিষ্ঠার স্থান: মালে, মালদ্বীপ।
– বর্তমান সদস্য: ৭৪টি।
– বর্তমান সভাপতি: বার্বাডোস।
⇒ ২০০৯ সালের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত COP-15 সম্মেলনের আগে বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ ১১টি দেশ মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে একত্রিত হয়ে CVF প্রতিষ্ঠা করে।
– উদ্যোক্তা: মালদ্বীপের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ নাশিদ।
⇒ Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর উদ্দেশ্য:
– আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সদস্য দেশগুলির অভ্যন্তরীণভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রচার করা
– গবেষণা ও তথ্য প্রদান → জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া ও নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা।
– সচেতনতা ও সমর্থন বৃদ্ধি → বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য বৈশ্বিক জনমত ও সহায়তা আদায়।
উৎস: Climate Vulnerable Forum ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১১৬. ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়?
ক) ১৯৬০ খ) ১৯৬৬ গ) ১৯৭৪ ঘ) ১৯৭৫
সঠিক উত্তর: ক) ১৯৬০
Live MCQ Analytics: Right: 37%; Wrong: 22%; Unanswered: 40%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি ১৯৬০ সালে সম্পাদিত হয়।
সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি (Indus Waters Treaty):
– ভারতের উজান থেকে পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকায় প্রবাহিত নদীগুলোর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি হচ্ছে সিন্ধু পানি চুক্তি।
– চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়: ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সাল।
– চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান: করাচি, পাকিস্তান।
– মধ্যস্থতাকারী: বিশ্বব্যাংক।
– চুক্তি স্বাক্ষরকারী: ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান।
⇒ সিন্ধু পানি চুক্তি অনুসরণ করেই এসব নদীর পানি ব্যবহার করা হয়।
– এই চুক্তি সিন্ধু নদের অববাহিকার ছয়টি নদী দুই দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে।
– চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে তিনটি পূর্বাঞ্চলীয় নদীর নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল। এগুলো হলো ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু।
– অন্যদিকে পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলীয় তিনটি নদ–নদী অর্থাৎ সিন্ধু, ঝিলম এবং চেনাবের নিয়ন্ত্রণ। বলা হয় পশ্চিম অংশের এ তিনটি নদ–নদীর মাধ্যমে পাকিস্তানে মোট পানির প্রায় ৮০ ভাগ সরবরাহ করে।
– চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান পায় ৭০ ভাগ পানি আর ভারত পায় ৩০ ভাগ পানি।
– চুক্তিটি কোনো দেশ একতরফাভাবে স্থগিত বা বাতিল করার বিধান নেই। বরং এতে সুস্পষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।
উৎস: i) Britannica. ii) UNTC ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১১৭. UNOPS এর পূর্ণরূপ কী?
ক) United Nations Organization for Peace and Security
খ) United Nations Office for Public Service
গ) United Nations Office for Project Service
ঘ) United Nations Operations and planning system
সঠিক উত্তর: গ) United Nations Office for Project Service
Live MCQ Analytics: Right: 11%; Wrong: 48%; Unanswered: 39%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ UNOPS এর পূর্ণরূপ – United Nations Office for Project Services.
UNOPS:
– UNOPS-এর পূর্ণরুপ: United Nations Office for Project Services.
– এটি জাতিসংঘের প্রকল্প পরিষেবা অফিস।
– প্রতিস্থিত হয়: ১৯৭৩ সালে (প্রথমে UNDP-এর অংশ, পরে ১৯৯৫ সালে স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়)।
– সদর দপ্তর: কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক।
– বর্তমান মহাপরিচালক: জর্জ মোরেরা দা সিলভা (Jorge Moreira da Silva)।
– এটি বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে প্রকল্প সমর্থন করে।
⇒ কাজ:
– উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
– শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে সহায়তা।
– মানবিক সাহায্য ও পুনর্গঠন কার্যক্রম।
– টেকসই অবকাঠামো ও সেবা প্রদান।
উৎস: UNOPS ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১১৮. বর্তমানে অর্থনীতির ব্যাপ্তি অনুসারে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট কোনটি?
ক) EU খ) WTO গ) RCEP ঘ) AU
সঠিক উত্তর: গ) RCEP
Live MCQ Analytics: Right: 30%; Wrong: 52%; Unanswered: 17%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ বর্তমানে অর্থনীতির ব্যাপ্তি অনুসারে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট RCEP।
RCEP:
– RCEP-এর পূর্ণরূপ: Regional Comprehensive Economic Partnership.
– RCEP হলো Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) এর সদস্য রাষ্ট্র। এটি বিশ্বের বৃহত্তম আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি।
– স্বাক্ষরিত হয়: ১৫ নভেম্বর, ২০২০।
– কার্যকর হয়: ১ জানুয়ারি, ২০২২।
– স্বাক্ষরকারী দেশ: ১৫টি (চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর, কম্বোডিয়া, লাওস ও মিয়ানমার)।
⇒ অর্থনীতির ব্যাপ্তি:
– বৈশ্বিক GDP-এর প্রায় ৩০%,
– বৈশ্বিক জনসংখ্যারও প্রায় ৩০% (প্রায় ২.২ বিলিয়ন),
– বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রায় ২৮.৮%।
অন্যদিকে –
→ EU (European Union):
– বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
– এর অর্থনীতির ব্যাপ্তি বৈশ্বিক জনসংখ্যারও প্রায় ৫.৬% (প্রায় ৪৪৮ মিলিয়ন), বৈশ্বিক GDP-এর প্রায় ১৪.৭%।
– তাই বর্তমানে অর্থনীতির ব্যাপ্তি অনুসারে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট EU নয়।
এছাড়াও,
– WTO (World Trade Organization): এটি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা, অর্থনৈতিক জোট নয়।
– AU (African Union): আফ্রিকান ইউনিয়ন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগঠন, তবে অর্থনৈতিক শক্তি তুলনামূলকভাবে দুর্বল।
উৎস: i) Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade ওয়েবসাইট।
ii) European Commission ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১১৯. জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা বা জাতিসংঘ পর্যটন (পূর্বতন UNWTO) এর সদর দপ্তর কোথায়?
ক) তুরিন, ইতালি খ) মাদ্রিদ, স্পেন
গ) প্যারিস, ফ্রান্স ঘ) ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি
সঠিক উত্তর: খ) মাদ্রিদ, স্পেন
Live MCQ Analytics: Right: 49%; Wrong: 17%; Unanswered: 33%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা বা জাতিসংঘ পর্যটন (পূর্বতন UNWTO) এর সদর দপ্তর মাদ্রিদ, স্পেন-এ অবস্থিত।
UN Tourism:
– জাতিসংঘের পর্যটন সংস্থা UNWTO এর পূর্ণরূপ: United Nations World Tourism Organization.
– এটি জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা যা বৈশ্বিক পর্যটন খাতের উন্নয়ন, সহযোগিতা এবং টেকসই ভ্রমণকে উৎসাহিত করে।
– প্রতিষ্ঠিত হয়: ১ নভেম্বর, ১৯৭৫।
– ২০০৩ সালে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে।
– সদর দপ্তর: মাদ্রিদ, স্পেন।
– বর্তমান সদস্য: ১৬০টি।
– বর্তমান মহাসচিব: যুরাব পলোকাসভিলি (Zurab Pololikashvili)।
⇒ উদ্দেশ্য:
– বৈশ্বিক পর্যটন খাতের উন্নয়ন, টেকসই পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব ভ্রমণ নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য হ্রাসে পর্যটনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা, পর্যটন খাতে আন্তর্জাতিক মান ও নীতি নির্ধারণ করা ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পর্যটনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
⇒ সংস্থাটি ১৯৩৪ সালে International Union of Official Tourist Propaganda Organizations (IUOTPO) নামে যাত্রা শুরু করে।
– ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ অফিসিয়াল ট্যুরিস্ট প্রোপাগান্ডা অর্গানাইজেশন (IUOTPO) প্রতিস্থাপনের জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়।
– পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মেক্সিকো সিটিতে IUOTO বিশেষ সাধারণ পরিষদের সভায় এর নাম পরিবর্তন করে The World Tourism Organization (UNWTO) রাখা হয়।
– ১৯৭৫ সালে স্প্যানিশ সরকারের আমন্ত্রণে মে মাসে মাদ্রিদে প্রথম WTO সাধারণ পরিষদের বৈঠক হয়। রবার্ট লোনাতিকে প্রথম WTO মহাসচিব হিসেবে ভোট দেওয়া হয় এবং অ্যাসেম্বলি মাদ্রিদে তার সদর দপ্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।
– ২০২৩ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে “UN Tourism” ব্যবহার করা শুরু হয়।
উল্লেখ্য,
– বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয় ২৭ সেপ্টেম্বর।
উৎস: UNWTO ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১২০. কোন দেশটি OPEC এর সদস্য নয়?
ক) ইন্দোনেশিয়া খ) নাইজেরিয়া
গ) বাংলাদেশ ঘ) গ্যাবন
সঠিক উত্তর: গ) বাংলাদেশ
Live MCQ Analytics: Right: 73%; Wrong: 7%; Unanswered: 18%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ OPEC-এর সদস্য নয়- বাংলাদেশ। কখনোই বাংলাদেশ OPEC-এর সদস্য ছিল না।
→ OPEC-এর সদস্য – আলজেরিয়া, কঙ্গো, নিরক্ষীয় গিনি, গ্যাবন, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া, নাইজেরিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভেনিজুয়েলা।
→ উল্লেখ্য, ইন্দোনেশিয়া আগে OPEC-এর সদস্য ছিল (১৯৬২), ২০০৯ সালে স্থগিত, ২০১৬ সালে আবার যোগ দেয়, পরে আবার স্থগিত করে।
OPEC:
– OPEC-এর পূর্ণরূপ: Organization of the Petroleum Exporting Countries.
– এটি পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশসমূহের একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন।
– প্রধান উদ্দেশ্য: সদস্য দেশসমূহের পেট্রোলিয়ামের নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয় এবং বৈশ্বিক তেলের দাম নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রন করা।
⇒ OPEC গঠনের প্রস্তাবক দেশ ভেনেজুয়েলা।
– প্রতিষ্ঠিত হয়: সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সালে (বাগদাদ সম্মেলনের মাধ্যমে)।
– প্রতিষ্ঠার স্থান: বাগদাদ, ইরাক।
– প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য: ৫টি (ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব ও ভেনিজুয়েলা)।
– বর্তমান সদস্য: ১২টি।
– সদরদপ্তর: ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া (১৯৬৫ সালের পূর্বে এর সদর দপ্তর ছিল সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়)।
উল্লেখ্য,
– ইন্দোনেশিয়া ২০০৮ সালে ওপেক থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়।
– এ ছাড়া ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি কাতার এবং ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি ইকুয়েডর সদস্যপদ ছেড়ে দেয়।
– ১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অ্যাঙ্গোলা OPEC থেকে বেরিয়ে এসেছে।
এছাড়াও,
• OPEC Plus (OPEC+):
– তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর জোট ও তাদের সহযোগীরা ওপেক প্লাস হিসেবে পরিচিত।
– গঠিত হয়: ২০১৬ সালে (আলজেরিয়া)।
– OPEC+ দেশ: ৮টি (সৌদি আরব, রাশিয়া, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাজাখস্তান, আলজেরিয়া এবং ওমান)।
– এরা বিশ্বের তেল উৎপাদনের প্রায় ৫৯% নিয়ন্ত্রণ করে।
উৎস: i) OPEC ওয়েবসাইট। ii) History.com
ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
প্রশ্ন ১২১. বাংলাদেশের দীর্ঘতম স্থলসীমান্ত ভারতের কোন রাজ্যের সাথে?
ক) মেঘালয় খ) আসাম
গ) পশ্চিমবঙ্গ ঘ) ত্রিপুরা
সঠিক উত্তর: গ) পশ্চিমবঙ্গ
Live MCQ Analytics: Right: 73%; Wrong: 7%; Unanswered: 19%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের দীর্ঘতম স্থলসীমান্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাথে।
• বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত:
– বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত ভারতের পাঁচটি রাজ্যের সাথে সংযুক্ত। যথা:
– পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম।
– বাংলাদেশের সাথে মেঘালয়ের স্থলসীমান্ত রয়েছে, যা প্রায় ৪৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ।
– আসামের সাথে বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত প্রায় ২৬৪ কিলোমিটার।
– ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত প্রায় ৮৭৪ কিলোমিটার।
– বাংলাদেশের সাথে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্থলসীমান্ত সবচেয়ে দীর্ঘ, যা প্রায় ২,২৬২ কিলোমিটার।
– সর্বমোট স্থল সীমানা ৪১৫৬ কিলোমিটার।
• পশ্চিমবঙ্গ:
– বাংলাদেশের সাথে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্থলসীমান্ত সবচেয়ে দীর্ঘ, যা প্রায় ২,২৬২ কিলোমিটার।
– এই সীমান্ত বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশিরভাগ জেলার সাথে সংযুক্ত, যেমন রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, সাতক্ষীরা, এবং দিনাজপুরের এলাকা।
– পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের এই দীর্ঘ সীমান্তের কারণে এটি দীর্ঘতম হিসেবে বিবেচিত।
∴ সুতারাং সঠিক উত্তর: পশ্চিমবঙ্গ,পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের এই দীর্ঘ সীমান্তের কারণে এটি দীর্ঘতম হিসেবে বিবেচিত।
উৎস: বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড।
প্রশ্ন ১২২. প্রতি ৩০° দ্রাঘিমার স্থানান্তরে সময়ের ব্যবধান কত মিনিট হয়?
ক) ১৫ মিনিট খ) ৩০ মিনিট
গ) ৬০ মিনিট ঘ) ১২০ মিনিট
সঠিক উত্তর: ঘ) ১২০ মিনিট
Live MCQ Analytics: Right: 76%; Wrong: 4%; Unanswered: 18%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ প্রতি ৩০° দ্রাঘিমার স্থানান্তরে সময়ের ব্যবধান হয় ১২০ মিনিট।
গ্রিনিচ মান সময়:
– গ্রিনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশ সময় ৬ ঘণ্টা আগে।
– পৃথিবীতে প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্যে সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট করে।
– সেজন্যে বাংলাদেশ মূল মধ্যরেখা বা গ্রিনিচ মানমন্দির থেকে ৯০ ডিগ্রি পূর্বদিকে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের সাথে গ্রিনিচের সময়ের পার্থক্য ৯০ x ৪ = ৩৬০ মিনিট বা ৬ ঘন্টা।
– গ্রিনিচের পূর্ব দিকে অবস্থিত স্থানগুলোর সময় গ্রিনিচের থেকে এগিয়ে থাকে।
– গ্রিনিচের পশ্চিমের স্থানগুলোর সময় গ্রিনিচ থেকে পিছিয়ে থাকে।
স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য:
– প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ৪ মিনিট।
– পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে, এজন্যই পূর্ব দিকের স্থানগুলোতে আগে দিন হচ্ছে এবং পশ্চিম দিকের স্থানগুলোতে পরে দিন হচ্ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশ পূর্ব দিকে অবস্থিত, সেসব দেশে আগে সকাল হবে এবং পশ্চিম দিকের দেশগুলোতে পরে সকাল হবে।
– প্রতি ডিগ্রি দূরত্বের জন্য সময়ের ব্যবধান হচ্ছে ৪ মিনিট। এই প্রতিটি ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে ভাগ করা হয় এবং প্রতি ১ মিনিট দূরত্বের জন্য ৪ সেকেন্ড সময়ের পার্থক্য হয়।
– এখানে, একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে দূরত্বের ব্যবধানের মিনিটকে অনেকে সময়ের মিনিট হিসেবে ধরে ভুল করে। আসলে দূরত্বের মিনিটের ক্ষেত্রে ১ ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে ভাগ করা হয়। এই দূরত্বের ৬০ মিনিটের প্রতি মিনিটের জন্য সময়ের ৪ সেকেন্ড লাগে। এভাবে দূরত্বের ব্যবধানের ৬০ মিনিটের জন্য লাগে ৬০ × ৪ = ২৪০ সেকেন্ড অর্থাৎ ৪ মিনিট সময়।
এখন, প্রতি ১° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় = ৪ মিনিট
সুতরাং, প্রতি ৩০° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় = (৩০ × ৪) মিনিট = ১২০ মিনিট।
উৎস: ভূগোল ও পরিবেশ, নবম-দশম শ্রেণি এবং গ্রিনিচ মানমন্দির ওয়েবসাইট।।
প্রশ্ন ১২৩. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক করিডরের মাঝখানে?
ক) মালাক্কা ও হরমুজ প্রণালী খ) হরমুজ ও পক প্রণালী
গ) সুয়েজ খাল ও জিব্রাল্টার প্রণালী
ঘ) জিব্রাল্টার ও বসফরাস প্রণালী
সঠিক উত্তর: ক) মালাক্কা ও হরমুজ প্রণালী
Live MCQ Analytics: Right: 36%; Wrong: 31%; Unanswered: 31%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান মালাক্কা ও হরমুজ প্রণালী সামুদ্রিক করিডরের মাঝখানে।
• মালাক্কা প্রণালী:
– এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অবস্থিত,- যা ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযুক্ত করে।
– এটি বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম সামুদ্রিক পথগুলোর একটি, যার মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য পণ্য পরিবহন হয়।
• হরমুজ প্রণালী:
– পারস্য উপসাগরকে পূর্বের ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সাথে যুক্ত করে।
– যা মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল রপ্তানির প্রধান পথ।
– বাংলাদেশের অবস্থান বঙ্গোপসাগরে এই দুটি প্রণালীর মধ্যে কৌশলগত সংযোগ তৈরি করে।
• পক প্রণালী:
-পক প্রণালী ভারতীয় রাজ্য তামিলনাড়ু ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী একটি সামুদ্রিক প্রণালী।
– এটি বঙ্গোপসাগর ও মান্নার উপসাগরকে একসঙ্গে যুক্ত করেছে।
• সুয়েজ খাল ও জিব্রাল্টার প্রণালী:
– সুয়েজ খাল ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করে,
– জিব্রাল্টার প্রণালী ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরকে সংযুক্ত করে।
– এই দুটি পথই বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে এবং ভৌগোলিকভাবে এর অবস্থানের সাথে কৌশলগতভাবে সম্পর্কিত নয়।
• হরমুজ ও পক প্রণালী বাংলাদেশের সামুদ্রীক করিডর মধ্য অবস্থান নয়। এটি একদিকে অবস্থান করে।
– তাই এটি সঠিক উত্তর যুক্তি যসঙ্গত নয়।
∴ সঠিক উত্তর: মালাক্কা ও হরমুজ প্রণালী।
উৎস: indiannavy.nic.in.
প্রশ্ন ১২৪. হিমালয় পর্বতমালার উদ্ভব কোন দুটি টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষে হয়েছে?
ক) ইউরেশিয়ান ও আফ্রিকান
খ) ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান ও ইউরেশিয়ান
গ) আমেরিকান ও ইউরেশিয়ান
ঘ) প্যাসিফিক ও ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান
সঠিক উত্তর: খ) ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান ও ইউরেশিয়ান
Live MCQ Analytics: Right: 35%; Wrong: 24%; Unanswered: 39%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ হিমালয় পর্বতমালার উদ্ভব ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান ও ইউরেশিয়ান টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষে হয়েছে।
• ইউরেশিয়ান প্লেট বিশ্বের সবচেয়ে বড় কনটিনেন্টাল প্লেট, যা ইউরোপ এবং এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত।
• ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান প্লেট (বা ইন্ডিয়ান প্লেট) ভারতীয় উপমহাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া অন্তর্ভুক্ত করে।
– এটি উত্তর দিকে চলমান হয়ে ইউরেশিয়ান প্লেটের সাথে সংঘর্ষ করে, যা হিমালয় গঠনের প্রধান কারণ।
• আমেরিকান ও ইউরেশিয়ান‘:
– আমেরিকান’ বলতে সম্ভবত নর্থ আমেরিকান (North American) বা সাউথ আমেরিকান (South American) প্লেট বোঝানো হয়েছে।
– নর্থ আমেরিকান প্লেট উত্তর আমেরিকা এবং আটলান্টিকের অংশ কভার করে, যখন সাউথ আমেরিকান প্লেট দক্ষিণ আমেরিকা।
– হিমালয়ের সাথে এদের কোনো যোগ নেই।
• প্যাসিফিক ও ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান:
– প্যাসিফিক প্লেট প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে অবস্থিত ।
– ‘রিং অফ ফায়ার’-এর জন্য দায়ী, যেখানে সাবডাকশনের ফলে আন্দিজ (Andes) বা জাপানের পর্বত গঠিত হয়।
– ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান প্লেটের সাথে এর সীমান্তে জাভা ট্রেঞ্চ (Java Trench) আছে, যা ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির কারণ, কিন্তু কোনো পর্বতমালা গঠন হয়নি।
– আফ্রিকান প্লেট ইউরেশিয়ানের সাথে সংঘর্ষ করে মরক্কো থেকে ইউরোপীয় পর্বত গঠন করে, কিন্তু হিমালয়ের জন্য নয়।
∴ সুতরাং সঠিক উত্তর: ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান ও ইউরেশিয়ান।
সোর্স: ওয়ার্ল্ড এটলাস ও ব্রিটানিকা।
প্রশ্ন ১২৫. বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে ওজোন গ্যাসের স্তর অবস্থান করে?
ক) ট্রপোমণ্ডল খ) থার্মোমণ্ডল
গ) স্ট্র্যাটোমণ্ডল ঘ) মেসোমণ্ডল
সঠিক উত্তর: গ) স্ট্র্যাটোমণ্ডল
Live MCQ Analytics: Right: 72%; Wrong: 10%; Unanswered: 16%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
◉ বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের স্তর অবস্থান করে।
• স্ট্রাটোমণ্ডল:
– ট্রপোমণ্ডলের ঠিক উপরেই শুরু হয়েছে স্ট্রাটোমণ্ডল।
– বায়ুমণ্ডলের এই স্তর ট্রপোমণ্ডল থেকে শুরু করে প্রায় ৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত।
– বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে ওজোন নামের একটি গ্যাসের স্তর রয়েছে, এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে।
– বায়ুমণ্ডলের এই স্তর এবং এর উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য গ্যাস খুব কম পরিমাণে আছে।
• ট্রপোমণ্ডল:
– ভূপৃষ্ঠ থেকে বারো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রপোমণ্ডল।
– বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে বায়ুর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প থাকে।
– বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সব ঘটনা ঘটে।
যেমন- এই স্তরে মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু প্রবাহ, ঝড়, কুয়াশা এসব হয়; তাই ট্রপোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।
• মেসোমণ্ডল:
– স্ট্রাটোমণ্ডল শেষ হয়ে বায়ুমণ্ডলের এই স্তর শুরু হয়।
– বায়ুমণ্ডলের এই স্তর প্রায় ৮০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত।
– বায়ুমণ্ডলের এই স্তরের উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকে।
• তাপমণ্ডল:
– বায়ুমণ্ডলের এই স্তর প্রায় বায়ুশুন্য।
– বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে বায়ুর তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে, তাই এর নাম তাপমণ্ডল।
– বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।
উৎস: বিজ্ঞান, সপ্তম শ্রেণি।
প্রশ্ন ১২৬. ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে পুরাতন শিলা গঠন পাওয়া যায়?
ক) সিলেট খ) দিনাজপুর
গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম ঘ) মধ্যভাগের উচ্চভূমি
সঠিক উত্তর: খ) দিনাজপুর
Live MCQ Analytics: Right: 22%; Wrong: 48%; Unanswered: 29%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী বাংলাদেশের দিনাজপুর অঞ্চলে সবচেয়ে পুরাতন শিলা গঠন পাওয়া যায়।
ভূ-গাঠনিক রূপরেখা:
– বাংলাদেশ দুটি প্রধান ভূ-গাঠনিক ইউনিটে বিভক্ত:
ক) উত্তর পশ্চিমের সুস্থিত প্রাক-ক্যামব্রীয় প্ল্যাটফর্ম ও
খ) দক্ষিণ-পূর্বের মহীখাতীয় অববাহিকা।
– হিঞ্জ অঞ্চল (Hinge zone) নামের একটি সংকীর্ণ উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি তৃতীয় ইউনিট দেশের প্রায় মাঝ বরাবর উপরোক্ত দুটি ইউনিটকে বিভক্ত করে রেখেছে।
⇒ সুস্থিত প্রাক-ক্যামব্রীয় প্ল্যাটফর্ম রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত।
– প্রাক-ক্যামব্রীয় আগ্নেয় ও রূপান্তরজ ভিত্তিশিলার উপর সীমিত থেকে মাঝারি পুরুত্ববিশিষ্ট পাললিক শিলার আস্তর এর বৈশিষ্ট্য।
– আপেক্ষিক অর্থে এই ইউনিট ভূতাত্ত্বিকভাবে সুস্থিত এবং ভঙ্গিল বিচলনের (Fold movement) কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। কিছু চ্যুতিবেষ্টিত গ্রস্ত-অববাহিকা প্রাক-ক্যামব্রীয় ভিত্তিশিলার আওতাভুক্ত অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।
– এই সব অববাহিকা পার্মিয় যুগের (আজ থেকে ২৮৬-২৪৫ মিলিয়ন বছর আগে) কয়লাবাহী শিলার ইউনিট ধারণ করে।
– বাংলাদেশে প্রাপ্ত এটিই সর্বাধিক প্রাচীন পাললিক শিলা।
– বাংলাদেশে প্রাক-ক্যামব্রীয় প্ল্যাটফর্ম দুভাগে বিভক্ত: খুবই অগভীর প্রাক-ক্যামব্রীয় ভিত্তিশিলা (১৩০ থেকে ১০০০ মিটার) বিশিষ্ট উত্তরাঞ্চলীয় রংপুর অবতল (Rangpur saddle) এবং মাঝারি গভীরতা সম্পন্ন (১-৬ কিমি) দক্ষিণাঞ্চলীয় বগুড়া সোপান। বগুড়া সোপানে পাললিক স্তরসমূহ হিঞ্জ অঞ্চল পর্যন্ত খুব আলতোভাবে দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর নতিশীল এবং এরপর হঠাৎ করে এই ঢাল ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পাললিক ইউনিটসমূহ অতল গভীরে নেমে দক্ষিণ-পূর্বে গভীর মহীখাতীয় অববাহিকার মধ্যে এসে পড়েছে।
⇒ দক্ষিণ-পূর্বের মহীখাতীয় অববাহিকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাপক পুরুত্বের (অববাহিকার কেন্দ্রে সর্বাধিক প্রায় ২০ কিমি) ক্লাসটিক পাললিক শিলা (clastic sedimentary rock), যার অধিকাংশ বেলেপাথর ও টারশিয়ারী যুগের কর্দম শিলা।
– বৃহত্তর ঢাকা-ফরিদপুর-নোয়াখালী-সিলেট-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগর এর অন্তর্গত।
উৎস: বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ১২৭. কনরাড বিযুক্তি ভূ-অভ্যন্তরের কোন স্তরসমূহের মাঝে অবস্থান করে?
ক) সিয়াল ও সিমা খ) অশ্বমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল
গ) গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল ঘ) সিমা ও অশ্বমণ্ডল
সঠিক উত্তর: ক) সিয়াল ও সিমা
Live MCQ Analytics: Right: 4%; Wrong: 6%; Unanswered: 88%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ কনরাড বিযুক্তি ভূ-অভ্যন্তরের সিয়াল ও সিমা স্তরসমূহের মাঝে অবস্থান করে।
কনরাড বিযুক্তি:
– Sial ও Sima বিভাজনকারী স্তরকে কনরাড বিযুক্তি রেখা বলে।
– অর্থাৎ ভূ-ত্বকের লঘু ও গুরু শিলান্তরদ্বয় সীমারেখায় মিলিত হয়েছে তাকে কনরাড বিযুক্তি (Conrad Discontinuity) বলে।
⇒ সমুদ্র তলদেশের ভূত্বক প্রধানত ব্যাসল্ট জাতীয় এবং মহাদেশীয় ভূত্বক ফেলসিক স্তরবিহীন, ব্যাসল্ট-এর প্রধান খনিজ উপাদানের নাম সিলিকন (Si) এবং ম্যাগনেসিয়াম (Mg) যা সাধারণভাবে সিমা (Sima) নামে পরিচিত। ধারণা করা হয় যে, এ ব্যাসল্ট স্তরই সারা পৃথিবী জুড়ে বহিরাবরণ হিসেবে মহাদেশের মেফিক স্তরের নিচে ও গভীর সমুদ্রের তলদেশে বিদ্যমান। ভূ-ত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° সে. তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
⇒ ওপরের লঘুশিলা ভূ-ত্বকের বাইরের স্তর। এর ওপরেই আমরা গাছপালা ও তৃণাদি জন্মাতে দেখি। এ স্তরে গ্রাণাইড শিলার পরিমাণ বেশি তাই এক গ্রানাইট শিলা স্তর বলা হয়। গ্রানাইটে সিলিকা (Silica) ও অ্যালুমিনিয়ামের (Aluminium) পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তাই একে সিয়াল (Sial) স্তর বলে। মহাদেশগুলো প্রধানত এ জাতীয় শিলায় গঠিত।
→ সুতরাং ভূ-ত্বকের গঠন মোটামুটি নিম্নরূপ:
১. সিয়াল (গ্রানাইট) →এটি ভূ-ত্বকের ওপরের কনরাড বিযুক্তি।
২. সিমা (ব্যাসল্ট) → এটি ভূ-ত্বকের মধ্যবর্তী স্তর।
৩. অলিভিন → এটি ভূ-ত্বকের নিচের অংশ।
এছাড়াও,
– পৃথিবীর অভ্যন্তর তিনটি স্তরে বিভক্ত। স্তর তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ওপরের স্তর যেটি গুরুমন্ডলের ওপরে অবস্থিত সেটিকেই অশ্বমন্ডল বলে। এটাই পৃথিবীর কঠিন বহিরাবরণ। এটি নানা প্রকার শিলা ও খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত। এর গভীরতা ৩০ কি. মি. হতে প্রায় প্রায় ৬৪ কি.মি.। অশ্মমন্ডল যে সকল উপাদানে গঠিত তারমধ্যে সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।
– কেন্দ্র মন্ডলের বহিঃভাগ থেকে অশ্বমন্ডলের (ভূ-ত্বকের) নিম্ন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে গুরুমন্ডল বলে। এটি পৃথিবীর আয়তনের শতকরা ৮২ ভাগ এবং ওজনের শতকরা ৬৮ ভাগ দখল করে আছে।
– পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬,৪৩৪ কি.মি.। পৃথিবীর কেন্দ্রের চারিদিকে প্রায় ৩,৪৮৬ কি.মি. ব্যাসার্ধের এক গোলক অবস্থিত। এই গোলকটির নাম দেয়া হয়েছে কেন্দ্রমন্ডল। অন্তঃকেন্দ্র ও বহিঃকেন্দ্রকে একত্রে কেন্দ্রন্ডল বলে। এই স্তরের ঘনত্ব প্রায় ১০.৭৮ গ্রাম/সে.মি., যা গুরুমন্ডলের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন। কেন্দ্রমন্ডল লৌহ, নিকেল, পারদ, সীসা প্রভৃতি কঠিন ও ভারী পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই স্তরে নিকেল (Ni) ও লৌহের (Fe) পরিমাণ বেশি থাকায় একে নাইফ (Nife) বলা হয়।
উৎস: ভূমিবিদ্যা, এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ১২৮. বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি?
ক) চুনাপাথর খ) কাঁচবালি
গ) কয়লা ঘ) খনিজ লবণ
সঠিক উত্তর: গ) কয়লা
Live MCQ Analytics: Right: 70%; Wrong: 8%; Unanswered: 20%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
◉ বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা।
• কয়লা:
– ১৯৫৯ সালে ভূ-পৃষ্ঠের অত্যধিক গভীরতায় সর্বপ্রথম কয়লা আবিষ্কৃত হয়।
– বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জি.এস.বি)-এর অব্যাহত প্রচেষ্টায় ৪টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়।
– পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার যৌথ কোম্পানি বি.এইচ.পি-মিনারেলস আরও একটি কয়লাখনি আবিষ্কার করলে দেশে কয়লাখনির মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫টিতে।
– আবিষ্কৃত সকল কয়লাখনিই দেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত।
– উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেকয়লা প্রধান খনিজ সম্পদ।
– যথা: জামালগঞ্জ, বড়পুকুরিয়া,খালাশপীর,দীঘিপাড়া,ফুলবাড়ী তে অবস্থিত কয়লার খনিগুলো।
• চুনাপাথর:
– ১৯৬০-এর দশকের প্রথমভাগে দেশের উত্তর-পূর্বভাগে অবস্থিত টাকেরঘাট এলাকায় ইয়োসিনযুগীয় চুনাপাথরের একটি ক্ষুদ্র মজুত থেকে চুনাপাথর আহরণ করে তা একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে সরবরাহ করা হয়।
– নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলায় চুনাপথর খনি রয়েছে।
• কাচাঁবালি:
– বাংলাদেশে কাচবালির উল্লেখযোগ্য মজুত রয়েছে।
– বাংলাদেশের উপকূলীয় বলয় ও উপকূলীয় দ্বীপসমূহে সৈকত বালির মজুত চিহ্নিত করা হয়েছে।
• খনিজ লবণ:
– বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এবং খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে সমুদ্রের লোনা পানি বাষ্পীভবন বা সৌর পদ্ধতিতে আটকে রেখে লবণ উৎপাদন করা হয়।
– যা প্রধান খনিজ সম্পদ নয়।
∴ সুতরাং সঠিক উত্তর কয়লা।
উৎস: বাংলাপিডিয়া।
প্রশ্ন ১২৯. এল নিনো বাংলাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক আবহাওয়ায় কীভাবে প্রভাব ফেলে?
ক) শীতকালীন তাপমাত্রা বৃদ্ধি
খ) বর্ষার বৃষ্টিপাতের ধরনে অনিয়ম সৃষ্টি করে
গ) গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কমায়
ঘ) ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধি পায়
সঠিক উত্তর: খ) বর্ষার বৃষ্টিপাতের ধরনে অনিয়ম সৃষ্টি করে
Live MCQ Analytics: Right: 20%; Wrong: 34%; Unanswered: 45%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
◉ এল নিনো বাংলাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক আবহাওয়ায় বর্ষার বৃষ্টিপাতের ধরনে অনিয়ম সৃষ্টি করে।
– বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা কমানোর কোনো সরাসরি সম্পর্ক এল নিনোর সাথে পাওয়া যায় না।
– এল নিনো সাধারণত বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বাড়ায় না, বরং কিছু ক্ষেত্রে এটি ঘূর্ণিঝড়ের ফ্রিকোয়েন্সি বা তীব্রতা কমাতে পারে। – এল নিনো সাধারণত শীতকালীন তাপমাত্রার উপর সরাসরি বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে না বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।
– এর প্রভাব বেশি দেখা যায় বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত এবং সামগ্রিক জলবায়ু প্যাটার্নে।
– শীতকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ এল নিনোর সাথে সরাসরি যুক্ত নয় এই অঞ্চলে।
• এল নিনো:
– এল নিনো হলো প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার একটি জলবায়ু ঘটনা,
– যা বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক আবহাওয়ার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।
– বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবহাওয়ার ক্ষেত্রে এল নিনোর প্রভাব নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যায়:
– এল নিনোর সময় উষ্ণ সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতি ঘূর্ণিঝড় গঠনের জন্য অনুকূল পরিবেশ কমিয়ে দেয়।
– তবে, এটি সম্পূর্ণরূপে ঘূর্ণিঝড় বন্ধ করে না; শুধু তাদের ধরন বা সময় পরিবর্তন করতে পারে।
∴ সুতরাং সঠিত উত্তর বর্ষার বৃষ্টিপাতের ধরনে অনিয়ম সৃষ্টি করে।
উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। এবং NOAA ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১৩০. বাংলাদেশের ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন‘ কবে প্রণীত হয়?
ক) ২০০৫ খ) ২০০৮
গ) ২০১২ ঘ) ২০১৫
সঠিক উত্তর: গ) ২০১২
Live MCQ Analytics: Right: 38%; Wrong: 20%; Unanswered: 40%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
◉ বাংলাদেশের ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন‘ ২০১২ সালে প্রণীত হয়।
– অন্য অপশনগুলো যথা উপযুক্ত নয়।
• বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন:
– দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাঠামো গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।
– ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এই আইন প্রণীত হয়।
– ২০১২ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে।
– বাংলাদেশের সংসদে ‘দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২’ পাসের মাধ্যমে এই অধিদপ্তর গঠিত হয়।
উৎস: জাতীয় তথ্য বাতায়ন।
সাধারণ বিজ্ঞান
প্রশ্ন ১৩১. তরঙ্গের বেলায় কোন্টি সত্য?
ক) তড়িৎ চৌম্বকতরঙ্গ আলোর বেগে গমন করে
খ) শব্দতরঙ্গ একধরনের তড়িৎ চৌম্বকতরঙ্গ
গ) সকল তরঙ্গেই প্রতিফলন-প্রতিসরণ হয় না
ঘ) তরঙ্গবেগ হলো এর কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুপাত
সঠিক উত্তর: ক) তড়িৎ চৌম্বকতরঙ্গ আলোর বেগে গমন করে
Live MCQ Analytics: Right: 33%; Wrong: 27%; Unanswered: 38%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ:
– যখন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্রের পর্যাবৃত্ত আন্দোলন স্থানান্তরিত হয়, তখন একে বলা হয় বিদ্যুৎচুম্বকীয় বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ।
– এই ধরনের তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ার জন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না।
যেমন- আলোর তরঙ্গ, গামা রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের উদাহরণ।
তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ আলোর বেগে (3 × 108 m/s) চলাচল করে।
তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ t = 0 সময়ে উৎপন্ন হলে এবং কোনো প্রকার বাঁধাপ্রাপ্ত না হলে অর্থাৎ মুক্ত স্থানে (Free Space) একই বেগ অর্থাৎ আলোর বেগে প্রবাহিত হয়। বিভিন্ন তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের মধ্যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর পার্থক্য রয়েছে তবে মুক্তস্থানে সকলেরই বেগ সমান।
অন্য অপশনগুলোর মধ্যে –
খ) শব্দ একটি যান্ত্রিক তরঙ্গ, কারণ বস্তুকণার কম্পনের ফলে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং সেটি সঞ্চালনের জন্য একটি স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের দরকার হয়। শব্দ তরঙ্গের বেগ মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যেমন- বায়বীয় মাধ্যমে এর বেগ কম, তরলে তার চেয়ে বেশি, কঠিন পদার্থে আরো বেশি। যেকোনো তরঙ্গের মতোই শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং উপরিপাতন হতে পারে।
গ) প্রায় সব তরঙ্গেরই প্রতিফলন কিংবা প্রতিসরণ হয়।
ঘ) তরঙ্গ নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ঐ তরঙ্গের বেগ বা সংক্ষেপে তরঙ্গ বেগ বলে। অর্থাৎ তরঙ্গ বেগ হলো কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গুণফল, অনুপাত নয়। যেমন: v = fλ.উৎস: পদার্থবিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি এবং পদার্থ প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ১৩২. হিগের কণার (Higgs Particle) প্রকৃতির সাথে কোন বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর নাম জড়িয়ে আছে?
ক) স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু খ) সত্যেন্দ্র নাথ বসু
গ) প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম ঘ) ড. কুদরত-ই-খুদা
সঠিক উত্তর: খ) সত্যেন্দ্র নাথ বসু
Live MCQ Analytics: Right: 51%; Wrong: 27%; Unanswered: 21%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
– বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু 1924 সালে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ধারণা ব্যবহার করে বিকিরণ সংক্রান্ত কোয়ান্টাম সংখ্যায়নতত্ত্ব প্রদান করেন। এজন্য বিজ্ঞানী বসুকে কোয়ান্টাম সংখ্যায়নতত্ত্বের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়, এবং তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একশ্রেণির মৌলিক কণাকে বোসন (Boson) নাম দেওয়া হয়। 1900 থেকে 1930 সাল পর্যন্ত এই সময়টিতে হাইজেনবার্গ, শ্রোডিঙ্গার, ডিরাকসহ অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী মিলে পদার্থের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।
বোসন (Boson):
– মৌলিক বলগুলো কাজ করে কণার আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এই বলবাহী কণাগুলোই হচ্ছে বোসন।
– এদের স্পিন পূর্ণসংখ্যা 0, 1 ইত্যাদি।
– বোসন কণা পাউলির বর্জন নীতি মানে না।
– এদের আলাদা প্রতিকণা নেই।
– এরা নিজেরাই নিজেদের প্রতিকণা।
– স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুসারে বোসন কণাগুলো দুই ধরনের।
যথা-
(i) গেজ বোসন (Gauge Boson):
– এদের স্পিন হলো 1 ।
– এই কণাগুলো হলো- গণ্ডুওন (g), ফোটন (γ) এবং W ও Z বোসন।
• গণ্ডুণ্ডন: গণ্ডুওন কণা হলো সবল নিউক্লিয় বলবাহী কণা। এর নিশ্চল ভর শূন্য।
• ফোটন: এই কণা তাড়িতচৌম্বক বল বহন করে। এর নিশ্চল ভর শূন্য।
• W ও Z বোসন: W+, W– এবং W0 এই তিনটি বোসন কণা দুর্বল নিউক্লিয় বলের বাহক। এ কণাগুলোর ভর আছে।
(ii) হিগস বোসন (Higgs Boson):
– হিগস বোসন এর স্পিন 0, তবে এর ভর আছে।
– হিগস বোসন বুঝতে হলে হিগস ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানতে হবে। হিগস ক্ষেত্র একটি তাত্ত্বিক বলক্ষেত্র যা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই ক্ষেত্রের কাজ হলো মৌলিক কণাগুলোকে ভর প্রদান করা।
– যখন কোনো ভরহীন কণা হিগস ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তা ধীরে ধীরে ভর লাভ করে। ফলে তার চলার গতি ধীর হয়ে যায়।
– হিগস বোসনের মাধ্যমে ভর কণাতে স্তানান্তরিত হয়। হিগস ক্ষেত্র ভর সৃষ্টি করে না, তা কেবল ভর স্তানান্তরিত করে হিগস বোসনের মাধ্যমে।
– এই হিগস বোসনই ঈশ্বর কণা (God’s Particle) নামে পরিচিত।
উৎস: পদার্থবিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি এবং পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ১৩৩. কোন্ গ্যাস গ্রিন হাউস ইফেক্ট ঘটায়?
ক) হাইড্রোজেন খ) নাইট্রোজেন
গ) অক্সিজেন ঘ) মিথেন
সঠিক উত্তর: ঘ) মিথেন
Live MCQ Analytics: Right: 76%; Wrong: 7%; Unanswered: 15%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
– অপশনে উল্লিখিত গ্যাসসমূহের মধ্যে মিথেন গ্যাস গ্রিন হাউস ইফেক্ট ঘটায়।
গ্রিন হাউজ প্রভাব:
– শীতপ্রধান দেশে গ্রিন হাউসের (কাঁচ নির্মিত একটি ঘর) মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সবুজ উদ্ভিদ জন্মানো হয়।
– গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ শীতপ্রধান দেশের গ্রিন হাউস ঘরের ন্যায় সূর্য থেকে আগত রশ্মি তাপ বিকিরণে বাঁধা সৃষ্টি করে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে।
– গ্রিন হাউস গ্যাস কর্তৃক বায়ুমণ্ডলের এইরূপ তাপ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে গ্রিন হাউস অ্যাফেক্ট (Greenhouse effect) বলে।
– গ্রিন হাউস অ্যাফেক্ট কথাটি সর্বপ্রথম সোভানটে আরহেনিয়াস প্রথম ব্যবহার করেন।
– গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ হলো- কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO2), মিথেন (CH4), নাইট্রাস অক্সাইড (N2O), ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC) ইত্যাদি।
– বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক হিসেবে নিম্নে গ্রিন হাউস গ্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-
• গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ (Green House Gases):
১। কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO2):
– কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্ণহীন, সামান্য গন্ধযুক্ত কার্বন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত একটি গ্যাস। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ০.০৩ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড। জীবের প্রশ্বাসের সাথে কার্বন ডাই-অক্সাইড, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে, উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের পচন, মোটরযান ও শিল্প কারখানার জ্বালানি (কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, তৈল) পোড়ানো থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে যোগ হয়। বর্তমানে তরল ও কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড রেফ্রিজারেন্ট হিসেবে আইসক্রিম, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। সবুজ উদ্ভিদ এর খাদ্য প্রস্তুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করলেও বন উজাড় বৃদ্ধি পাওয়ায়, অধিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার, মোটরযানের সংখ্যা প্রভৃতি বৃদ্ধির কারণে বায়ুমণ্ডলে বিশ্বব্যাপী কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে এবং বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে।
২। মিথেন (CH4):
– প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন। এছাড়াও জলাভূমিতে পানির নিচে পানা পচনের মাধ্যমে, ধানের বর্জ্য অবশিষ্টাংশের পচন থেকে মিথেন পাওয়া যায়। তাপ ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে মিথেন কার্বন ডাই-অক্সাইডের চাইতে ২০ গুণ বেশি তাপ ধারণ করে।
৩। ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC):
– সিএফসি সাধারণত বিষমুক্ত, নিষ্ক্রিয় এবং ফ্লোরিন ও কার্বনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ। সিএফসি হিমায়নে (ফ্রিজ, এসি) ও স্প্রে-ক্যানে (অ্যারেসোল), মাইক্রো ইলেকট্রিক সার্কিট ও প্লাস্টিক ফোমে ব্যবহৃত হয়।
৪। নাইট্রাস অক্সাইড (N2O):
– অক্সিজেনের সাথে নাইট্রোজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ তৈরি করে। এটিও বর্ণহীন, সামান্য মিষ্টিগন্ধযুক্ত। এই গ্যাসের উৎসসমূহ হলো মোটরযান, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ রাসায়নিক সার, কারখানা।
অন্যদিকে,
– নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্রীন হাউজ গ্যাস নয়, এই গ্যাসগুলো বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে।
– হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা গ্যাস যা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় একটি রংহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাস।
উৎস: পরিবেশ বিজ্ঞান, বিবিএ বাংলা প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ১৩৪. বিরল ভূতল খনিজ (Rare-Earth Minerals) সম্পর্কিত কোন তথ্যটি সঠিক?
ক) এর মধ্যে ১৫টি ধাতু রয়েছে
খ) লিথিয়াম এই খনিজের মধ্যে অন্যতম সদস্য
গ) এর অসাধারণ চৌম্বক ধর্ম রয়েছে
ঘ) ইউক্রেন এ খনিজ উৎপাদনে শীর্ষ অবস্থানে আছে
সঠিক উত্তর: গ) এর অসাধারণ চৌম্বক ধর্ম রয়েছে
Live MCQ Analytics: Right: 6%; Wrong: 33%; Unanswered: 60%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
– বিরল ভূতল খনিজ (Rare-Earth Minerals) সম্পর্কিত সঠিক তথ্যটি হচ্ছে- বিরল ভূতল খনিজ পদার্থের অসাধারণ চৌম্বক ধর্ম রয়েছে।
অন্যদিকে,
– বিরল ভূতল খনিজ মৌল রয়েছে ১৭ টি।
– বিরল ভূতল খনিজের মধ্যে কিছু মাত্রায় লিথিয়াম পাওয়া যায় কিন্তু এটি এগুলোর অন্যতম সদস্য নয়।
– উৎপাদনের দিক থেকে চীন শীর্ষস্থানে রয়েছে।
বিরল খনিজ:
– ১৭টি মৌলের একটি গ্রুপ হলো বিরল খনিজ।
– ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রির (আইইউপিএসি) নামকরণ অনুযায়ী, পর্যায় সারণির ল্যান্থানাইড সিরিজের ১৫টি মৌলের (ল্যান্থানাম, সিরিয়াম, প্রাসিয়োডিমিয়াম, নিওডিমিয়াম, প্রমিথিয়াম, স্যামারিয়াম, ইউরোপিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম, টারবিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম, হোলমিয়াম, আরবিয়াম, থুলিয়াম, ইটারবিয়াম ও লুটেশিয়াম) সঙ্গে স্ক্যান্ডিয়াম ও ইট্রিয়ামকে একত্রে বিরল খনিজ বলছে যুক্তরাষ্ট্রের জিওসায়েন্স ইনস্টিটিউট।
– যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক খনিজ সংস্থা ভার্জিনিয়া এনার্জির মতে, বিরল খনিজের দুটি ভাগ রয়েছে- হালকা ও ভারী।
– হালকা বিরল খনিজের মধ্যে আছে ল্যান্থানাম, সিরিয়াম, প্রাসিয়োডিমিয়াম, নিওডিমিয়াম, প্রমিথিয়াম ও স্যামারিয়াম।
– আর ভারী বিরল খনিজের মধ্যে আছে ইউরোপিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম, টারবিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম, হোলমিয়াম, আরবিয়াম, থুলিয়াম, ইটারবিয়াম ও লুটেশিয়াম। এছাড়া আছে স্ক্যান্ডিয়াম ও ইট্রিয়াম।
– আধুনিক প্রযুক্তি, শিল্প ও প্রতিরক্ষা খাতে বিরল খনিজ অপরিহার্য। আধুনিক প্রযুক্তির প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিরল খনিজের ব্যবহার আছে।
যেমন- • মুঠোফোন, কম্পিউটারের হার্ডড্রাইভ, বৈদ্যুতিক ও হাইব্রিড যানবাহন, টেলিভিশনের এলইডি ডিসপ্লে তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
• প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ প্রযুক্তি যেমন- লেজার, রাডার ও সোলার সিস্টেম, জেট ইঞ্জিন, মিসাইল সিস্টেম ও স্যাটেলাইটেও এর ভূমিকা আছে।
• এছাড়া নবায়নযোগ্য শক্তি, যেমন- বায়ু টারবাইন ও সৌর প্যানেল এবং চিকিৎসা, অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি (যন্ত্র নির্মাণশিল্প) এবং কাচ ও সিরামিক শিল্পও এখন বিরল খনিজনির্ভর। তবে এদের উত্তোলন এবং পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়বহুল।
– চীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিরল খনিজ মজুতের অধিকারী। দেশটিতে ৪ কোটি ৪০ লাখ মেট্রিক টন বিরল খনিজ মজুত আছে। বর্তমানে বিরল খনিজ খননের ৭০ শতাংশ, প্রক্রিয়াজাতকরণের ৯০ শতাংশ আর চুম্বক তৈরির ৯৩ শতাংশই চীনের হাতে।
– দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ব্রাজিল, দেশটির মজুতের পরিমাণ ২ কোটি ১০ লাখ টন।
– এছাড়া ভারতে ৬৯ লাখ টন, অস্ট্রেলিয়ায় ৫৭ লাখ টন, রাশিয়ায় ৩৮ লাখ টন, ভিয়েতনামে ৩৫ লাখ টন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৯ লাখ টন বিরল খনিজের মজুত আছে।
– উৎপাদনের দিক থেকেও চীন শীর্ষস্থানে রয়েছে। ২০২৪ সালে দেশটি ২ লাখ ৭০ হাজার টন বিরল খনিজ উৎপাদন করেছে।
– একই বছর ব্রাজিল ও ভারত ২ হাজার ৯০০ টন, রাশিয়া ২ হাজার ৫০০ টন এবং যুক্তরাষ্ট্র ৪৫ হাজার টন বিরল খনিজ উৎপাদন করেছে।
– আর ১৩ হাজার টন উৎপাদন নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে অস্ট্রেলিয়া।
– বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন সিলেট, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহের পাহাড়ি স্রোতধারা, গাইবান্ধার যমুনা নদী, ধরলা নদীর বালু, এবং দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে তেজস্ক্রিয় মৌল ও বিরল মৃত্তিকা মৌলের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।
– বিশেষ করে মোনাজাইট ও জিরকনের সঙ্গে যুক্ত এসব মৌলের মধ্যে লিথিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, স্যামারিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম, টারবিয়াম ও ডিসপ্রোসিয়াম উল্লেখযোগ্য।
– গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি কেজি বালুতে ৬০–১৭৬ মিলিগ্রাম বিরল মৌল থাকতে পারে, যা দেশের জন্য বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা তৈরি করছে।
উৎস: দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা [লিঙ্ক] [লিঙ্ক] এবং ব্রিটানিকা ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১৩৫. কোন ধাতু পানিতে ফেললে আগুন ধরে যায়?
ক) সোডিয়াম খ) ম্যাগনেসিয়াম
গ) রেডিয়াম ঘ) ইউরেনিয়াম
সঠিক উত্তর: ক) সোডিয়াম
Live MCQ Analytics: Right: 49%; Wrong: 16%; Unanswered: 34%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
– সোডিয়াম ধাতুকে পানিতে ফেললে আগুন ধরে যায়।
সোডিয়াম:
– সোডিয়াম একটি সক্রিয় ধাতু।
– সোডিয়াম পানির সঙ্গে দ্রুত বিক্রিয়া করে তাপ উৎপন্ন করে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত করে।
– এই বিক্রিয়াটি এতটাই দ্রুত হয় যে নির্গত হাইড্রোজেন গ্যাস আগুনের সংস্পর্শে এসে জ্বলে ওঠে।
– সোডিয়াম স্বাভাবিকভাবে বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, বাতাসের জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে এটি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
– সাধারণ বাতাসে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) এর একটি আস্তরণ তৈরি হয়, যা বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটে (NaHCO3) পরিণত হয়।
– সোডিয়ামকে সাধারণত কেরোসিন বা ন্যাপথার মতো inert তরলে ডুবিয়ে রাখা হয়, কারণ এটি নাইট্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না।
– তরল অবস্থায় সোডিয়াম কঠিন অবস্থার চেয়ে বেশি সক্রিয় এবং প্রায় ১২৫ °C (২৫৭ °F) তাপমাত্রায় এটি জ্বলে উঠতে পারে।
অন্যদিকে,
– ম্যাগনেসিয়াম সাধারণত +2 জারণ অবস্থায় থাকে। এটি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ডিএনএ, আরএনএ এবং এটিপি-এর সঙ্গে জড়িত।
– ইউরেনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক উপাদান, যা পারমাণবিক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
– রেডিয়াম অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় এবং এর যৌগগুলি অন্ধকারে হালকা নীল রঙের আলো ছড়ায়।
উৎস: ব্রিটানিকা ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১৩৬. EPI-এর পূর্ণরূপ কী?
ক) Extended Program on immunization
খ) Expanded program on immunization
গ) Essential polio immunization
ঘ) Extended pediatric immunization
সঠিক উত্তর: খ) Expanded program on immunization
Live MCQ Analytics: Right: 52%; Wrong: 36%; Unanswered: 11%; [Total: 3660]
ব্যাখ্যা:– EPI-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Expanded Program on Immunization যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO) এর একটি কার্যক্রম যার আওতায় শিশুদের প্রাণঘাতী কয়েকটি রোগের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।
বাংলাদেশে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম:
– রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে টিকার আবিষ্কার এবং টিকার প্রচলন মানুষের জন্য আশীর্বাদ।
– টিকার মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে চূড়ান্তভাবে নির্মূলের পূর্বে গুটি বসন্ত এককভাবে পৃথিবীর প্রায় ৩০-৪০ কোটি মানুষের প্রাণ হরণ করেছে।
– আবিষ্কৃত পোলিও ভ্যাকসিন OPV এবং এটির ব্যবহার দ্বারা বাংলাদেশ বর্তমানে পোলিও রোগ মুক্ত হয়েছে।
– এই টিকা বা ভ্যাকসিনের জন্যই রুবেলা, হাম, মাম্পস, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, পারটুসিস, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে।
– বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO) এর (Expanded Program on Immunization-EPI) কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের প্রাণঘাতী কয়েকটি রোগ, যথা- যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, টিটেনাস, পোলিও এবং হাম ইত্যাদির ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এছাড়াও হেপাটাইটিস-বি এবং হিমোফাইলা ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি-এর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।
– মা এবং শিশুকে টিটেনাস থেকে রক্ষার জন্য টিটেনাস টক্সেয়েড (tetanus toxoid) ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।
– ভ্যাকসিনেশনের জাতীয় কর্মসূচীতে নিচের ছক অনুযায়ী টিকা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়-
উৎস: প্রাণিবিজ্ঞান, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটানিকা।
প্রশ্ন ১৩৭. কোন স্পেস টেলিস্কোপ ২০২১ সালে হাবল টেলিস্কোপের স্থলাভিষিক্ত হয়?
ক) জেমস ওয়েব খ) পাথ ফাইন্ডার
গ) স্পিটজার ঘ) জন কেপলার
সঠিক উত্তর: ক) জেমস ওয়েব
Live MCQ Analytics: Right: 42%; Wrong: 12%; Unanswered: 45%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
– জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ ২০২১ সালে হাবল টেলিস্কোপের স্থলাভিষিক্ত হয়।
জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ:
– মহাকাশে পাঠানো এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ হচ্ছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (জেডব্লিউএসটি)।
– মহাজাগতিক রহস্য অনুসন্ধানের পাশাপাশি মহাবিশ্বের প্রান্তে কী আছে, তা নিয়েও আশ্চর্যজনক ছবি প্রকাশ করছে টেলিস্কোপটি।
– ২০২১ সালের ২৫ ডিসেম্বর মহাকাশে পাঠানোর পর থেকে টানা তিন বছর টেলিস্কোপটির মাধ্যমে দূরবর্তী বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলের তথ্য বিশ্লেষণসহ মহাজাগতিক রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।
– তিন বছর আগে এই দিনে দক্ষিণ আমেরিকার ফ্রেঞ্চ গায়ানা থেকে ইউরোপিয়ান আরিয়ান রকেটে করে মহাকাশে পাঠানো হয় জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ।
– জেমস ওয়েব টেলিস্কোপকে বিখ্যাত হাবল স্পেস টেলিস্কোপের উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
– প্রায় ৩০ বছর ধরে তৈরি করা হয়েছে টেলিস্কোপটি, খরচ হয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি মার্কিন ডলার।
– বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হলেও মাত্র তিন বছরের মধ্যেই টেলিস্কোপটি মহাজাগতিক তথ্য সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।
– জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এমন গ্যালাক্সির খোঁজ পেয়েছে যেটি পৃথিবী থেকে ১৩.৪ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।
– ২০২৩ সালে টেলিস্কোপটি প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরজাগতিক গ্রহ আবিষ্কার করে।
– এলএইচএস ৪৭৫বি নামের গ্রহটি পৃথিবীর মতোই দেখতে।
– জেমস ওয়েব বেশ কয়েকটি ব্ল্যাকহোলও আবিষ্কার করেছে। আর তাই টেলিস্কোপটির মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও অনেক চমকের খোঁজ পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।
উৎস: দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা [লিঙ্ক] এবং ব্রিটানিকা।
প্রশ্ন ১৩৮. QR কোডে ব্যবহৃত হয় –
ক) তড়িৎ চৌম্বকত্ব খ) রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি
গ) কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ঘ) অপটিক্যাল রিডিং
সঠিক উত্তর: ঘ) অপটিক্যাল রিডিং
Live MCQ Analytics: Right: 56%; Wrong: 15%; Unanswered: 28%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
– QR কোডে ব্যবহৃত হয়- অপটিক্যাল রিডিং।
QR কোড:
– QR কোড হলো এক ধরনের বারকোড, যা ছোট কালো ও সাদা বর্গক্ষেত্র দিয়ে তৈরি।
– এই বর্গক্ষেত্রগুলিতে তথ্য সংরক্ষিত থাকে, যা সহজে কম্পিউটার বা স্মার্টফোন স্ক্যানার দিয়ে পড়া যায়।
– কালো-সাদা স্কোয়ারগুলোতে সংখ্যা, ইংরেজি অক্ষর বা এমনকি জাপানি কানজি ও অন্যান্য অ-ল্যাটিন অক্ষরও রাখা যেতে পারে।
QR কোডের ব্যবহার:
– মূলত QR কোড তৈরি করা হয়েছিল অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ ট্র্যাক করার জন্য।
– এখন এটি বিজ্ঞাপন, টিকিট, পণ্য ট্র্যাকিং এবং আরও নানা কাজে ব্যবহার করা হয়।
QR কোড স্ক্যান ও বৈশিষ্ট্য:
– QR কোড স্ক্যান করতে ব্যবহারকারীদের ফোন বা লেজার স্ক্যানার প্রয়োজন হয়।
– বিশেষ সফটওয়্যার তথ্যটি ডিকোড করে দেখায়।
– সবচেয়ে বড় QR কোড (Version 40) 177 × 177 পিক্সেলের হয় এবং সবচেয়ে ছোট (Version 1) 21 × 21 পিক্সেলের হয়।
– Version 40 QR কোডে প্রায় 7,089টি সংখ্যা বা 4,296টি আলফানিউমেরিক অক্ষর সংরক্ষণ করা যায়।
– অনেক স্মার্টফোনে বিল্ট-ইন QR রিডার থাকায় এগুলি বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় সহজেই ব্যবহার করা যায়।
Source: 1. Kaspersky. 2. Britannica.
প্রশ্ন ১৩৯. ইথার সম্বন্ধে কোনটি মিথ্যা?
ক) এটি একটি রাসায়নিক তরল পদার্থ
খ) এটি একটি কাল্পনিক মাধ্যম যা মহাবিশ্বে সর্বত্র বিরাজমান ছিল
গ) এ মাধ্যম ছাড়া তাড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব নয়
ঘ) এ কাল্পনিক মাধ্যমটির স্থিতিস্থাপক ধর্ম ছিলো
সঠিক উত্তর: গ) এ মাধ্যম ছাড়া তাড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব নয়
Live MCQ Analytics: Right: 14%; Wrong: 85%; Unanswered: 0%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
• অপশন বিশ্লেষণ:
ক) সত্য: ইথার একটি রাসায়নিক তরল পদার্থ। (Chemistry).
– ডাই-ইথাইল ইথার (C4H10O) একটি বাস্তব রাসায়নিক যৌগ।
– এটি অতীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অ্যানেস্থেটিক (চেতনানাশক) হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
– এটি একটি উড়নশীল (volatile), দাহ্য (flammable) তরল দ্রাবক।
খ) সত্য: ইথার ছিল একটি কাল্পনিক মাধ্যম যা মহাবিশ্বে সর্বত্র বিদ্যমান বলে ধরা হতো। (Physics).
– ১৯ শতকে বিজ্ঞানীরা “লুমিনিফেরাস ইথার” নামক ধারণা দেন।
– তারা বিশ্বাস করতেন এটি সমগ্র মহাবিশ্বে বিরাজমান।
– ধারণা করা হতো আলো ও তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য এটি অপরিহার্য।
ঘ) সত্য: কাল্পনিক মাধ্যমে স্থিতিস্থাপক ধর্ম ছিল বলে মনে করা হতো। (Physics).
– বিজ্ঞানীরা তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে ইথারের স্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
– এর ফলে তরঙ্গ সঞ্চালিত হতে পারত।
– যেমন শব্দ তরঙ্গ চলাচলের জন্য স্থিতিস্থাপক মাধ্যম (বায়ু) প্রয়োজন হয়।
গ) মিথ্যা: এ মাধ্যম ছাড়া তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব নয়। (Physics).
• কেন মিথ্যা?
• ঐতিহাসিক প্রমাণ:
– মাইকেলসন–মর্লে পরীক্ষা (১৮৮৭) ইথারের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়।
– এতে প্রমাণিত হয় যে ইথার বাস্তবে নেই।
– এই পরীক্ষাই পরবর্তীকালে বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথ তৈরি করে।
• আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা:
– ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ প্রমাণ করে যে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ শূন্যতায়ও চলতে পারে।
– আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (১৯০৫) ইথারের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করে দেয়।
– তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ হলো বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের স্ব-প্রসারিত বিচ্যুতি।
• পরীক্ষামূলক প্রমাণ:
– নক্ষত্র থেকে আলো শূন্য মহাশূন্য পেরিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছায়।
– মহাকাশযানের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ শূন্য মহাশূন্যে সম্ভব।
– সব ধরনের তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ (রেডিও, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, দৃশ্যমান, আল্ট্রাভায়োলেট, এক্স-রে, গামা) শূন্যতায় ভ্রমণ করতে সক্ষম।
• বিস্তারিত আলোচনা:
– তড়িৎচৌম্বক (EM) তরঙ্গ, যেমন দৃশ্যমান আলো, শূন্য মহাশূন্যের মধ্য দিয়েই চলতে পারে এবং এদের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।
• ইথার ধারণা:
– ১৯শ শতকে পদার্থবিদরা মনে করতেন যে সব তরঙ্গের জন্য একটি মাধ্যম দরকার। যেমন শব্দ তরঙ্গের জন্য বায়ু ও জলতরঙ্গের জন্য পানি লাগে, তেমনি তারা ধারণা করেন যে আলোও শূন্যতায় ছড়াতে হলে কোনো এক বিশেষ মাধ্যম লাগবে। এই কাল্পনিক, অদৃশ্য ও সর্বব্যাপী মাধ্যমকে বলা হয় লুমিনিফেরাস ইথার।
• ইথার তত্ত্বের পতন:
– মাইকেলসন–মর্লে পরীক্ষা (১৮৮৭): তাঁরা পৃথিবীর গতির কারণে “ইথার বায়ু” (aether wind) শনাক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।
– ফল: কোনো দিকেই আলোর গতির পার্থক্য পাওয়া যায়নি। এটি ছিল ইথারের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রথম শক্ত প্রমাণ।
– আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা (১৯০৫): এ তত্ত্ব প্রমাণ করে যে শূন্যতায় আলোর গতি সব পর্যবেক্ষকের জন্য একই এবং কোনো মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল নয়। ফলে ইথার ধারণা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়।
সূত্র: – NASA. [link] – Britannica. [link]
– European Journal of Applied Physics. [link]
প্রশ্ন ১৪০. আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে ব্যবহৃত শব্দের কম্পাঙ্ক কত?
ক) ০.০১-০১ মেগাহার্জ খ) ০১-১০ মেগাহার্জ
গ) ১০-২০ মেগাহার্জ ঘ) ২০-৩০ মেগাহার্জ
সঠিক উত্তর: খ) ০১-১০ মেগাহার্জ
Live MCQ Analytics: Right: 8%; Wrong: 16%; Unanswered: 75%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
আল্ট্রাসনোগ্রাফি:
– আল্ট্রাসনোগ্রাফি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দের প্রতিফলনের উপর নির্ভরশীল।
– উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ যখন শরীরের গভীরের কোনো অঙ্গ বা পেশি থেকে প্রতিফলিত হয় তখন প্রতিফলিত তরঙ্গের সাহায্যে ঐ অঙ্গের অনুরূপ একটি প্রতিবিম্ব মনিটরের পর্দায় গঠন করা হয়।
– রোগ নির্ণয়ের জন্য যে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হয় সেই শব্দের কম্পাঙ্ক 1-10 মেগাহার্টজ হয়ে থাকে।
– আট্রাসনোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার স্ত্রীরোগ এবং প্রসূতিবিজ্ঞানে লক্ষ্য করা যায়।
– এর সাহায্যে ভ্রুণের আকার, পূর্ণতা, ভ্রুণের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থান জানা যায়।
– প্রসূতিবিদ্যায় এটি একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য কৌশল।
– আল্ট্রাসনোগ্রাফির সাহায্যে পিত্তপাথর, জড়ায়ুর টিউমার এবং অন্যান্য পেলভিক মাসের উপস্থিতিও শনাক্ত করা যায়।
– এক্সরের তুলনায় আল্ট্রাসনোগ্রাফি অধিকতর নিরাপদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, তবুও আল্ট্রাসাউন্ড খুব সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করতে হবে।
উৎস: পদার্থবিজ্ঞান, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটানিকা।
প্রশ্ন ১৪১. কোনটি শরীরে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে?
ক) খনিজ লবণ খ) ভিটামিন
গ) স্নেহ ঘ) আমিষ
সঠিক উত্তর: ঘ) আমিষ
Live MCQ Analytics: Right: 53%; Wrong: 19%; Unanswered: 27%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
আমিষ (Protein):
– আমিষ বা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত।
– আমিষে শতকরা 16 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে।
– আমিষে সামান্য পরিমাণে সালফার, ফসফরাস এবং আয়রনও থকে।
– নাইট্রোজেন এবং শেষোক্ত উপাদানগুলোর উপস্থিতির কারণে আমিষের গুরুত্ব শর্করা ও স্নেহ পদার্থ থেকে আলাদা। শুধু আমিষজাতীয় খাদ্যই শরীরে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে বলে পুষ্টিবিজ্ঞানে আমিষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
আমিষের উৎস:
– মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, শিমের বীচি, শুঁটকি মাছ, চিনাবাদাম ইত্যাদি থেকে আমিষ পাওয়া যায়।
– উৎস অনুযায়ী আমিষ দুই ধরনের।
যথা- প্রাণিজ আমিষ এবং উদ্ভিজ্জ আমিষ।
প্রাণিজ আমিষ:
– মাছ, মাংস, ডিম, পনির, ছানা, কলিজা বা যকৃৎ ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ। এসব খাদ্যে দেহের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়।
উদ্ভিজ্জ আমিষ:
– ডাল, চিনাবাদাম, শিমের বীচি ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষ। একসময় ধারণা করা হতো এগুলো প্রাণিজ আমিষের তুলনায় কম পুষ্টিকর, কারণ উদ্ভিজ্জ আমিষে প্রয়োজনীয় সবকয়টি অ্যামাইনো এসিড থাকে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিজ্জ আমিষ প্রাণিজ আমিষের মতোই সকল অ্যামাইনো এসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে ধারণ করে।
– অনেক সময়, দুই বা ততোধিক উদ্ভিজ্জ আমিষ একত্রে রান্না করা যায়। কিন্তু এতে অ্যামাইনো এসিডের অনুপাতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না।
উৎস: জীববিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি।
প্রশ্ন ১৪২. হাইড্রোজেন বোমায় ক্রিয়া করে-
ক) ফিশন বিক্রিয়া খ) ফিউশন বিক্রিয়া
গ) ফিশন ও ফিউশন উভয়টিই ঘ) সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়া
সঠিক উত্তর: গ) ফিশন ও ফিউশন উভয়টিই
Live MCQ Analytics: Right: 6%; Wrong: 70%; Unanswered: 23%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
• হাইড্রোজেন বোমা:
– হাইড্রোজেন বোমায় মূলত পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে।
– এখানে ফিশন ও ফিউশন উভয় বিক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।
– হাইড্রোজেন বোমার মূল শক্তি ফিউশন বিক্রিয়া থেকে আসলেও, সেই বিক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রথমে একটি ফিশন বিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।
– প্রথমে ফিশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়।
– সেই শক্তি দিয়ে হাইড্রোজেন আইসোটোপ (ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম)-এর ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হয়।
– এই ফিউশন বিক্রিয়ায় অতি অল্প সময়ে বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয়।
– হাইড্রোজেন বোমা কে বলা হয় থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা।
– এটি সাধারণ পারমাণবিক বোমার তুলনায় অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী।
– সঠিক উত্তর: গ) ফিশন ও ফিউশন উভয়টিই।
– উল্লেখ্য, অপশনে, “ফিশন ও ফিউশন উভয়টিই” – না থাকে – তাহলে, “ফিউশন বিক্রিয়া” – উত্তর হিসেবে গণ্য হবে।
• নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া:
– যে বিক্রিয়ায় কোনো মৌলের নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন ঘটে তাকে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বলে।
– রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুর বা আয়নের সর্ববহিস্থ শক্তিস্তর থেকে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে। নিউক্লিয়াসের কোনো পরিবর্তন হয় না।
– কিন্তু নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন ঘটে, এখানে ইলেকট্রনের কোনো ভূমিকা নেই।
– এ বিক্রিয়ার ফলে নতুন মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়।
– যে বিক্রিয়ার ফলে ছোট ছোট মৌলের নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে বড় মৌলের নিউক্লিয়াস অথবা কোনো বড় মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙে একাধিক ছোট মৌলের নিউক্লিয়াস তৈরি হয় সেই বিক্রিয়াকে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বলে।
– নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়।
– বিভিন্ন রকমের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া আছে; তবে এদের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া ও নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া অন্যতম।
• নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া:
– যে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় ছোট ছোট নিউক্লিয়াসসমূহ একত্রিত হয়ে বড় নিউক্লিয়াস গঠন করে তাকে নিউক্লিয় ফিউশন (Fusion) বিক্রিয়া বলে।
নিচে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হলো-
• নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া:
– যে নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ায় কোনো বড় এবং ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙে ছোট ছোট মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় তাকে নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া বলে।
– এই বিক্রিয়ার সাথে নিউট্রন আর প্রচুর (Fission) পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়।
– স্বল্পগতির নিউট্রন দিয়ে কে আঘাত করলে নিউক্লিয়াসটি প্রায় দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হয়ে এর নিউক্লিয়াস ও তিনটি নিউট্রন ও তার সাথে প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। এটি একটি নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া।
– এই বিক্রিয়ার ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়, যা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পারমাণবিক অস্ত্র, বিশেষত পারমাণবিক বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
উৎস: ব্রিটানিকা [link]
প্রশ্ন ১৪৩. কোন গ্রহে ‘Curiosity’ মহাকাশযানটি প্রেরণ করা হয়?
ক) শনি খ) মঙ্গল
গ) বৃহস্পতি ঘ) ইউরেনাস
সঠিক উত্তর: খ) মঙ্গল
Live MCQ Analytics: Right: 38%; Wrong: 6%; Unanswered: 55%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
– মঙ্গল গ্রহে ‘Curiosity’ মহাকাশযানটি প্রেরণ করা হয়।
মঙ্গলে প্রেরিত ‘কিউরিওসিটি’:
– মঙ্গল গ্রহে পাঠানো যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার যান ‘কিউরিওসিটি’।
– ২০১২ সালের ৫ আগস্ট মহাকাশযানটি মঙ্গলের পৃষ্ঠে সফলভাবে অবতরণ করে।
– ‘লাল গ্রহ’ মঙ্গলে গবেষণাকাজে এটাকে বড় একটি অর্জন বিবেচনা করা হয়। পরের বছরের একই দিনে মহাকাশযানটিতে বাজানো হয় ‘হ্যাপি বার্থডে’ গান। এর মধ্য দিয়ে মঙ্গলে প্রথমবারের মতো কোনো সুর বেজে ওঠে।
– মঙ্গল গ্রহে মাকড়সার জালের মতো দেখতে বেশ রহস্যময় একটি অঞ্চলের সন্ধান পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। মঙ্গল গ্রহে থাকা মাকড়সার জালটি আসলে একধরনের স্ফটিকযুক্ত খনিজের কাঠামো।
– সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহে মাকড়সার জালের মতো দেখতে রহস্যময় অঞ্চলের ছবি তুলেছে নাসার কিউরিওসিটি রোভার।
– কিউরিওসিটি রোভার বর্তমানে ‘গেল ক্রেটার’ নামের বিশাল খাদের রহস্য উন্মোচনে কাজ করছে।
– মঙ্গল গ্রহে কিউরিওসিটির রোভার অবতরণ করার পর থেকেই মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছে রোভারটি।
– বর্তমানে রোভারটি মঙ্গল গ্রহে থাকা বক্সওয়ার্ক প্যাটার্ন নামের শক্ত নিচু শৈলশিরা বিশ্লেষণ করছে।
– প্রবালের মতো পাথরের ছবি মঙ্গলবুকে ধারণ করেছে রোভার কিউরিওসিটির রিমোট মাইক্রো ইমেজার।
– নাসার কিউরিওসিটি মার্স রোভার সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে একটি পাথরের কালো ও সাদা ছবি পাঠিয়েছে। সে পাথরটি দেখতে পৃথিবীতে পাওয়া প্রবালের টুকরার মতো।
– মার্কিন মহাকাশ সংস্থা–নাসার তথ্যমতে, হালকা রঙের পাথরটি বাতাসের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। শিলাটি মঙ্গল গ্রহের অববাহিকা গ্যাল ক্রেটারে নামের খাদে পাওয়া গেছে। শিলাটি প্রায় এক ইঞ্চি প্রশস্ত।
– সমুদ্রের তলদেশে সাধারণভাবে দেখা প্রবালের মতো শাখা–প্রশাখা দেখা যাচ্ছে। শিলাটির বর্ণহীন ছবিটি কিউরিওসিটির রিমোট মাইক্রো ইমেজারের মাধ্যমে তোলা হয়েছে। এটি একটি উচ্চ রেজল্যুশনের টেলিস্কোপিক ক্যামেরা।
– এখন পর্যন্ত কিউরিওসিটি ১৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ খাদের প্রায় ৩৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। চলার পথটি আঁকাবাঁকা হওয়ার কারণে ধীরভাবে কাজ করছে রোভারটি।
উৎস: দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা [লিঙ্ক] [লিঙ্ক] [লিঙ্ক] এবং ব্রিটানিকা।
প্রশ্ন ১৪৪. ফিটকিরিতে কত অণু পানি থাকে?
ক) ২৪ খ) ১৫
গ) ০৭ ঘ) ০৫
সঠিক উত্তর: ক) ২৪
Live MCQ Analytics: Right: 52%; Wrong: 9%; Unanswered: 38%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
ফিটকিরি:
– প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে এন্টিসেপটিক হিসেবে ফিটকিরির ব্যবহার প্রচলিত।
– ফিটকিরি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, পটাশিয়াম সালফার ও ২৪ অণু পানির যৌগ।
– ফিটকিরির রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে [K2SO4.Al2(SO4)3. 24H2O] ।
– ফিটকিরি বা পটাস অ্যালামে ২৪ অণু কেলাস পানি যুক্ত থাকে।
– ফিটকিরি মানুষের কাছে পটাশ অ্যালাম নামে পরিচিত।
– ফিটকিরি একটি দ্বি-লবণ অর্থাৎ দুটি লবণ (পটাসিয়াম সালফেট এবং অ্যালুমিনিয়াম সালফেট) এর সাধারণ মিশ্রণ।
– অ্যালাম কঠিন অবস্থায় সুনির্দিষ্ট আকৃতির কেলাস।
– এটি সাধারণত কঠিন অবস্থায় বাজারে প্রচলিত।
– বিভিন্ন কাজে ফিটকিরি ব্যবহার করা হয়।
যেমন-
• এটি জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
• কোথাও কেটে গেলে, ছিঁড়ে গেলে সেখানে পানিতে ভিজানো ফিটকিরি ঘষে দেওয়া হয়।
• ফিটকিরি কঠিন অবস্থায় থাকে বলে প্রথমে পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয় অথবা পানিতে দ্রবীভূত করে তা ক্ষতস্থানে লাগানো হয়।
• খাবার পানি বিশুদ্ধ বা জীবাণুমুক্ত করার জন্য এর সাথে পরিমাণমত ফিটকিরি ব্যবহারের ঘণ্টাখানেক আগে দিয়ে রাখা হয়।
• ফিটকিরি গলে গেলে পানি ছেঁকে নেয়া হয়।
• অনেকে দাড়ি কাটার পর এন্টিসেপটিক হিসেবে ফিটকিরি ব্যবহার করেন।
• এটি আফটার সেভ লোশান হিসেবে কাজ করে।
• ফিটকিরি রক্তক্ষরণও বন্ধ করে।
উৎস: রসায়ন, নবম-দশম শ্রেণি এবং রসায়ন প্রথম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ১৪৫. ‘Necessary evil’ কোনটি?
ক) প্রস্বেদন খ) অভিস্রবন
গ) ব্যাপন ঘ) শোষণ
সঠিক উত্তর: ক) প্রস্বেদন
Live MCQ Analytics: Right: 55%; Wrong: 7%; Unanswered: 37%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
প্রস্বেদন (Transpiration):
– উদ্ভিদ প্রধানত মূল দিয়ে তার প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করে। শোষিত পানির অতি সামান্য অংশ উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলির জন্য ব্যয় হয়, অবশিষ্ট পানি উদ্ভিদের বায়বীয় অংশ দিয়ে বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়ে যায়।
– সাধারণত স্থলজ উদ্ভিদ যে শারীরতত্ত্বীয় প্রক্রিয়ায় তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানি বের করে দেয়, সেটাই প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া। – এই কাজটি তার বায়বীয় অঙ্গের কোন অংশের মাধ্যমে ঘটে, তার ভিত্তিতে এদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
যথা:
১। পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন (Stomatal transpiration):
– পাতায়, কচিকাণ্ডে, ফুলের বৃতি ও পাপড়িতে দুটি রক্ষীকোষ (Guard cell) বেষ্টিত এক ধরনের রন্ধ্র থাকে, এদেরকে পত্ররন্ধ্র (একবচন stoma, বহুবচন stomata) বলে। কোনো উদ্ভিদের মোট প্রস্বেদনের 90-95% হয় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে।
২। কিউটিকুলার প্রস্বেদন (Cuticular transpiration):
– উদ্ভিদের বহিঃত্বকে বিশেষ করে পাতার উপরে এবং নিচে কিউটিনের আবরণ থাকে, এ আবরণকে কিউটিকল বলে। কিউটিকল ভেদ করে কিছু পানি বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়, এ প্রক্রিয়াকে কিউটিকুলার প্রস্বেদন বলে।
৩। লেন্টিকুলার প্রস্বেদন (Lenticular transpiration):
– উদ্ভিদে গৌণ বৃদ্ধি হলে কাণ্ডের বাকল ফেটে লেন্টিসেল নামক ছিদ্র সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেলের ভিতরের কোষগুলো আলাদাভাবে সজ্জিত থাকে এবং এর মাধ্যমে কিছু পানি বাইরে বেরিয়ে যায়, একে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন বলে।
প্রস্বেদন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল (Transpiration is a necessary evil):
– প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার উপরে সজীব উদ্ভিদ কোষের বিপাকীয় কার্যক্রম অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রস্বেদনের ফলে জাইলেমবাহিকায় টান পড়ে। এই টানের ফলে উদ্ভিদের মূলরোম কর্তৃক শোষিত পানি এবং খনিজ লবণ পাতায় পরিবাহিত হয়। এ টানের ঘাটতি হলে পানি শোষণ কমে যাবে এবং খাদ্য প্রস্তুতসহ অনেক বিপাকীয় কার্যক্রম শ্লথ হয়ে যাবে। প্রস্বেদনের ফলে পাতার মেসোফিলে ব্যাপন চাপ ঘাটতি সৃষ্টি হয়, যা পানি শোষণে সাহায্য করে। উদ্ভিদ প্রস্বেদনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পত্রফলক দিয়ে শোষিত তাপশক্তি হ্রাস করে পাতার কোষগুলোর তাপমাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখে।
অন্যদিকে,
– গুরুত্বপূর্ণ এই প্রস্বেদন প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের বহু ধরনের উপকার করলেও এর কিছু অপকারী ভূমিকাও রয়েছে।
যেমন: পানি শোষণের চেয়ে প্রস্বেদনে পানি হারানোর হার বেশি হলে উদ্ভিদের জন্য পানি এবং খনিজের ঘাটতি দেখা দিবে। এর ফলে উদ্ভিদটির মৃত্যু হতে পারে। মাটিতে পানির ঘাটতি থাকলে শোষণ কম হবে কিন্তু প্রস্বেদন পূর্বের মতো চলতে থাকবে। এ অবস্থাকে ঠেকাতে প্রকৃতি শীত মৌসুমে বহু উদ্ভিদের পাতা ঝরিয়ে দেয়। প্রস্বেদনের অভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাপন চাপ ঘাটতি হবে না, ফলে অভিস্রবণ কম হবে।
এমতাবস্থায় বলা যায়, প্রস্বেদন কিছু ক্ষতিসাধন করলেও এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি কার্যক্রম। বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের জন্য বিজ্ঞানী কার্টিস প্রস্বেদনকে ‘প্রয়োজনীয় ক্ষতি‘ (Necessary Evil) নামে অভিহিত করেছেন। তবে সার্বিক বিচারে এটি উদ্ভিদকে টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধা দেয় বলে অপকারী দিক থাকা সত্ত্বেও প্রস্বেদন প্রক্রিয়া বিবর্তিত হয়েছে।
উৎস: জীববিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি।
কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি
প্রশ্ন ১৪৬. একটি কম্পিউটারের প্রোসেসর ক্লক স্পিড ৪.০০ গিগা হার্জ হলে এর ক্লক মাইকেল টাইম কত?
ক) ২.৫ ন্যানো সেকেন্ড (ns) খ) ২.৫ মাইক্রো সেকেন্ড (ms)
গ) ৪ (ms) ঘ) ৪ (ns)
সঠিক উত্তর: ক) ২.৫ ন্যানো সেকেন্ড (ns)
Live MCQ Analytics: Right: 7%; Wrong: 7%; Unanswered: 85%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
(মূল প্রশ্নে কিছু বানান ভুল ছিল, মাইকেল ⇒ সাইকেল)।
প্রদত্ত ক্লক স্পিড:
f = 4.00 GHz = 4.00 × 109 Hz
ক্লক পিরিয়ড (Clock Cycle Time) = 1 / ফ্রিকোয়েন্সি
T = 1 / f = 1 / (4.00 × 109) seconds
হিসাব করি:
T = 0.25 × 10-9 s = 0.25 ns
লক্ষ্যযোগ্য বিষয়:
প্রকৃত ক্লক টাইম = 0.25 ns, প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি হলো ২.৫ ns। সম্ভবত প্রশ্নে টাইপো বা স্পিড 400 MHz ধরে নেওয়া হয়েছে।
ক্লক স্পিড (Clock Speed):
– ক্লক স্পিড হলো কম্পিউটারের প্রসেসর কত দ্রুত কাজ করতে পারে তার পরিমাপ।
– এটি সাধারণত GHz (Gigahertz) বা MHz (Megahertz) এককে প্রকাশ করা হয়।
– ক্লক স্পিড যত বেশি হবে, প্রসেসর তত দ্রুত নির্দেশনা (Instruction) সম্পাদন করতে পারবে।
– এটি নির্ধারণ করে প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো সাইকেল (Cycle) সম্পন্ন হচ্ছে।
– তবে শুধু ক্লক স্পিড বেশি হওয়াই কম্পিউটারকে দ্রুতগতির করে না, প্রসেসরের আর্কিটেকচার এবং কোর সংখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ক্লক মাইকেল টাইম (Clock Cycle Time):
– ক্লক সাইকেল টাইম হলো একটি ক্লক সাইকেল সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে।
– এটি সাধারণত ন্যানোসেকেন্ড (ns) এ পরিমাপ করা হয়।
– ক্লক সাইকেল টাইম এবং ক্লক স্পিড একে অপরের বিপরীত অনুপাতিক। অর্থাৎ, ক্লক স্পিড যত বেশি হবে, ক্লক সাইকেল টাইম তত কম হবে।
– উদাহরণস্বরূপ, যদি ক্লক স্পিড হয় 2 GHz, তবে ক্লক সাইকেল টাইম হবে প্রায় 0.5 ns।
– প্রসেসরের পারফরম্যান্স বুঝতে ক্লক স্পিড এবং ক্লক সাইকেল টাইম—দুটোই গুরুত্বপূর্ণ।
সূত্র: – Intel [link] – sciencedirect [link]
প্রশ্ন ১৪৭. Precision Agriculture এ সাধারণত নিচের কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?
ক) ইনফ্রা রেড ইমেজিং খ) আই.ও.টি (IoT), সেন্সর
গ) তার মাধ্যম সম্পন্ন নেটওয়ার্ক ঘ) ও.এল.ই.ডি (OLED) ডিসপ্লে
সঠিক উত্তর: খ) আই.ও.টি (IoT), সেন্সর
Live MCQ Analytics: Right: 27%; Wrong: 7%; Unanswered: 65%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
• Precision Agriculture হল এমন একটি আধুনিক কৃষি পদ্ধতি যা ফসলের উৎপাদন, জমির স্বাস্থ্য এবং কৃষি সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে ইনফ্রা রেড ইমেজিং, IoT ও সেন্সর এবং তার মাধ্যমে সম্পন্ন নেটওয়ার্ক মূল ভূমিকা রাখে। ইনফ্রা রেড ইমেজিং-এর মাধ্যমে ফসলের জল, পুষ্টি এবং রোগের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। IoT ডিভাইস এবং সেন্সর জমির আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ও অন্যান্য পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ করে। এই তথ্যগুলি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে রিয়েল-টাইম ডেটা প্রদান করে, যা কৃষককে দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে OLED ডিসপ্লে সরাসরি Precision Agriculture-এ ব্যবহৃত হয় না।
– তবে, সঠিক উত্তর হিসেবে – [আই.ও.টি (IoT), সেন্সর] নেয়া হয়েছে।
– মাঠে স্থাপিত সেন্সরগুলো মাটি, পানি, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, এবং পুষ্টি উপাদানের তথ্য সংগ্রহ করে। এই ডেটা রিয়েল-টাইমে কৃষকদের কাছে পৌঁছে এবং তারা সেই অনুযায়ী সেচ, সার প্রয়োগ বা অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে পারে। ফলে উৎপাদন বাড়ে, পরিবেশ দূষণ কমে এবং খরচ সাশ্রয় হয়। Precision Agriculture-এ শুধু সেন্সর নয়, IoT-এর মাধ্যমে এই ডেটা সংযুক্ত থাকে, যা স্বয়ংক্রিয় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
উত্তর: খ) IoT, সেন্সর।
• অপশন আলোচনা:
ক) ইনফ্রা রেড ইমেজিং: মাটি ও ফসলের স্বাস্থ্য ও আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত।
খ) আই.ও.টি (IoT), সেন্সর: মাটির আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, পুষ্টি পরিমাপের জন্য প্রধান প্রযুক্তি। (সঠিক উত্তর)।
গ) তার মাধ্যম সম্পন্ন নেটওয়ার্ক: সেন্সর ও ডিভাইসগুলোর ডেটা সংযোগ ও ট্রান্সমিশনের জন্য ব্যবহৃত।
ঘ) ও.এল.ই.ডি (OLED) ডিসপ্লে: মূলত ডিসপ্লে বা প্রদর্শনের জন্য, কৃষি প্রযুক্তিতে সরাসরি প্রয়োগ কম।
• ইন্টারনেট অফ থিংস (Internal of things – IoT):
– ইন্টারনেট অফ থিংস (IOT) হলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এমন একটি সনাক্তকারী কম্পিউটিং ডিভাইস, যা একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের বা মানুষের সাথে কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা স্থানান্তর করতে সাহায্য করে।
– এটি ইন্টারনেটের সাথে শারীরিক ডিভাইস এবং দৈনন্দিন বস্তুকে সংযুক্ত করার ধারণাকে বোঝায়, তাদের ডেটা সংগ্রহ এবং বিনিময় করার অনুমতি দেয়।
– এই সংযুক্ত ডিভাইসগুলি স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট এবং রেফ্রিজারেটরের মতো গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে শিল্প মেশিন, পরিধানযোগ্য এবং যানবাহন পর্যন্ত হতে পারে।
– IoT-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল এই ডিভাইসগুলিকে একে অপরের সাথে এবং কেন্দ্রীভূত সিস্টেম বা ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম করা।
• IoT এর উদাহরণ:
– স্মার্ট হোম ডিভাইস (যেমন স্মার্ট লাইট, স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট)।
– ওয়্যারেবল ডিভাইস (যেমন ফিটনেস ট্র্যাকার)।
– শিল্পক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি (Industrial IoT)।
উৎস: – UNDP [link] – digi [link] – Britannica [link]
প্রশ্ন ১৪৮. অপারেটিং সিস্টেমে ভার্চুয়াল মেমোরি ব্যবহার করা হয়-
ক) অনেক বেশি ডেটা সংরক্ষণের জন্য
খ) ক্লাউডে ডেটা সংরক্ষণের জন্য
গ) সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবহার করে RAM বাড়াতে
ঘ) এক্সটারনাল মেমোরি সংযোগের জন্য
সঠিক উত্তর: গ) সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবহার করে RAM বাড়াতে
Live MCQ Analytics: Right: 35%; Wrong: 26%; Unanswered: 38%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
• অপারেটিং সিস্টেমে ভার্চুয়াল মেমোরি ব্যবহার করা হয় মূলত সেকেন্ডারি স্টোরেজকে RAM হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। কম্পিউটার মেশিনের ফিজিক্যাল RAM সীমিত থাকে, কিন্তু অনেক বড় প্রোগ্রাম চালানোর সময় তা যথেষ্ট নাও হতে পারে। ভার্চুয়াল মেমোরি প্রযুক্তি ডিস্কের জায়গা ব্যবহার করে RAM-এর উপর লোড থাকা ডেটা বা প্রোগ্রামের অংশ সাময়িকভাবে রাখে, ফলে ব্যবহারকারীর কাছে মনে হয় RAM অনেক বেশি আছে। এটি মেমোরি ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে, মাল্টি-প্রোগ্রামিং সমর্থন দেয় এবং সিস্টেমের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সংক্ষেপে, ভার্চুয়াল মেমোরি RAM-এর সীমাবদ্ধতা দূর করে সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবহার করে মেমোরি বৃদ্ধি করে।
সঠিক উত্তর: গ) সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবহার করে RAM বাড়াতে।
• ভার্চুয়াল মেমোরি (Virtual Memory):
– ভার্চুয়াল মেমোরি হলো অপারেটিং সিস্টেমের একটি প্রযুক্তি যা RAM এবং সেকেন্ডারি স্টোরেজ (যেমন হার্ড ডিস্ক) একত্রে ব্যবহার করে।
– এটি প্রোগ্রামকে তার বাস্তব RAM এর চেয়ে বেশি মেমোরি ব্যবহার করতে সক্ষম করে।
– ভার্চুয়াল মেমোরি সিস্টেম RAM পূর্ণ হলে, অপ্রয়োজনীয় ডেটা বা প্রোগ্রাম অংশকে সেকেন্ডারি স্টোরেজে স্থানান্তরিত করে।
– অপারেটিং সিস্টেম এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে, ফলে ব্যবহারকারী বা প্রোগ্রামারকে মেমোরি সীমা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।
– মূল উদ্দেশ্য: সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবহার করে RAM বাড়ানো।
সূত্র:
– geeksforgeeks [link]
– Computer Science | University of Illinois Chicago [link]
প্রশ্ন ১৪৯. কম্পিউটার সিস্টেমের বেঞ্চমার্কিং করা হয় কী পরিমাপের জন্য?
ক) সিস্টেমের দাম
খ) সিস্টেমের কর্ম ক্ষমতা (Performance)
গ) শুধু বিদ্যুৎ শক্তি খরচের পরিমাণ
ঘ) স্টোরেজের ধারণ ক্ষমতা
সঠিক উত্তর: খ) সিস্টেমের কর্ম ক্ষমতা (Performance)
Live MCQ Analytics: Right: 41%; Wrong: 3%; Unanswered: 55%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
• কম্পিউটার সিস্টেমের বেঞ্চমার্কিং মূলত সিস্টেমের কর্মক্ষমতা (Performance) পরিমাপের জন্য করা হয়। বেঞ্চমার্ক হল একটি মানক পরীক্ষা বা সফটওয়্যার যা কম্পিউটারের প্রসেসর, মেমরি, গ্রাফিক্স, স্টোরেজ এবং অন্যান্য উপাদানের কার্যকারিতা যাচাই করে। এটি ব্যবহারকারীদের এবং নির্মাতাদের সিস্টেমের তুলনামূলক দক্ষতা বোঝার সুযোগ দেয়। বেঞ্চমার্কিংয়ের মাধ্যমে বোঝা যায়, একটি কম্পিউটার নির্দিষ্ট কাজ কত দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে এবং বিভিন্ন সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য শনাক্ত করা যায়। তাই বেঞ্চমার্কিং সরাসরি দাম, বিদ্যুৎ শক্তি খরচ বা স্টোরেজ ক্ষমতা নয়, বরং কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
সঠিক উত্তর: খ) সিস্টেমের কর্ম ক্ষমতা (Performance)।
• কম্পিউটারের কর্মক্ষমতা:
– কম্পিউটারের কর্মক্ষমতা বলতে বোঝায়, কম্পিউটার কত দ্রুত কাজ করতে পারে। এটিকে বিভিন্নভাবে পরিমাপ করা যায়, যেমন প্রসেসিং স্পিড, মেমোরি স্পিড, হার্ডডিস্কের গতি ইত্যাদি।
• Benchmark সফটওয়্যার হল এমন একটি বিশেষ ধরণের প্রোগ্রাম যা কম্পিউটারের বিভিন্ন হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের দক্ষতা (performance) যাচাই করতে সাহায্য করে।
– এটি CPU, GPU, RAM, ডিস্ক স্পিড ইত্যাদির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে।
– ফলাফল হিসেবে একটি স্কোর বা তুলনামূলক রিপোর্ট দেয় — যা অন্য কম্পিউটারের সাথে তুলনা করা যায়।
• কিছু জনপ্রিয় Benchmark সফটওয়্যারের নাম:
– Cinebench, Geekbench, 3DMark, PassMark.
তথ্যসূত্র:
– “Computer Fundamentals” by P.K. Sinha.
– এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা।
প্রশ্ন ১৫০. নিচের কোন ডিভাইসটি প্রধানত এম্বেডেড সিস্টেম ব্যবহৃত হয়?
ক) রাউটার খ) সুপার কম্পিউটার
গ) হাই-অ্যান্ড সার্ভার ঘ) মাইক্রোকন্ট্রোলার
সঠিক উত্তর: ঘ) মাইক্রোকন্ট্রোলার
Live MCQ Analytics: Right: 36%; Wrong: 25%; Unanswered: 37%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
• প্রধানত এম্বেডেড সিস্টেম ব্যবহৃত হয় মাইক্রোকন্ট্রোলার-এ। এম্বেডেড সিস্টেম হলো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পন্ন কম্পিউটার সিস্টেম, যা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য ডিজাইন করা হয়। মাইক্রোকন্ট্রোলার সাধারণত ছোট আকারের এবং একক চিপে প্রসেসর, মেমোরি ও ইনপুট/আউটপুট পেরিফেরাল থাকে। এটি ঘড়ি, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন, সিকিউরিটি ডিভাইস এবং অন্যান্য ছোট ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, রাউটার, সুপার কম্পিউটার বা হাই-এন্ড সার্ভার সাধারণত জেনেরাল-পারপাস কম্পিউটিং বা নেটওয়ার্কিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এগুলো এম্বেডেড সিস্টেম হিসেবে বিবেচিত হয় না। তাই এম্বেডেড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মাইক্রোকন্ট্রোলারই সঠিক উত্তর।
• এমবেডেড কম্পিউটার:
এমবেডেড কম্পিউটার হলো একটি বিশেষায়িত কম্পিউটার সিস্টেম যা বৃহৎ সিস্টেম বা মেশিনের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত একটি মাইক্রোপ্রসেসর বোর্ড এবং নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম সম্বলিত রম (ROM) নিয়ে গঠিত। আধুনিক এমবেডেড সিস্টেমে মাইক্রোকন্ট্রোলারের ব্যবহার করা হয়।
• এমবেডেড কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ:
– গাড়ি, সেলফোন ও স্মার্টফোন, প্রিন্টার, মাইক্রোওয়েভ, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার কন্ডিশন(এসি), ঘড়ি, থার্মোস্ট্যাট, ভিডিও গেমস্, ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং, ATM, সিকিউরিটি ক্যামেরা ইত্যাদি।
উৎস: ১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ২. Auburn University Samuel Ginn College of Engineering [link]
প্রশ্ন ১৫১. ই-কমার্সে সুরক্ষিত অনলাইন লেনদেনে প্রধানত কোন প্রটোকল ব্যবহৃত হয়?
ক) DHCP খ) SMTP
গ) HTTPS ঘ) ARP
সঠিক উত্তর: গ) HTTPS
Live MCQ Analytics: Right: 42%; Wrong: 19%; Unanswered: 38%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) মূলত ডেটা এনক্রিপশন নিশ্চিত করে, যা ব্যবহারকারী এবং ওয়েবসাইটের মধ্যে আদান-প্রদানকৃত তথ্য (যেমন—লগইন ক্রেডেনশিয়াল, ব্যক্তিগত ডেটা, পেমেন্ট তথ্য) নিরাপদে রাখে।
– ই-কমার্সে যখন গ্রাহক অনলাইনে টাকা পরিশোধ করেন বা ব্যক্তিগত তথ্য (পাসওয়ার্ড, কার্ড নম্বর ইত্যাদি) দেন, তখন সেই ডেটাকে সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য ব্যবহৃত হয় HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure).
HTTPS:
– https এর পূর্ণরূপ হচ্ছে- Hypertext Transfer Protocol Secure.
– HTTPS হলো একটি প্রোটোকল যা ব্যবহারকারীর ওয়েব ব্রাউজার এবং একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে যোগাযোগ এবং ডেটা স্থানান্তর সুরক্ষিত করে।
– কোন ওয়েবসাইটের ঠিকানায় ব্যবহৃত https এর ‘S’ দিয়ে Secured (সুরক্ষিত) বোঝায়।
– HTTPS Protocol-টি ইন্টারনেটে তথ্য আদান-প্রদানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে।
– https, http-এর চেয়ে অধিকতর নিরাপদ।
– সাধারণত প্রায় সব ওয়েব অ্যাড্রেসই শুরু হয় http:// দিয়ে।
– তাই ওয়েব অ্যাড্রেসে এ অংশটি লিখা হয় না। www অংশ দিয়েই শুরু করা হয়।
অন্যান্য অপশনসমূহ,
DHCP: IP address assignment এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
SMTP: ইমেইল পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
ARP: IP থেকে MAC address mapping এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
উৎস: ১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, মাহবুবুর রহমান। ২। Bigcommerce Essentials ওয়েবসাইট। [লিংক]
প্রশ্ন ১৫২. বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নিচের কোন ডিভাইসটি ব্যবহৃত হয়?
ক) রাউটার খ) সুইচ
গ) ব্রিজ ঘ) হাব
সঠিক উত্তর: ক) রাউটার
Live MCQ Analytics: Right: 32%; Wrong: 42%; Unanswered: 25%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাউটার ব্যবহার করা হয়। রাউটার হলো একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা একাধিক নেটওয়ার্কের মধ্যে ডেটা প্যাকেটের গতি এবং পথ নির্ধারণ করে। এটি মূলত আইপি ঠিকানার ভিত্তিতে ডেটা ট্রান্সমিশন করে, ফলে ভিন্ন নেটওয়ার্কে সংযুক্ত ডিভাইসগুলো একে অপরের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। অন্যদিকে, সুইচ শুধুমাত্র একই নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডেটা স্থানান্তর করে, ব্রিজ দুটি নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে কিন্তু সীমিত পরিসরে, আর হাব ডেটা শুধু পুনরায় সম্প্রচার করে, কোনো গন্তব্য ঠিক করে না। তাই ভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগের জন্য রাউটার অপরিহার্য।
• সুইচ:
– সুইচ একটি ডিভাইস যা নেটওয়ার্কের ডাটাকে বিভক্ত করে নেটওয়ার্কের সকল সিস্টেমে না পাঠিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পাঠিয়ে দেয়।
– হাব এবং সুইচ এর কাজ প্রায় একই। তবে হাব প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর একই সাথে প্রত্যেকটি কম্পিউটারে পাঠায় কিন্তু সুইচ প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর টার্গেট কম্পিউটারে পাঠায়।
– স্টার টপোলজিতে সুইচ একটি কেন্দ্রিয় কানেকটিভ ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
• রাউটার:
– রাউটার ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ করা হয়।
– ছোট ছোট নেটওয়ার্ক রাউটারের মাধ্যমে সংযুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়।
– রাউটার নেটওয়ার্কের মধ্যে একাধিক পথ সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক যেমন ইথারনেট, টোকেন, রিং কে সংযুক্ত করতে পারে।
– রাউটার একই প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।
• হাব:
– হাবের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে।
– হাবের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কম্পিউটারের সংযোগের সংখ্যা।
– স্টার টপোলজিতে হাব একটি কেন্দ্রিয় ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
– হাবে মাল্টিপল পোর্ট থাকে।
– যখন একটি প্যাকেট কোন একটি পোর্টে পৌঁছায়, এটি সেই প্যাকেটকে কপি করে হাবের সকল পোর্টে পাঠায়।
• কার্যকারিতার দিক থেকে হাব দুই প্রকার। যথা-
১. সক্রিয় হাব (Active HUB ):
– এ ধরণের হাব সংকেতের মানকে বৃদ্ধি করে।
– আবার কোন কোন সক্রিয় হাব সংকেতকে অল্প মাত্রায় প্রসেসও করে থাকে।
– এই সকল হাব মূল সংকেত থেকে অপ্রয়োজনীয় সংকেত বাদ দিয়ে
প্রয়োজনীয় সংকেত প্রেরণ করে ।
২. নিষ্ক্রিয় হাব (Passive HUB):
– এ ধরণের হাব সংকেতের মানকে বৃদ্ধি করে ।
– এ সকল হাব শুধু তথ্য আদান প্রদানে সহায়তা করে মাত্র।
– এজন্য এই সকল হাবকে কোন সক্রিয় হাবের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়।
• ব্রিজ (Bridge):
– এক ধরনের নেটওয়ার্ক ডিভাইস, যা একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে থাকে।
– এর সাহায্যে ভিন্ন মাধ্যম অথবা ভিন্ন কাঠামো বিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা যায়।
– তবে এর সাহায্যে ভিন্ন প্রটোকল বিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা যায় না।
– ব্রিজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
১. লোকাল ব্রিজ (Local Bridge):
– এটি সরাসরি LAN এর সাথে যুক্ত থাকে।
২. রিমোট ব্রিজ (Remote Bridge):
– ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দু’টি অবস্থানের দু’টি ল্যান সেগমেন্টকে সংযুক্ত করে।
৩. ওয়্যারলেস ব্রিজ (Wireless Bridge):
– একাধিক LAN যুক্ত করা অথবা LAN এর দূরবর্তী স্টেশনকে সংযুক্ত করার জন্য ওয়ারলেস ব্রিজ ব্যবহৃত হতে পারে।
এছাড়াও,
• গেটওয়ে:
– গেটওয়ে ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ করা হয়।
– গেটওয়ে এবং রাউটার ব্যবহার করে ছোট ছোট নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়।
– রাউটার একই প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে কিন্তু গেটওয়ে বিভিন্ন প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।
উৎস: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ১৫৩. ক্লাউড কম্পিউটিং এর কোন মডেলটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য প্রোগ্রামারদেরকে প্লাটফর্ম সরবরাহ করে?
ক) laaS খ) SaaS
গ) PaaS ঘ) DaaS
সঠিক উত্তর: গ) PaaS
Live MCQ Analytics: Right: 38%; Wrong: 24%; Unanswered: 36%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে বিভিন্ন মডেল রয়েছে, যেগুলো আলাদা ধরণের সেবা প্রদান করে। এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, কোন মডেলটি প্রোগ্রামারদের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে। এর মধ্যে PaaS (Platform as a Service) সেই মডেল যা ডেভেলপারদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। PaaS ব্যবহার করে প্রোগ্রামাররা সার্ভার, স্টোরেজ, নেটওয়ার্ক বা হোস্টিং নিয়ে চিন্তা না করে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, পরীক্ষা ও ডিপ্লয় করতে পারে। এটি কোডিং, ডাটাবেস, API, ডেভেলপমেন্ট টুলস এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম ফিচার সরবরাহ করে, যা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে। অন্যদিকে IaaS কেবল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেয়, SaaS সরাসরি ব্যবহারযোগ্য সফটওয়্যার দেয়, এবং DaaS ডেস্কটপ ভার্চুয়ালাইজেশন সেবা। সুতরাং প্রোগ্রামারদের জন্য যথাযথ মডেল হলো PaaS.
• অপশন আলোচনা:
– IaaS (Infrastructure as a Service) – সার্ভার, স্টোরেজ ও নেটওয়ার্কের ইনফ্রাস্ট্রাকচার সরবরাহ করে, অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার সরাসরি প্ল্যাটফর্ম নয়।
– SaaS (Software as a Service) – সম্পূর্ণ তৈরি সফটওয়্যার ব্যবহার করার সুবিধা দেয়, প্রোগ্রামার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে না।
– PaaS (Platform as a Service) – প্রোগ্রামারদের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, ডেপ্লয় ও পরিচালনার জন্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।
– DaaS (Desktop as a Service) – ভার্চুয়াল ডেস্কটপ পরিবেশ সরবরাহ করে, অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য নয়।
– সঠিক উত্তর: গ) PaaS.
• ক্লাউড কম্পিউটিং:
– ক্লাউড কম্পিউটিং হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে দূরবর্তী সার্ভার থেকে ডাটা, সফটওয়্যার এবং বিভিন্ন কম্পিউটিং রিসোর্স ব্যবহার করার প্রযুক্তি।
– ক্লাউড কম্পিউটিং এর মূল বিষয়টি হলো নিজের ব্যবহৃত কম্পিউটারের হার্ডড্রাইভের পরিবর্তে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সার্ভিস বা হার্ডওয়্যার ভাড়া নেওয়া।
• ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভিসদাতা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রদান করে থাকে। এ সব সার্ভিস মডেলকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
১। অবকাঠামোগত সেবা (IaaS: Infrastructure as a service):
– এই মডেলে অবকাঠামো ভাড়া দেওয়া হয়। অ্যামাজন-এর ইলাস্টিক কম্পিউটিং ক্লাউড (EC2) এরকম একটি মডেল। EC2-এর প্রতিটি সার্ভারে 1 থেকে 4 টি ভার্চুয়াল মেশিনে চলে, ক্রেতারা এগুলোই ভাড়া নিয়ে থাকেন। ব্যবহারকারীরা ভার্চুয়াল মেশিনে নিজেদের ইচ্ছেমতো অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে নিজের নিয়ন্ত্রণে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার চালাতে
পারেন।
২। প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা (PaaS: Platform as a service):
– এই মডেলে ভার্চুয়াল মেশিন ভাড়া না দিয়ে ভাড়া দেওয়া হয় কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অপারেটিং সিস্টেম, প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এক্সিকিউশন পরিবেশ, ডেটাবেজ এবং ওয়েব সার্ভার ইত্যাদি। এই প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারী স্বল্প ব্যয়ে তার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার উন্নয়ন করতে পারেন। Google -এর App Engine এই মডেলের উদাহরণ।
৩। সফটওয়্যারভিত্তিক সেবা (SaaS: Software as a service):
– এই মডেলে ব্যবহারকারীরা সার্ভিসদাতা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা সফটওয়্যার ও ডেটাবেজে অ্যাকসেস এবং ব্যবহারে সুযোগ পায়। এর ফলে ব্যবহারকারীকে সিপিইউ বা স্টোরেজের অবস্থান, কনফিগারেশন ইত্যাদি জানা বা রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না।
উৎস: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-দ্বাদশ (আলিম শ্রেণি)।
প্রশ্ন ১৫৪. একটি কম্পিউটার সিস্টেমে (১১০০১০১১)২ বাইনারি সংখ্যাটির মান ডেসিমেল এ কত হবে?
ক) – ৫২ খ) – ৫৩
গ) ২০৩ ঘ) উপরের সবকটি হতে পারে
সঠিক উত্তর: ঘ) উপরের সবকটি হতে পারে
Live MCQ Analytics: Right: 1%; Wrong: 98%; Unanswered: 0%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
প্রশ্ন: একটি কম্পিউটার সিস্টেমে (11001011)2 বাইনারি সংখ্যাটির মান ডেসিমেল এ কত হবে?
• একটি কম্পিউটার সিস্টেমে ৮-বিট বাইনারি সংখ্যা (11001011)2 এর মান নির্ভর করে আমরা কীভাবে তা ইন্টারপ্রেট করি তার ওপর। যদি এটি Unsigned সংখ্যা হিসেবে ধরা হয়, তাহলে সব বিটই ধনাত্মক অবদান রাখে এবং দশমিক মান হবে 128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 = 203, অর্থাৎ অপশন (গ)।
– তবে, যদি আমরা এটিকে Signed Two’s Complement হিসেবে ধরি, তাহলে প্রথম বিট (MSB) = 1 হওয়ায় সংখ্যা ঋণাত্মক। Two’s complement বের করতে প্রথমে বিটগুলো উল্টে 00110100 পাই এবং ১ যোগ করলে 00110101 হয়, যার দশমিক মান = 53, সুতরাং Signed হিসেবে মান = – 53, অর্থাৎ অপশন (খ)।
– অন্যদিকে, One’s Complement অনুযায়ী, MSB = 1 → ঋণাত্মক, এবং বিটগুলো উল্টে 00110100 পাওয়া যায়, যার দশমিক মান = 52, অর্থাৎ মান = – 52, অর্থাৎ অপশন (ক)।
– তাই প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গে, একই বাইনারি সংখ্যা Unsigned, Signed Two’s Complement, বা One’s Complement হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন মান দিতে পারে, এবং প্রদত্ত অপশন অনুযায়ী সবকটি মান সম্ভব।
– একই ৮-বিট সংখ্যা (11001011)2 এর জন্য Unsigned = 203, Two’s Complement Signed = -53, One’s Complement Signed = – 52
[উল্লেখ্য, PSC অপশন (ঘ) তে সচরারচর – “উপরের সবকটি” দিয়ে থাকে, কিন্তু ৪৭ তম বিসিএসে এবার অপশন (ঘ) – “উপরের সবকটি হতে পারে” দিয়েছে। সব ছোট বিষয়ও খেয়াল রেখে উত্তর করতে হবে।]
• বিস্তারিত সমাধান:
১. যদি Unsigned সংখ্যা হিসেবে ধরা হয়:
(11001011)2 = (1 × 27) + (1 × 26) + (0 × 25) + (0 × 24) + (1 × 23) + (0 × 22) + (1 × 21) + (1 × 20)
= 128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 = 203
অতএব, Unsigned হলে মান = 203
২. যদি Signed (Two’s Complement, 8-bit) সংখ্যা হিসেবে ধরা হয়:
– প্রথম বিট = 1 → সংখ্যা নেগেটিভ।
– Two’s complement বের করতে: প্রথমে বিট ইনভার্ট → 00110100
– তারপর 1 যোগ করলে → 00110101 = 53
অতএব, Signed হলে মান = – 53
– Unsigned interpretation: 203
– Signed interpretation: – 53
(৩) One’s Complement নিয়ম (8-bit):
MSB = 1 → সংখ্যা ঋণাত্মক।
Magnitude = Bitwise complement (বিটের উল্টো)
⇒ 8-bit সংখ্যা 110010112
⇒ MSB = 1 → সংখ্যা ঋণাত্মক।
⇒ Bitwise complement:
11001011 → 001101002
⇒ 001101002 এর দশমিক মান = 52
⇒ অতএব, One’s Complement অনুযায়ী এই সংখ্যার মান = -52 (অপশন ক)
উল্লেখ্য,
– MSB এর পূর্ণরূপ হলো: Most Significant Bit.
– এটি একটি বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিট।
– সাধারণত, MSB সংখ্যা নির্ধারণ করে যে সংখ্যা ধনাত্মক না ঋণাত্মক (Signed Binary Number) বা বাইনারি সংখ্যার সর্বোচ্চ মানের অংশ।
(11001011)2
এখানে, প্রথম 1 = MSB
Signed 8-bit Two’s Complement এ MSB = 1 → সংখ্যা ঋণাত্মক
MSB = 0 → সংখ্যা ধনাত্মক।
সূত্র:
– “Digital Design” by M. Morris Mano.
– “Digital Electronics: Principles and Applications” by Roger L. Tokheim.
– rapidtables [link]
প্রশ্ন ১৫৫. কোন CPU আর্কিটেকচার স্মার্টফোনে বেশি ব্যবহৃত হয়?
ক) X86 খ) X64
গ) Qualcomm ঘ) RISC
সঠিক উত্তর: ঘ) RISC
Live MCQ Analytics: Right: 8%; Wrong: 26%; Unanswered: 64%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
◉ স্মার্টফোনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত CPU আর্কিটেকচার হলো RISC. বিশেষ করে ARM আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে তৈরি RISC (Reduced Instruction Set Computing) প্রসেসর স্মার্টফোনে ব্যবহার হয়। RISC আর্কিটেকচার কম সংখ্যক, সহজ নির্দেশনা ব্যবহার করে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে, যা ব্যাটারি খরচ কমাতে সহায়ক। এর ফলে মোবাইল ডিভাইসে উচ্চ পারফরম্যান্স এবং শক্তি সাশ্রয়ী কার্যক্ষমতা পাওয়া যায়। অন্যদিকে X86 বা X64 সাধারণত ডেস্কটপ ও ল্যাপটপে ব্যবহৃত হয়। Qualcomm একটি কোম্পানি যা ARM ভিত্তিক চিপset তৈরি করে, তাই এটি একটি আর্কিটেকচার নয়। তাই মোবাইলে প্রধানত RISC/ARM আর্কিটেকচার ব্যবহৃত হয়।
• RISC (Reduced Instruction Set Computer):
– RISC হলো এমন এক মাইক্রোপ্রসেসর আর্কিটেকচার যা simplicity এবং গতির ওপর জোর দেয়। এর মূল ধারণা হলো, কম এবং সরল ইনস্ট্রাকশন সেট ব্যবহার করে প্রোগ্রামের কার্যসম্পাদনকে দ্রুততর করা।
– RISC প্রসেসরগুলো দ্রুত এবং দক্ষ, কারণ এগুলো কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশনকে ছোট ছোট সহজ ইনস্ট্রাকশনে ভেঙে কার্যকর করে।
– আধুনিক মোবাইল প্রসেসরগুলো (যেমন ARM architecture) মূলত RISC ভিত্তিক।
– RISC আর্কিটেকচার কম শক্তি খরচ করে, দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে পারে এবং ব্যাটারি-চালিত ডিভাইসের (যেমন স্মার্টফোন, ট্যাবলেট) জন্য আদর্শ।
অন্যদিকে,
X86/X64: Intel/AMD এর আর্কিটেকচার, ডেস্কটপ/ল্যাপটপে ব্যবহৃত, বেশি পাওয়ার খরচ করে।
Qualcomm: এটি মূলত কোম্পানির নাম, আর্কিটেকচারের নাম নয় (Qualcomm RISC ভিত্তিক ARM প্রসেসর বানায়)।
উৎস: 1. Arm.com Website. [Link]
2. Encyclopedia Britannica. [Link]
প্রশ্ন ১৫৬. কম্পিউটার টার্ন অন এর সময় সঠিক অর্ডার নিচের কোনটি?
ক) POST → Kernel → Bootloader
খ) Kernel → POST → Bootloader
গ) Kernel → Bootloader → POST
ঘ) POST → Bootloader → Kernel
সঠিক উত্তর: ঘ) POST → Bootloader → Kernel
Live MCQ Analytics: Right: 19%; Wrong: 15%; Unanswered: 65%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
◉ Booting প্রক্রিয়ায় ধাপগুলো হলো: Power On → POST (হার্ডওয়্যার চেক) → Bootloader Execution → OS Loading → User Interface Ready.
– অর্থাৎ কম্পিউটার চালু হলে BIOS/UEFI POST করে, Bootloader Kernel লোড করে এবং শেষে ইউজার ইন্টারফেস প্রস্তুত হয়।
• বুটিং (Booting):
– একটি কম্পিউটারকে চালু করা হলে তা সিপিইউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট প্রথমেই যাচাই করে নেয় যে কী-বোর্ড, মাউস, মনিটর ইত্যাদি যন্ত্রাংশ এর সঙ্গে সঠিকভাবে যুক্ত আছে কিনা। এই যাচাই করার প্রক্রিয়াকে বলে পোস্ট Power on self test (POST)।
– যদি এই যন্ত্রাংশগুলো সঠিক ভাবে যুক্ত থাকে, তা হলে সিপিইউ কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমকে হার্ডডিস্ক থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে র্যামের মধ্যে তুলে নেয় এবং কম্পিউটারকে ব্যবহারকরীর নির্দেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় বুটিং (Booting)।
– অর্থাৎ বুটিং একটি স্বয়ক্রিয় প্রক্রিয়া, যা সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই কম্পিউটারকে ব্যবহার করা হয়।
• Booting-এর ধাপগুলো:
1) Power On → ককম্পিউটার চালু করলে মাদারবোর্ডের ফার্মওয়্যার (BIOS/UEFI) সক্রিয় হয়।
2) POST (Power-On Self Test) → হার্ডওয়্যার ঠিকমতো কাজ করছে কিনা চেক করা হয়। BIOS/UEFI হার্ডওয়্যার চেক করে (RAM, CPU, Keyboard, Monitor, Storage)।
3) Boot Loader Execution → অপারেটিং সিস্টেমের boot manager (যেমন Windows Boot Manager বা GRUB) চালু হয়।
4) OS Loading → Bootloader নির্বাচিত Kernel মেমরিতে লোড করে। Kernel hardware initialize করে এবং প্রয়োজনীয় ড্রাইভার, সার্ভিস লোড করে। এরপর অপারেটিং সিস্টেম পূর্ণভাবে চালু হয়।
5) User Interface Ready → ইউজার login করতে পারে এবং সিস্টেম ব্যবহার করতে পারে।
উৎস: ১। মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা, বিবিএ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ২। Lenovo Website. ৩। geeksforgeeks [link]
প্রশ্ন ১৫৭. কোন ধরনের Storage Device সবচেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন?
ক) HDD খ) Floppy Disk
গ) SSD ঘ) SSHD
সঠিক উত্তর: গ) SSD
Live MCQ Analytics: Right: 45%; Wrong: 21%; Unanswered: 33%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:• সবচেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন স্টোরেজ ডিভাইস হলো SSD (Solid State Drive)। SSD-তে কোনো চলমান পার্ট নেই, বরং এটি NAND ফ্ল্যাশ মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণ করে, যা ডেটা অ্যাক্সেসের সময়কে অনেক দ্রুত করে তোলে। তুলনায়, HDD (Hard Disk Drive) এবং SSHD (Solid State Hybrid Drive) এ মেকানিক্যাল অংশ থাকে, যেমন ঘূর্ণনশীল ডিস্ক এবং রিড/রাইট হেড, যা তথ্য পড়া ও লেখা ধীর করে। Floppy Disk সবচেয়ে ধীর, কারণ এটি খুব পুরনো এবং সীমিত ডেটা স্থান ধারণ করতে পারে। SSD দ্রুত বুটিং, ফাইল ট্রান্সফার এবং অ্যাপ্লিকেশন লোডিং-এর জন্য আদর্শ, তাই আধুনিক কম্পিউটার ও ল্যাপটপে SSD ব্যবহারের প্রবণতা বেশি।
• অপশন আলোচনা:
– HDD: মেকানিক্যাল ঘূর্ণন ভিত্তিক, তুলনামূলক ধীর।
– Floppy Disk: খুব ধীর, প্রায় পুরনো প্রযুক্তি।
– SSD: ফ্ল্যাশ মেমোরি ভিত্তিক, অত্যন্ত দ্রুত।
– SSHD: হাইব্রিড, HDD-এর চেয়ে দ্রুত কিন্তু SSD-এর তুলনায় ধীর।
– সবচেয়ে দ্রুত: SSD.
• SSD:
– SSD এর পূর্ণরূপ Solid State Drive.
– সলিড-স্টেট ড্রাইভ (SSD) কম্পিউটারে ব্যবহৃত স্টোরেজ ডিভাইসের একটি নতুন প্রজন্ম।
– SSD ফ্ল্যাশ-ভিত্তিক মেমোরি ব্যবহার করে ডেটা সংরক্ষণ করে, যা Traditional Hard Disk এর তুলনায় অনেক দ্রুত।
– SSD ব্যবহারের ফলে কম্পিউটার পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গতি আসে।
• সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস:
– কম্পিউটারে বিপুল পরিমাণে তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হার্ডওয়্যারসমূহকে বলা হয় সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস।
– হার্ডডিস্ক, এসএসডি, সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ, জিপ ড্রাইভ, ম্যাগনেটিক টেপ ইত্যাদি সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসের উদাহরণ।
উৎস: Avast website এবং মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা, বিবিএ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ১৫৮. ধরা যাক Algorithm A এর running time O(n2) এবং Algorithm B এর running time O(n)। তাহলে নিচের কোনটি সবচেয়ে সঠিক?
ক) Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে ধীর গতির
খ) Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে দ্রুত গতির
গ) Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে asymptotically ধীর গতির
ঘ) Algorithm B সর্বদা Algorithm A এর চেয়ে দ্রুত চলে
সঠিক উত্তর: গ) Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে asymptotically ধীর গতির
Live MCQ Analytics: Right: 7%; Wrong: 18%; Unanswered: 74%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: • Algorithm A এর running time হলো O(n2) এবং Algorithm B এর running time হলো O(n)। Asymptotic analysis অনুযায়ী n বড় হলে O(n2) এর মান দ্রুত বৃদ্ধি পায়, আর O(n) তুলনামূলক ধীরে বৃদ্ধি পায়। তাই ছোট ইনপুটের ক্ষেত্রে কখনও Algorithm A দ্রুত হতে পারে, কিন্তু ইনপুট সাইজ যত বড় হবে, Algorithm A তত বেশি সময় নেবে। এজন্য বলা যায় Algorithm A asymptotically Algorithm B এর চেয়ে ধীর গতির। সঠিক উত্তর হবে গ), কারণ এটি দীর্ঘমেয়াদী (asymptotic) আচরণকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে, অন্য অপশন গুলো সম্পূর্ণভাবে সঠিক নয়।
• অ্যালগরিদম (Algorithm A এবং B):
– Algorithm A এর running time হলো O(n2)।
– Algorithm B এর running time হলো O(n)।
– এখানে O(n2) মানে ইনপুট সাইজ বাড়ার সাথে সাথে Algorithm A এর সময় অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
– অন্যদিকে O(n) মানে ইনপুট সাইজ বাড়লেও Algorithm B এর সময় ধীরে বৃদ্ধি পায়।
– তাই বড় ইনপুট সাইজের ক্ষেত্রে Algorithm A, Algorithm B এর তুলনায় অনেক ধীর হবে।
– তবে ছোট ইনপুট সাইজের ক্ষেত্রে কখনও কখনও Algorithm A দ্রুত হতে পারে, কারণ constant factor বা lower order terms এর প্রভাব থাকতে পারে।
– Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে asymptotically ধীর গতির।
– সঠিক উত্তর: গ) Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে asymptotically ধীর গতির।
সূত্র:
– Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein – Introduction to Algorithms (CLRS).
– MIT OpenCourseWare – Introduction To Algorithms [link]
– Stanford CS 161 – Design and Analysis of Algorithms [link]
প্রশ্ন ১৫৯. LLM চালানোর জন্য নিম্নোক্ত কম্পিউটারের কোন যন্ত্রাংশ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?
ক) RAM খ) Processor
গ) Graphics Card ঘ) Storage Device
সঠিক উত্তর: গ) Graphics Card
Live MCQ Analytics: Right: 9%; Wrong: 10%; Unanswered: 79%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:• LLM বা Large Language Model চালানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ হলো Graphics Card (GPU)। কারণ LLM-এর প্রশিক্ষণ ও ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই বিপুল পরিমাণ ম্যাট্রিক্স গণনা ও প্যারালাল প্রসেসিং প্রয়োজন হয়, যা সাধারণ Processor (CPU) দিয়ে ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়। শক্তিশালী GPU একসঙ্গে লক্ষাধিক অপারেশন দ্রুত সম্পাদন করতে সক্ষম, ফলে মডেল কার্যকরভাবে চালানো যায়। RAM, Storage Device এবং Processor অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা রাখে, তবে মূলত GPU-এর ক্ষমতাই নির্ধারণ করে মডেল কতটা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে। তাই LLM চালানোর ক্ষেত্রে Graphics Card-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
• LLM চালানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ:
– LLM (Large Language Model) চালানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল Graphics Card (GPU).
• Graphics Card (GPU):
– GPU বিশাল পরিমাণ ডেটা সমান্তরালভাবে প্রসেস করতে পারে।
– LLM মডেলগুলোর প্রশিক্ষণ ও কার্যকরভাবে চালানোর জন্য হাজার হাজার কোর বিশিষ্ট GPU ব্যবহৃত হয়।
– CPU এর তুলনায় GPU অনেক দ্রুতগতিতে ম্যাট্রিক্স ও টেনসর অপারেশন করতে সক্ষম।
– LLM ট্রেনিং ও ইনফারেন্স—দুটোর ক্ষেত্রেই GPU অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।
– বর্তমান সময়ে NVIDIA A100, H100 এর মতো GPU LLM এর জন্য সবচেয়ে ব্যবহৃত।
– GPU এর ক্ষমতা যত বেশি হবে, তত দ্রুত ও কার্যকরভাবে LLM চালানো সম্ভব হবে।
অন্য যন্ত্রাংশগুলোর ভূমিকা:
– RAM: ডেটা সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করে এবং GPU/CPU তে সরবরাহ করে।
– Processor (CPU): সাধারণ কাজ, সিস্টেম কন্ট্রোল ও ডেটা হ্যান্ডলিং এ সহায়তা করে।
– Storage Device: ডেটাসেট, মডেল ফাইল ও চেকপয়েন্ট সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।
– যদিও RAM, Processor এবং Storage Device জরুরি, কিন্তু LLM চালানোর জন্য – সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল Graphics Card (GPU).
সূত্র: – ASUS [link] – geeksforgeeks [link]
প্রশ্ন ১৬০. Quantum Computing এর জনক কাকে মনে করা হয়?
ক) David Deutsch খ) Richard Feynman
গ) Paul Benloff ঘ) Alexei Kitaev
সঠিক উত্তর: ক) David Deutsch
Live MCQ Analytics: Right: 2%; Wrong: 19%; Unanswered: 77%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
• কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের জনক হিসেবে ডেভিড ডয়েচ (David Deutsch)-কে মনে করা হয়। তিনি ১৯৮৫ সালে প্রথম একটি সাধারণ উদ্দেশ্যপূর্ণ কোয়ান্টাম কম্পিউটার মডেল প্রস্তাব করেন, যা “ইউনিভার্সাল কোয়ান্টাম কম্পিউটার” নামে পরিচিত। তার কাজ প্রমাণ করে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নীতি ব্যবহার করে এমন কম্পিউটার তৈরি করা সম্ভব, যা ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার দিয়ে সমাধান করা প্রায় অসম্ভব কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারে। যদিও রিচার্ড ফাইনম্যান, পল বেনিওফ প্রমুখ গবেষকরা কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের ধারণা ও ভিত্তি তৈরিতে অবদান রাখেন, তবুও পূর্ণাঙ্গ মডেল উপস্থাপনের জন্য ডয়েচ-ই এ ক্ষেত্রে “জনক” হিসেবে স্বীকৃত।
• “Father of quantum computing” উপাধিটি আধুনিক উৎসে সবচেয়ে বেশি David Deutsch –এর নামের সাথে ব্যবহৃত হয়। তিনি ১৯৮৫ সালে universal quantum computer-এর আনুষ্ঠানিক তত্ত্ব (quantum Turing machine, quantum logic gates) প্রস্তাব করেন—যা কেবল ধারণা নয়, একটি সাধারণ ফ্রেমওয়ার্ক দেয় কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম ও কম্পিউটেশনের জন্য। তাই গণমাধ্যম ও রেফারেন্স গ্রন্থে তাঁকে “father of quantum computing” বলা হয়।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে,
– David Deutsch এর পূর্বে Richard Feynman ১৯৮১/৮২ সালে Simulating Physics with Computers-এ কোয়ান্টাম সিস্টেমকে কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে সিমুলেট করার যুক্তি দেন- যা ক্ষেত্রটির সূচনালগ্নের অনুপ্রেরণা। পরে Deutsch সেই ধারণাকে “universal” মডেলে রূপ দেন। তাই অনেক লেখায় Feynman-কে পথপ্রদর্শক/অগ্রদূত বলা হলেও “জনক” হিসেবে Deutsch-কেই বেশি উল্লেখকরা হয়।
– উল্লেখ্য, রিচার্ড ফেইনম্যান প্রথম কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ধারণা দেন।
– Richard Feynman was the first scientist who proposed the idea of a quantum computer.
– কিন্তু, Quantum Computing এর জনক (Father Of Quantum Computing) হচ্ছেন – David Deutsch.
• অপশন আলোচনা:
ক) David Deutsch – কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের জনক হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত, ১৯৮৫ সালে প্রথম কোয়ান্টাম টুরিং মেশিন প্রস্তাব করেন।
খ) Richard Feynman – ১৯৮১ সালে কোয়ান্টাম সিস্টেম সিমুলেশনের জন্য কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহারের ধারণা দেন।
গ) Paul Benioff – ১৯৮০ সালে প্রথম কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মডেলে কম্পিউটার বর্ণনা করেন।
ঘ) Alexei Kitaev – টপোলজিক্যাল কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও কিটায়েভ অ্যালগরিদমের জন্য বিখ্যাত।
• কোয়ান্টাম কম্পিউটিং- এ অবদান রাখা উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী:
• ডেভিড ডয়চ (David Deutsch):
– ডেভিড ডয়চ একজন ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী।
– তিনি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর জনক হিসেবে পরিচিত।
– ডয়চ কোয়ান্টাম টিউরিং মেশিন (Quantum Turing Machine) ধারণাটি প্রবর্তন করেন।
– তার গবেষণায় কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হয়।
• পিটার শোর (Peter Shor):
– পিটার শোর একজন আমেরিকান গণিতবিদ এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী।
– শোরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাজ হলো শোরের অ্যালগরিদম (Shor’s Algorithm)।
– শোরের অ্যালগরিদম কোয়ান্টাম কম্পিউটারে বৃহৎ সংখ্যার ফ্যাক্টরাইজেশনকে কার্যকরীভাবে সমাধান করতে পারে।
– এটি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর নিরাপত্তা এবং ক্রিপ্টোগ্রাফির ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।
• গ্রোভার(Lov Grover):
– লাভ্লস একজন আমেরিকান কম্পিউটার বিজ্ঞানী।
– গ্রোভারের অ্যালগরিদম (Grover’s Algorithm) কোয়ান্টাম সার্চিং অ্যালগরিদম হিসেবে পরিচিত।
– এটি ডাটাবেস অনুসন্ধানের কাজকে তাত্ত্বিকভাবে দ্রুততর করে।
– গ্রোভার কোয়ান্টাম অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।
• রিচার্ড ফেইনম্যান (Richard Feynman):
– রিচার্ড ফেইনম্যান একজন আমেরিকান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী।
– ফেইনম্যান কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং কুইন্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স (QED) এর ক্ষেত্রে বিখ্যাত।
– তিনি প্রথমে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ধারণার ধারণা দেন এবং ১৯৮১ সালে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।
– ফেইনম্যান নোবেল পুরস্কার পান ১৯৬৫ সালে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্সে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য।
• কোয়ান্টাম কম্পিউটার:
– এটি এমন একটি কম্পিউটার যা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গুণাবলী (যেমন: সুপারপজিশন ও এনট্যাঙ্গলমেন্ট) ব্যবহার করে জটিল গণনা করে।
– প্রচলিত ডিজিটাল কম্পিউটারের চেয়ে অনেক দ্রুত ও শক্তিশালী হতে পারে।
– রিচার্ড ফেইনম্যান প্রথম কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ধারণা দেন।
– কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার করে কিউবিট (Quantum Bit), যা একসাথে 0 এবং 1 হতে পারে – একে বলে Superposition।
– একটি কিউবিট একই সাথে অনেকগুলো সম্ভাব্য অবস্থায় থাকতে পারে। এটি একাধিক গাণিতিক সমস্যার সমাধান একই সাথে করতে সাহায্য করে।
– ডেভিড ডয়চ (১৯৮৫): কোয়ান্টাম লজিক গেটের ধারণা দেন।
– পিটার শোর (১৯৯৪): কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম উদ্ভাবন করেন যা বড় সংখ্যা অল্প সময়ে ভেঙে ফেলতে পারে।
• কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ৩টি মূল পদ্ধতি:
– NMR (Nuclear Magnetic Resonance): নিউক্লিয়াস স্পিন ব্যবহার করে।
– Ion Trap: আয়নকে ট্র্যাপ করে এবং লেজার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
– Quantum Dots: অতি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহী অঞ্চলে ইলেকট্রনের স্পিন ব্যবহৃত হয়।
• কোয়ান্টাম কম্পিউটিং:
– কোয়ান্টাম কম্পিউটিং আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং গাণিতিক সমস্যাগুলির সমাধানে একটি বিপ্লবী ধারণা।
– এটি কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর ধারণা ব্যবহার করে, যেখানে কোয়ান্টাম বিট (Qubit) একাধিক অবস্থানে থাকতে পারে, এবং তার ফলে এটি নির্দিষ্ট কাজগুলো খুব দ্রুত এবং দক্ষভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।
– কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের জন্য যে অ্যালগরিদমগুলি তৈরি হয়েছে, সেগুলি সাধারণত ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের তুলনায় কিছু সমস্যা সমাধানে অনেক দ্রুত কাজ করে।
– এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোয়ান্টাম অ্যালগরিদমের মধ্যে একটি হল Shor’s Algorithm, যা বড় সংখ্যার গুণফল বের করা (Integer Factorization) এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
Shor’s Algorithm:
– Shor’s Algorithm কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের একটি প্রধান অ্যালগরিদম যা বড় সংখ্যাকে দ্রুত গুণফলে বিভক্ত (factorization) করতে পারে।
– এটা বিন্যাসযোগ্য সংখ্যা গুণফল (large number factorization) বের করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এর মাধ্যমে আধুনিক ক্রিপ্টোগ্রাফি সিস্টেম যেমন RSA সিকিউরিটি ভেঙে ফেলতে পারে।
– Shor’s Algorithm একটি কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যাগুলি অনেক দ্রুত সমাধান করতে সক্ষম, যেখানে সাধারণ কম্পিউটারে এসব সমস্যা সমাধান করতে কয়েক হাজার বছর সময় লাগতে পারে।
– Grover’s algorithm – কোয়ান্টাম কম্পিউটিং অ্যালগরিদমের আরেকটি উদাহরণ।
উৎস: 1) ব্রিটানিকা। 2) theguardian [link] 3) economist [link]
4) geeksforgeeks [link]
গাণিতিক যুক্তি
প্রশ্ন ১৬১. ক) খ)
গ) ঘ)
সঠিক উত্তর: ক)
Live MCQ Analytics: Right: 67%; Wrong: 5%; Unanswered: 27%; [Total: 13700]
সমাধান:
সঠিক উত্তর: ক
প্রশ্ন ১৬২. যদি কোনো বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ 10% বৃদ্ধি করা হয়, তবে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে?
ক) 20% খ) 25%
গ) 21% ঘ) 16%
সঠিক উত্তর: গ) 21%
Live MCQ Analytics: Right: 70%; Wrong: 6%; Unanswered: 22%; [Total: 30415]
সমাধান:
ধরি,
বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = 100 একক
∴ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (100)2 বর্গএকক
= 10000 বর্গএকক
আবার,
বাহুর দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করা হলে,
∴ বাহুর নতুন দৈর্ঘ্য = (100 + 100 এর 10%) একক
= (100 + 100 এর 10/100) একক
= (100 + 10) একক
= 110 একক
∴ বর্গক্ষেত্রের নতুন ক্ষেত্রফল = (110)2 = 12100 বর্গ একক
∴ ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায় = (12100 – 10000) বর্গ একক = 2100 বর্গ একক
এখন,
10000 বর্গ এককে বৃদ্ধি পায় = 2100 বর্গ একক
∴ 1 বর্গ এককে বৃদ্ধি পায় = 2100/10000 বর্গ একক
∴ 100 বর্গ এককে বৃদ্ধি পায় = {(2100 × 100)/10000} বর্গ একক
= 21 বর্গ একক
∴ ক্ষেত্রফল শতকরা বৃদ্ধি পাবে = 21%
প্রশ্ন ১৬৩. 100 টাকা 10% হারে 5 বছরের জন্য বিনিয়োগ করা হলে, সরল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত?
ক) 10.05 টাকা খ) 11.05 টাকা
গ) 12.05 টাকা ঘ) 13.05 টাকা
সঠিক উত্তর: খ) 11.05 টাকা
Live MCQ Analytics: Right: 31%; Wrong: 10%; Unanswered: 58%; [Total: 30415]
সমাধান:
মূলধন, P = 100 টাকা
সুদের হার, r = 10% = 10/100 = 1/10
সময়, n = 5 বছর
আমরা জানি,
সরল মুনাফার ক্ষেত্রে,
SI = P × r × n
= 100 × (1/10) × 5
= 50 টাকা
আবার,
চক্রবৃদ্ধি মুনাফায়,
C = P(1 + r)n
= 100 × (1 + 1/10)5
= 100 × (11/10)5
= 100 × (11/10) × (11/10) × (11/10) × (11/10) × (11/10)
= 100 × (161051/100000)
= 161051/1000
= 161.051 টাকা
∴ চক্রবৃদ্ধি মুনাফা = C – P
= (161.051 – 100) টাকা
= 61.051 টাকা
∴ সরল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য = 61.051 – 50 = 11.051 টাকা
প্রশ্ন ১৬৪. যদি x = √5 + √3 হয়, তবে এর মান কত?
ক) 18√5 খ) 22√5
গ) 28√5 ঘ) 32√5
সঠিক উত্তর: গ) 28√5
Live MCQ Analytics: Right: 29%; Wrong: 9%; Unanswered: 60%; [Total: 30415]
সমাধান:
প্রশ্ন ১৬৫. |x – 5| < 2, x ∈ IN অসমতাটির সমাধান সেট কোনটি?
ক) (3, 7) খ) [3, 7]
গ) {4, 5, 6} ঘ) {3, 4, 5, 6, 7}
সঠিক উত্তর: গ) {4, 5, 6}
Live MCQ Analytics: Right: 33%; Wrong: 35%; Unanswered: 30%; [Total: 30415]
সমাধান:
দেওয়া আছে,
|x – 5| < 2 এবং x ∈ N
⇒ – 2 < x – 5 < 2
⇒ – 2 + 5 < x – 5 + 5 < 2 + 5
⇒ 3 < x < 7
এখন,
x ∈ N এর অর্থ হলো x স্বাভাবিক সংখ্যা যা 3 থেকে বড় এবং 7 থেকে ছোট।
সুতরাং, 3 < x < 7 সীমার মধ্যে স্বাভাবিক সংখ্যা গুলো হলো 4, 5, 6
সুতরাং, সমাধান সেট = {4, 5, 6}
প্রশ্ন ১৬৬. যদি 5x3 – 2x2 + x + k = 0 এর একটি উৎপাদক (x – 3) হয়, তাহলে k এর মান কত?
ক) 50 খ) 60
গ) – 120 ঘ) – 60
সঠিক উত্তর: গ) – 120
Live MCQ Analytics: Right: 65%; Wrong: 1%; Unanswered: 32%; [Total: 30415]
সমাধান:
ধরি,
f(x) = 5x3 – 2x2 + x + k
∴ f(3) = 5(3)3 – 2(3)2 + 3 + k
= 5 × 27 – 2 × 9 + 3 + k
= 135 – 18 + 3 + k
= 120 + k
এখন,
5x3 – 2x2 + x + k এর একটি উৎপাদক x – 3 হলে, f(3) = 0 হবে,
এখন
f(3) = 0
⇒ 120 + k = 0
∴ k = – 120
প্রশ্ন ১৬৭. নিচের সিরিজের ফাঁকা যায়গায় কোন সংখ্যা হবে?
243, 81, ___ , 9, 3, 1
ক) 9 খ) 27
গ) 12 ঘ) 6
সঠিক উত্তর: খ) 27
Live MCQ Analytics: Right: 81%; Wrong: 0%; Unanswered: 17%; [Total: 30415]
সমাধান:
১ম পদ = 243
২য় পদ = 243 ÷ 3 = 81
৩য় পদ = 81 ÷ 3 = 27
৪র্থ পদ = 27 ÷ 3 = 9
৫ম পদ = 9 ÷ 3 = 3
৬ষ্ঠ পদ = 3 ÷ 3 = 1
অতএব, ফাঁকা যায়গায় 27 সংখ্যা হবে।
বিকল্প:
243, 81, ___ , 9, 3, 1
35, 34, 33, 32, 31, 30
অতএব, ফাঁকা যায়গায় 27 সংখ্যা হবে। 33 = 27
প্রশ্ন ১৬৮. যদি logx324 = 4 হয়, তবে x এর মান কত?
ক) 3√2 খ) 4√2
গ) 5√2 ঘ) √2
সঠিক উত্তর: ক) 3√2
Live MCQ Analytics: Right: 66%; Wrong: 4%; Unanswered: 28%; [Total: 30415]
সমাধান: logx324 = 4
⇒ x4 = 324
⇒ x4 = 81 × 4
⇒ x4 = 34 × 22
⇒ x4 = 34 × (√2)4
⇒ x4 = (3√2)4
⇒ x = 3√2
∴ x = 3√2
প্রশ্ন ১৬৯. একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় পদ যথাক্রমে 27 এবং 9, তাহলে ধারাটির দশম পদ কত?
ক) 1/3 খ) 1/525
গ) 1/729 ঘ) 1/615
সঠিক উত্তর: গ) 1/729
Live MCQ Analytics: Right: 64%; Wrong: 1%; Unanswered: 33%; [Total: 30415]
সমাধান: দেওয়া আছে
ধারাটির প্রথম পদ, a = 27
ধারাটির দ্বিতীয় পদ, ar2 – 1 = ar = 9
অতএব সাধারণ অনুপাত, r = 9/27 = 1/3
আমরা জানি,
গুণোত্তর ধারার n তম পদ = arn – 1
∴ দশম পদ, ar10 – 1 = 27(1/3)9
= (33 × 1)/(33 × 36)
= 1/36
= 1/729
সুতরাং, ধারাটির দশম পদ 1/729
প্রশ্ন ১৭০. একটি বৃত্তস্থ বর্গের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 2 সে.মি. হলে, ঐ বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত?
ক) π খ) 2π
গ) √2π ঘ) 2√2π
সঠিক উত্তর: খ) 2π
Live MCQ Analytics: Right: 58%; Wrong: 10%; Unanswered: 30%; [Total: 30415]
সমাধান:
দেওয়া আছে,
বৃত্তস্থ বর্গের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য = 2 সে.মি.
যদি একটি বর্গ বৃত্তস্থ হয়, তবে বৃত্তের ব্যাস = বর্গক্ষেত্রের কর্ণ
∴ বর্গক্ষেত্রের কর্ণ = √(22 + 22)
= √(4 + 4)
= √8
= 2√2 সে.মি.
অতএব, বৃত্তের ব্যাস = 2√2 সে.মি.
এখন,
বৃত্তের ব্যাসার্ধ, r = 2√2/2 = √2 সে.মি.
আমরা জানি,
বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr2 = π × (√2)2 = 2π বর্গ সে.মি.
প্রশ্ন ১৭১. 4 জন তাঁতী 4 দিনে 4টি মাদুর তৈরি করতে পারে। একই হারে 8 জন তাঁতী 8 দিনে কতটি মাদুর তৈরি করতে পারবে?
ক) 8টি খ) 12টি
গ) 16টি ঘ) 20টি
সঠিক উত্তর: গ) 16টি
Live MCQ Analytics: Right: 57%; Wrong: 17%; Unanswered: 24%; [Total: 30415]
সমাধান:
4 জন তাঁতি 4 দিনে মাদুর তৈরি করে = 4 টি
∴ 1 জন তাঁতি 1 দিনে মাদুর তৈরি করে = 4/(4 × 4) টি
∴ 8 জন তাঁতি 8 দিনে মাদুর তৈরি করে = (4 × 8 × 8)/(4 × 4) টি
= 16 টি
∴ 16 টি মাদুর তৈরি করতে পারবে।
প্রশ্ন ১৭২. (0, 0) এবং (3, 3) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ কোনটি?
ক) y = x খ) y = 3x
গ) y = x + 3 ঘ) y = 3x + 3
সঠিক উত্তর: ক) y = x
Live MCQ Analytics: Right: 58%; Wrong: 9%; Unanswered: 31%; [Total: 13460]
সমাধান:
দেওয়া আছে,
(x1, y1) = (0, 0) এবং (x2, y2) = (3, 3)
আমরা জানি,
দুটি বিন্দু (x1, y1) এবং (x2, y2) দিয়ে গঠিত সরলরেখার ঢাল,
m = (y2 – y1)/(x2 – x1)
= (3 – 0)/(3 – 0)
= 3/3
∴ m = 1
আমরা জানি,
সরলরেখার সমীকরণ,
y – y1 = m(x – x1)
⇒ y – 0 = 1 (x – 0) ; [(x1, y1) = (0, 0) এবং m = 1 বসিয়ে]
∴ y = x
অতএব, (0, 0) এবং (3, 3) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ হলো y = x বা x – y = 0
প্রশ্ন ১৭৩. যদি nC12 = nC8 হয়, তবে 22Cn এর মান কত?
ক) 230 খ) 231
গ) 232 ঘ) 233
সঠিক উত্তর: খ) 231
Live MCQ Analytics: Right: 35%; Wrong: 3%; Unanswered: 60%; [Total: 30415]
সমাধান:
দেওয়া আছে,
nC12 = nC8
⇒ nCn – 12 = nC8
⇒ n – 12 = 8
∴ n = 12 + 8 = 20
সুতরাং, প্রদত্ত রাশি,
= 22Cn
= 22C20 ; [n = 20]
= 22!/(20! × 2!)
= (22 × 21 × 20!)/(20! × 2)
= 11 × 21
= 231
প্রশ্ন ১৭৪. A = {x ∈ IN : 2 < x ≤ 6} এবং B = {x ∈ IN : x জোড় সংখ্যা এবং x ≤ 8} হলে A ∩ B এর মান কত?
ক) {3, 2} খ) {4, 6}
গ) {5, 6} ঘ) {4, 8}
সঠিক উত্তর: খ) {4, 6}
Live MCQ Analytics: Right: 71%; Wrong: 1%; Unanswered: 26%; [Total: 30415]
সমাধান:
দেয়া আছে,
A = {x ∈ N : 2 < x ≤ 6}
এখানে, x এর মান 2 থেকে বড় এবং 6 এর ছোট বা সমান স্বাভাবিক সংখ্যা।
∴ A = {3, 4, 5, 6}
আবার,
B = {x ∈ N : x জোড় সংখ্যা এবং x ≤ 8}
x স্বাভাবিক জোড় সংখ্যা যা 8 এর ছোট বা সমান।
∴ B = {2, 4, 6, 8}
প্রদত্ত রাশি,
A ∩ B = {3, 4, 5, 6} ∩ {2, 4, 6, 8} = {4, 6}
∴ A ∩ B = {4, 6}
প্রশ্ন ১৭৫. একটি ব্যাগে 2টি লাল, 3টি সবুজ এবং 2টি নীল বল আছে। যদি দৈবভাবে 2টি বল নেওয়া হয়, তাহলে বল দুটির কোনটিই নীল না হওয়ার সম্ভাবনা কত?
ক) 10/21 খ) 11/21
গ) 2/7 ঘ) 5/7
সঠিক উত্তর: ক) 10/21
Live MCQ Analytics: Right: 15%; Wrong: 42%; Unanswered: 42%; [Total: 30415]
সমাধান: মোট বলের সংখ্যা = 2 + 3 + 2 = 7
• নীল নয় এমন বলের সংখ্যা = 7 – 2 = 5
এখন,
7 টি বলের মধ্যে 5 টি বল নীল নয়।
∴ P(প্রথম বলটি নীল নয়) = 5/7
আবার,
প্রথম বলটি তোলার পরে, বাকি 6 টি বলের মধ্যে 4 টি বল নীল নয়।
∴ P (দ্বিতীয় বলটি নীল নয়) = 4/6 = 2/3
∴ P (টানা দুটি বলের কোনটিই নীল নয়) = (5/7) × (2/3) = 10/21
সুতরাং, বল দুটির কোনটিই নীল না হওয়ার সম্ভাবনা = 10/21
মানসিক দক্ষতা
প্রশ্ন ১৭৬. Seed : Sapling :: Egg : ?
ক) Omlette খ) Chicken
গ) Yolk ঘ) Chick
সঠিক উত্তর: ঘ) Chick
Live MCQ Analytics: Right: 30%; Wrong: 31%; Unanswered: 38%; [Total: 30415]
সমাধান: Seed মানে বীজ, Sapling মানে চারা গাছ
বীজ থেকে যেমন চারা গাছ হয়,
তেমনি, ডিম থেকে বাচ্চা হয়।
তাই, Egg : Chick হবে।
অন্য অপশনগুলো:
Omlette – প্রস্তুত খাবার, সম্পর্ক নেই
Chicken – পরিপূর্ণ মুরগি, কিন্তু Egg-এর সরাসরি উৎপাদিত নয়
Yolk – শুধু ডিমের অংশ, সম্পর্ক ঠিক নয়
সুতরাং, Seed : Sapling :: Egg : Chick
প্রশ্ন ১৭৭. যদি MFNPO অর্থ ‘Lemon’ হয়, তবে NBOHP অর্থ কী?
ক) Mango খ) Table
গ) Light ঘ) Shirt
সঠিক উত্তর: ক) Mango
Live MCQ Analytics: Right: 77%; Wrong: 0%; Unanswered: 22%; [Total: 30415]
সমাধান:
MFNPO অর্থ ‘Lemon’
এখানে, প্রতিটি বর্ণ তার পূর্বের বর্ণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।
একইভাবে,
সুতরাং, ‘NBOHP’ এর অর্থ ‘Mango’
প্রশ্ন ১৭৮. প্রদত্ত চিত্রে ত্রিভুজের সংখ্যা নির্ণয় করুন?
ক) ১৫ খ) ১৬
গ) ৭ ঘ) ৯
সঠিক উত্তর: খ) ১৬
Live MCQ Analytics: Right: 55%; Wrong: 20%; Unanswered: 24%; [Total: 30415]
সমাধান:
১টি ফাঁকা স্থান নিয়ে ত্রিভুজগুলো হলো-
AGE, EGC, GFC, BGF, DGB এবং ADG = ৬টি
২টি ফাঁকা স্থান নিয়ে ত্রিভুজগুলো হলো-
AGC, BGC, ABG = ৩টি
৩টি ফাঁকা স্থান নিয়ে ত্রিভুজগুলো হলো-
AFC, BEC, BDC, ABF, ABE এবং DAC = ৬টি
সবগুলো ফাঁকা স্থান নিয়ে ত্রিভুজ ABC = ১টি
∴ সর্বমোট ত্রিভুজের সংখ্যা = ৬ + ৩ + ৬ + ১ = ১৬ টি
প্রশ্ন ১৭৯. কোনটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থলাভিষিক্ত হবে?
ক) ১৮ খ) ১২
গ) ৯ ঘ) ৬
সঠিক উত্তর: গ) ৯
Live MCQ Analytics: Right: 40%; Wrong: 1%; Unanswered: 57%; [Total: 30415]
সমাধান: উপরের সংখ্যা গুলোর সমষ্টি ÷ ১০ = নিচের সংখ্যা
১ম চিত্রে,
১৮ + ১২ + ২০ = ৫০ ÷ ১০ = ৫
২য় চিত্রে,
১৬ + ১৪ + ৩০ = ৬০ ÷ ১০ = ৬
৩য় চিত্রে,
৪৫ + ১৮ + ২৭ = ৯০ ÷ ১০ = ৯
সুতরাং, প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থলাভিষিক্ত হবে ৯ সংখ্যাটি।
প্রশ্ন ১৮০. পানিতে প্রদত্ত প্রতিচ্ছবিগুলোর সাথে কোনটি ইংরেজিতে একটি শব্দের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
ক) খ) গ) ঘ) সঠিক উত্তর: ঘ)
Live MCQ Analytics: Right: 55%; Wrong: 18%; Unanswered: 26%; [Total: 30415]
সমাধান:
অপশনে সরাসরি সঠিক উত্তর নেই। W এর প্রতিচ্ছবি সম্পূর্ণভাবে M হয় না।
তবে অপশন বিবেচনায় ঘ) সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য। তাই অপশন ঘ) কে সঠিক উত্তর হিসাবে নেওয়া হয়েছে।
প্রশ্ন ১৮১. একজন ব্যক্তি ৪ মাইল উত্তরে, ১২ মাইল পূর্বে এবং তারপরে ১২ মাইল উত্তরে ভ্রমণ করেন। তিনি শুরুর বিন্দু থেকে কত দূরে আছেন?
ক) ২৮ মাইল খ) ২৪ মাইল
গ) ২১ মাইল ঘ) ২০ মাইল
সঠিক উত্তর: ঘ) ২০ মাইল
Live MCQ Analytics: Right: 56%; Wrong: 9%; Unanswered: 33%; [Total: 30415]
সমাধান:
ED = EC + CD = AB + CD = ৪ + ১২ = ১৬ মাইল
AE = BC = ১২ মাইল
∴ দূরত্ব AD = √(ED2 + AE2)
= √(১৬২ + ১২২)
= √(২৫৬ + ১৪৪)
= √৪০০
= ২০ মাইল
সুতরাং, শুরুর বিন্দু থেকে ২০ মাইল দূরে আছেন।
প্রশ্ন ১৮২. পাঁচজন ব্যক্তি গোল হয়ে বসে আছে এবং মাঝখানে তাকিয়ে তাস খেলছে। রাজিবের বামদিকে রয়েছে মুকুল, বিজয় রয়েছে অনিক ও নুরুলের মাঝখানে এবং অনিকের ডান দিকে। তাহলে নুরুলের ডান দিকে কে রয়েছে?
ক) অনিক খ) বিজয়
গ) মুকুল ঘ) রাজিব
সঠিক উত্তর: গ) মুকুল
Live MCQ Analytics: Right: 45%; Wrong: 22%; Unanswered: 31%; [Total: 30415]
সমাধান:
দেওয়া তথ্য মতে,
রাজিবের বামদিকে মুকুল।
বিজয় অনিক ও নুরুলের মাঝে আছে।
বিজয় অনিকের ডান দিকে আছে অর্থাৎ অনিকের ডান পাশে যে ব্যক্তি আছে তিনি বিজয়।
অতএব নূরুলের ডান দিকে সবসময় মুকুলই থাকে।
অতএব উত্তর: মুকুল।
প্রশ্ন ১৮৩. A যদি B এর সাথে খাপখায় যেমনভাবে C, D এর সাথে, তাহলে নিচের জোড়াগুলোর মধ্যে কোন জোড়া যুক্তিযুক্তভাবে খাপ খায়?
ক) পাখিকে যেমন দৌড়াতে হয়, মাছকে তেমন সাঁতার কাটতে হয়
খ) আঁধারের বিপরীত যেমন উজ্জল, তেমনি নীরবতার বিপরীত হলো উচ্চশব্দ
গ) খাদ্য যেমন খাবারের জন্য, পানি তেমনি পান করার জন্য
ঘ) রঙ যেমন ছায়াযুক্ত হয়, গতি তেমনি দ্রুত হয়
সঠিক উত্তর: গ) খাদ্য যেমন খাবারের জন্য, পানি তেমনি পান করার জন্য
Live MCQ Analytics: Right: 36%; Wrong: 18%; Unanswered: 45%; [Total: 30415]
সমাধান:
এই ধরনের যুক্তিভিত্তিক প্রশ্নে আমাদের দেখতে হবে কোন জোড়ায় সম্পর্কের ধরন একই রকম।
“A যদি B এর সাথে খাপখায় যেমনভাবে C, D এর সাথে” – এর মানে হলো:
• A এবং B এর মধ্যে যে সম্পর্ক,
• C এবং D এর মধ্যে সেই একই ধরনের সম্পর্ক।
» খাদ্য যেমন খাবারের জন্য, পানি তেমনি পান করার জন্য
ধরি, A = খাদ্য, B = খাবারের জন্য, C = পানি, D = পান করার জন্য।
সম্পর্ক বিশ্লেষণ:
খাদ্য এবং খাবারের জন্য: খাদ্য মানুষের জীবনধারণের জন্য খাওয়া হয়। এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক, যেখানে খাদ্যের উদ্দেশ্য হলো খাওয়া।
পানি এবং পান করার জন্য: পানি জীবনধারণের জন্য পান করা হয়। এটিও একটি উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক।
তুলনা: উভয় ক্ষেত্রেই A এবং C (খাদ্য এবং পানি) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, এবং B এবং D (খাবারের জন্য এবং পান করার জন্য) তাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্য নির্দেশ করে। এই সম্পর্কটি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।
অন্য অপশন গুলো:
ক) পাখিকে যেমন দৌড়াতে হয়, মাছকে তেমন সাঁতার কাটতে হয়।
ভুল, কারণ পাখি দৌড়ায় না, উড়ে। তাই সম্পর্কটি সঠিক নয়।
খ) আঁধারের বিপরীত যেমন উজ্জ্বল, তেমনি নীরবতার বিপরীত হলো উচ্চশব্দ।
এখানে ‘আঁধার – উজ্জ্বল’ বিপরীতার্থক সম্পর্ক, আর ‘নীরবতা – উচ্চশব্দ’ ও বিপরীতার্থক সম্পর্ক। যা সঠিক নয়।
ঘ) রঙ যেমন ছায়াযুক্ত হয়, গতি তেমনি দ্রুত হয়।
রঙের ছায়া হওয়া এবং গতির দ্রুত হওয়ার মধ্যে কোন যৌক্তিক সম্পর্ক নেই।
সুতরাং, সঠিক উত্তর – গ) খাদ্য যেমন খাবারের জন্য, পানি তেমনি পান করার জন্য।
প্রশ্ন ১৮৪. হাত, চোখ ও মস্তিষ্কের কার্যাবলি এতটাই ______ যে শৈশব কালের প্রথম দিকে হাতের ব্যবহার সম্পূর্ণ ______ বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে। উপরের ফাঁকা যায়গাগুলো নিম্নে উল্লিখিত জোড়াশব্দ দিয়ে পূরণ করুন।
ক) অপরিবর্তনীয় – বুদ্ধিসম্পর্কিত
খ) রহস্যময় – মনস্তাত্ত্বিক
গ) নিয়ন্ত্রিত – কিশোর
ঘ) ঘনিষ্টভাবে যুক্ত – প্রত্যক্ষণমূলক
সঠিক উত্তর: ঘ) ঘনিষ্টভাবে যুক্ত – প্রত্যক্ষণমূলক
Live MCQ Analytics: Right: 40%; Wrong: 24%; Unanswered: 34%; [Total: 30415]
সমাধান:
হাত, চোখ ও মস্তিষ্কের কার্যাবলি যদি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে তবে শিশুর প্রত্যক্ষণমূলক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।
‘ঘনিষ্টভাবে যুক্ত – প্রত্যক্ষণমূলক‘: এটি সবচেয়ে উপযুক্ত। হাত, চোখ ও মস্তিষ্কের কার্যাবলি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত (interconnected), এবং হাতের ব্যবহার প্রত্যক্ষণমূলক (perceptual) বিকাশকে ত্বরান্বিত করে (যেমন, দৃষ্টি-স্পর্শ সমন্বয়, স্থানিক বোধ ইত্যাদি)।
সুতরাং, সঠিক জোড়া হলো: ঘ) ঘনিষ্টভাবে যুক্ত – প্রত্যক্ষণমূলক।
উল্লেখ্য, অপশনের বাকি শব্দগুলো শূন্যস্থানে যথার্থ নয়।
প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়া:
– পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে আমরা যেসব অভিজ্ঞতা লাভ করি-অর্থাৎ পৃথিবীকে যেমন দেখি, শুনি, স্পর্শ করি, অনুভব করি, ঘ্রাণ পাই, স্বাদ নিই- সেগুলোই আমাদের প্রত্যক্ষণ। যে কোন বস্তুর বাস্তব অভিজ্ঞতাই প্রত্যক্ষণ।
– এ প্রেক্ষাপটে মরগান, কিং ও রবিনসন (১৯৭৯) বলেন, প্রত্যক্ষণ হলো আমরা যেভাবে বিশ্বকে দেখি, শুনি, অনুভব করি, স্বাদ গ্রহণ করি বা ঘ্রাণ নেই [Perception refers to the way the world looks, sounds, feels, tastes or smells] ।
– প্রত্যক্ষণ হলো একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে জীব তথা মানুষ ইন্দ্রিয় শক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর সব কিছুকে উপলব্ধি করে জ্ঞানীয় প্রক্রিয়া ব্যবহার করে একটি অর্থবহ ব্যাখ্যা দিতে পারে।
উৎস: শিল্প মনোবিজ্ঞান, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ১৮৫. নিম্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর মধ্যে কোন বানানটি সঠিক খুঁজে বের করুন?
ক) Randezvos খ) Rendezvous
গ) Rondezvous ঘ) Rendavous
সঠিক উত্তর: খ) Rendezvous
Live MCQ Analytics: Right: 32%; Wrong: 10%; Unanswered: 57%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:
সঠিক উত্তর: খ) Rendezvous.
• Rendezvous
English Meaning: an arrangement to meet someone, especially secretly, at a particular place and time, or the place itself.
Bangla Meaning: (১) একটি সম্মত সময়ে পরস্পর সাক্ষাৎ এবং ঐরূপ সাক্ষাতের স্থান; সংকেতস্থান। (২) যে স্থানে লোকে প্রায়ই মিলিত হয়; মিলনস্থল।
Example Sentence:
– We have a rendezvous for next week, don’t we?
– The lovers met at a secret rendezvous in the park.
Source:
1. Cambridge Dictionary.
2. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
প্রশ্ন ১৮৬. একটি গিয়ার ট্রেনে তিনটি গিয়ার আছে, গিয়ার ‘এ‘ এর ১২টি দাঁত, গিয়ার ‘বি‘ এর ৩৬টি দাঁত, এবং গিয়ার ‘সি‘ এর ২৪টি দাঁত আছে। যদি গিয়ার ‘এ‘ কে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেদিকে ঘোরানো হয়, তাহলে গিয়ার ‘সি‘ কোন দিকে ঘুরবে?
ক) ঘড়ির কাঁটার দিকে খ) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে
গ) স্থির ঘ) একেবারে ঘুরবে না
সঠিক উত্তর: ক) ঘড়ির কাঁটার দিকে
Live MCQ Analytics: Right: 54%; Wrong: 7%; Unanswered: 38%; [Total: 30415]
সমাধান:
গিয়ার ট্রেনের মূল নীতি:
• দুটি পরপর সংযুক্ত গিয়ার বিপরীত দিকে ঘোরে।
উদাহরণ: যদি A ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে ➝ B ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরবে ➝ C আবার ঘড়ির কাঁটার দিকেই ঘুরবে।
গিয়ার ঘূর্ণনের দিক:
1. গিয়ার A : ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরানো হয়েছে ।
2. গিয়ার B : A এর সঙ্গে সংযুক্ত, তাই ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরবে।
3. গিয়ার C : B এর সঙ্গে সংযুক্ত, তাই B এর বিপরীত দিকে ঘুরবে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরবে।
সুতরাং, গিয়ার C ঘুরবে ঘড়ির কাঁটার দিকে।
প্রশ্ন ১৮৭. যখন দুটি বস্তুর সংঘর্ষ হয় এবং তারা একসাথে লেগে থাকে, তখন তাকে কোন ধরনের সংঘর্ষ বলে?
ক) স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ খ) প্লাস্টিক সংঘর্ষ
গ) অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ ঘ) ঘর্ষনীয় সংঘর্ষ
সঠিক উত্তর: খ) প্লাস্টিক সংঘর্ষ
Live MCQ Analytics: Right: 1%; Wrong: 60%; Unanswered: 38%; [Total: 30415]
সমাধান:
চিত্র: পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ।
চিত্রে, পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে। m₁ এবং m₂ ভরের দুটি বস্তু একই সরলরেখায় একই দিকে যথাক্রমে v01 এবং v02 বেগে চলে পরস্পরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটাল। সংঘর্ষের পর বস্তু দুটি পরস্পর যুক্তহয়ে একই দিকে v বেগে চলতে লাগল।
• অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ (Inelastic Collision):
– সংজ্ঞা: এমন সংঘর্ষ যেখানে কাইনেটিক শক্তি সংরক্ষিত হয় না, কিন্তু ভরকেন্দ্রের ভরবেগ (momentum) সংরক্ষিত থাকে।
– সংঘর্ষের সময় কিছু গতি শক্তি তাপ, শব্দ বা বিকৃতি (deformation) আকারে চলে যায়।
– বস্তুগুলো সংযুক্ত হতে বা আলাদা হতে পারে।
– উদাহরণ: দুইটি গাড়ি ধাক্কা খেয়ে টক্কর মারলেও আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু ক্ষতি হয়।
• প্লাস্টিক বা নিখুঁত অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ (Plastic / Perfectly Inelastic Collision):
– সংজ্ঞা: অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের বিশেষ প্রকার যেখানে ধাক্কা খাওয়া বস্তুগুলো সংঘর্ষের পর একসাথে লেগে থাকে।
– গতি শক্তির সর্বাধিক ক্ষতি হয়।
– ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে।
– সংঘর্ষের পর সব বস্তু একই ভরের সাথে একত্রে চলে।
– উদাহরণ: দুটি মাটির গুটি একে অপরকে আঘাত করলে একসাথে লেগে যায়।
উল্লেখ্য,
– সব প্লাস্টিক সংঘর্ষই অস্থিতিস্থাপক, কিন্তু সব অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষই প্লাস্টিক নয়।
– “প্লাস্টিক” = নিখুঁত অস্থিতিস্থাপক = বস্তু সংযুক্ত থাকে।
– “অস্থিতিস্থাপক” = সাধারণ = বস্তু সংযুক্ত বা আলাদা হতে পারে।
– Plastic = Perfectly Inelastic Collision.
– Inelastic Collision = General.
(১) Plastic = Perfectly Inelastic Collision (একসাথে লেগে থাকে)-
(২) Elastic Collision –
(৩) Inelastic Collision (একসাথে লেগে না থেকে, আলাদাও হতে পারে) –
সূত্র: ব্রিটানিকা। [link]
প্রশ্ন ১৮৮. নিচের ছবিগুলোর পাশের প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানে কোন বিকল্পটি বসবে?
ক) ১ খ) ২
গ) ৩ ঘ) ৪
সঠিক উত্তর: গ) ৩
Live MCQ Analytics: Right: 57%; Wrong: 9%; Unanswered: 32%; [Total: 30415]
সমাধান:
এখানে,
১ম চিত্র থেকে ২য় চিত্রে তীরের দিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ১৩৫° ঘুরে, ২য় চিত্র থেকে ৩য় চিত্রে তীরের দিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ১৮০° ঘুরে।
আবার, ৩য় চিত্র থেকে ৪র্থ চিত্রে তীরের দিক ঘড়ির কাঁটার দিকে ১৩৫° ঘুরবে।
সেই হিসাবে সঠিক উত্তর ৩ নং।
প্রশ্ন ১৮৯. পৃথিবীর কক্ষপথের বিভিন্ন বিন্দু থেকে দেখলে কোন ঘটনার কারণে একটি নক্ষত্রের অবস্থানের আপাত পরিবর্তন ঘটে?
ক) ডপলার ইফেক্ট খ) রেডশিক্ট
গ) কসমিক ঘ) প্যারালেক্স
সঠিক উত্তর: ঘ) প্যারালেক্স
Live MCQ Analytics: Right: 5%; Wrong: 26%; Unanswered: 68%; [Total: 30415]
সমাধান:
• নক্ষত্রের অবস্থানের আপাত পরিবর্তন (Parallax):
– প্যারালেক্স হলো সেই ঘটনা যার মাধ্যমে পৃথিবীর কক্ষপথের বিভিন্ন বিন্দু থেকে একই নক্ষত্রের অবস্থান আপাতভাবে পরিবর্তিত দেখায়।
– এটি মূলত দূরত্ব পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়।
– নক্ষত্রের আসল অবস্থান পরিবর্তিত হয় না, কেবল পর্যবেক্ষকের অবস্থানের কারণে তার আপাত অবস্থান পরিবর্তিত দেখায়।
– প্যারালেক্স ব্যবহার করে নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ধারণ করা যায়।
– ডপলার ইফেক্ট, রেডশিফট বা কসমিক ঘটনার কারণে নক্ষত্রের অবস্থানের আপাত পরিবর্তন ঘটে না।
• ডপলার ইফেক্ট (Doppler Effect):
– ডপলার ইফেক্ট হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে কোনো সাউন্ড বা আলো তরঙ্গের পর্যবেক্ষকের দিকে বা থেকে সরে যাওয়ার কারণে তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয়।
– যদি উৎস পর্যবেক্ষকের দিকে চলে আসে, তরঙ্গ সংকুচিত হয় এবং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে।
– যদি উৎস পর্যবেক্ষকের থেকে দূরে সরে যায়, তরঙ্গ প্রসারিত হয় এবং ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়।
– এটি মূলত সাউন্ডে বেশি পরিচিত, যেমন- অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের সুর পরিবর্তন।
– আকাশবিজ্ঞানে, ডপলার ইফেক্ট ব্যবহার করে আমরা নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির গতি নির্ণয় করি।
– তবে এটি নক্ষত্রের আপাত অবস্থান পরিবর্তন ঘটায় না।
• রেডশিফট (Redshift):
– রেডশিফট হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে একটি নক্ষত্র বা আকাশীয় বস্তুর আলো দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে স্থানান্তরিত হয়।
– এর মানে হলো, বস্তুটি পর্যবেক্ষকের দিক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।
– এটি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
– রেডশিফটের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কোন গ্যালাক্সি আমাদের থেকে কত দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে।
– রেডশিফটের কারণ: বস্তুটির গতিবেগ এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ।
– ডপলার ইফেক্টের মত, আলোও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন দেখায়, কিন্তু নক্ষত্রের আপাত অবস্থান পরিবর্তিত হয় না।
• কসমিক (Cosmic):
– কসমিক শব্দটি সাধারণত মহাজাগতিক বা মহাবিশ্বসংক্রান্ত ঘটনা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।
– এটি মহাবিশ্বের বৃহৎ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, যেমন- মহাজাগতিক বিকিরণ, গ্যালাক্সি, কসমিক রশ্মি ইত্যাদি।
– কসমিক ঘটনা নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির আলোতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যেমন- রেডশিফট বা ব্লুশিফট।
– তবে এগুলো নক্ষত্রের আপাত অবস্থান পরিবর্তনের জন্য নয়।
– কসমিক প্রভাব মূলত শক্তি, বিকিরণ বা গতিশীলতার সাথে সম্পর্কিত।
সুতরাং, পৃথিবীর কক্ষপথের বিভিন্ন বিন্দু থেকে নক্ষত্রের আপাত অবস্থান পরিবর্তনের কারণ হল প্যারালেক্স।
সঠিক উত্তর: ঘ) প্যারালেক্স।
সূত্র: NASA [link]
প্রশ্ন ১৯০. প্রশ্নবোধক চিহ্নিত ঘরে কোন সংখ্যাটি বসবে?
ক) ৪ খ) ৫
গ) ৬ ঘ) ৭
সঠিক উত্তর: ক) ৪
Live MCQ Analytics: Right: 18%; Wrong: 5%; Unanswered: 76%; [Total: 30415]
সমাধান:
১৭ + ৮ = ২৫ ; ৫ × ৫ = ২৫
১৩ + ৭ = ২০ ; ৫ × ৪ = ২০
৬ + ১২ = ১৮ ; ৬ × ৩ = ১৮
১০ + ৬ = ১৬ ; ৪ × ৪ = ১৬
সুতরাং, প্রশ্নবোধক চিহ্নিত ঘরে ৪ বসবে।
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন
প্রশ্ন ১৯১. নিচের কোনটি পেশাগত নৈতিকতার উপাদান?
ক) স্বজনপ্রীতি খ) সাম্প্রদায়িকতা
গ) দরিদ্রতা ঘ) দক্ষতা
সঠিক উত্তর: ঘ) দক্ষতা
Live MCQ Analytics: Right: 77%; Wrong: 5%; Unanswered: 17%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ পেশাগত নৈতিকতার উপাদান দক্ষতা।
– স্বজনপ্রীতি, সাম্প্রদায়িকতা, দরিদ্রতা পেশাগত নৈতিকতার উপাদান নয়।
• পেশাগত নৈতিকতার উপাদানগুলোর মধ্যে:
– সততা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, পেশাগত চেতনা, এবং দায়িত্বশীলতা অন্যতম,
– যা পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং জনসাধারণের আস্থা ও সেবার মান উন্নত করে।
• পেশাগত নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ:
– সততা ও স্বচ্ছতা (Integrity and Transparency): পেশাদার কাজে সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা পেশাগত নৈতিকতার একটি মৌলিক দিক।
– দায়বদ্ধতা (Accountability): নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করা এবং পেশাগত কর্মের ফলাফল বা প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকা।
– পেশাগত চেতনা (Professional Consciousness): নিজের পেশার প্রতি গভীর সচেতনতা এবং এর মান ও মর্যাদা বজায় রাখার অঙ্গীকার।
– দায়িত্বশীলতা (Responsibility): পেশাগত দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করা এবং পেশার প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে চলা।
– দক্ষতা ও জ্ঞান (Expertise and Skill): পেশাগত ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রয়োগ করা, যা জনসাধারণের জন্য উপকারে আসে।
∴ সুতরাং সঠিক উত্তর দক্ষতা।
উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
প্রশ্ন ১৯২. উদ্দেশ্য নৈতিকতার আলোচ্য বিষয় কোনটি?
ক) উদ্দেশ্য খ) ফলাফল
গ) প্রক্রিয়া ঘ) উপরের সবগুলো
সঠিক উত্তর: খ) ফলাফল
Live MCQ Analytics: Right: 1%; Wrong: 55%; Unanswered: 42%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ প্রশ্নের অপশন অনুসারে – সঠিক উত্তর: খ) ফলাফল।
উদ্দেশ্য/পরিণামবাদী (Teleological/Consequentialist) নৈতিকতা
উদ্দেশ্যমুখী নৈতিক মতবাদ হল একটি নৈতিক দর্শন যা বলে যে একটি কাজের নৈতিকতা তার ফলাফলের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, যদি একটি কাজের ফলাফল ইতিবাচক হয়, তবে সেটি নৈতিকভাবে সঠিক এবং যদি ফলাফল নেতিবাচক হয়, তবে সেটি নৈতিকভাবে ভুল।
– উদ্দেশ্যবাদের অপর নাম পরিণামবাদ [Consequentialism]। এই মতবাদ অনুযায়ী, একটি কাজের উদ্দেশ্য নয়, বরং তার ফলাফলই গুরুত্বপূর্ণ।
– Teleological শব্দটি Greek টার্ম “telos,” শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো “End” বা পরিণাম; এবং logos যার অর্থ Science বা বিজ্ঞান।
– সুতরাং, এটি এমন একটি নৈতিক তত্ত্ব, যেখানে কর্তব্য বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা নির্ধারিত হয় সেই লক্ষ্য বা পরিণতির ফলাফল ভালো বা মন্দ হওয়ার উপর।
সূত্র: – ব্রিটানিকা: [Link]
প্রশ্ন ১৯৩. জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে- এ বিষয়ে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে?
ক) অনুচ্ছেদ-২১ খ) অনুচ্ছেদ-১৮
গ) অনুচ্ছেদ-২৮ ঘ) অনুচ্ছেদ-২৬
সঠিক উত্তর: খ) অনুচ্ছেদ-১৮
Live MCQ Analytics: Right: 66%; Wrong: 5%; Unanswered: 28%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে- এ বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ – ১৮ উল্লেখ রয়েছে।
– সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে রয়েছে নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য।
– সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদে রয়েছে মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল।
– সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে রয়েছে ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য।
• অনুচ্ছেদ – ১৮: জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা:
– (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
• অনুচ্ছেদ – ১৮ ক: পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
– বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে।
∴ সুতরাং সঠিক উত্তর অনুচ্ছেদ-১৮।
উৎস: বাংলাদেশের সংবিধান।
প্রশ্ন ১৯৪. ‘সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা‘-বিষয়টি সংবিধান মতে-
ক) নৈতিক বিষয় খ) মানবাধিকার
গ) মৌলিক অধিকার ঘ) নিয়োগ ও কর্মের শর্ত
সঠিক উত্তর: গ) মৌলিক অধিকার
Live MCQ Analytics: Right: 65%; Wrong: 14%; Unanswered: 19%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগ (অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে ৪৭) মৌলিক অধিকারসমূহের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে।
– এর মধ্যে অনুচ্ছেদ ২৯ নং অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে ‘সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা’ নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করে।
– অনুচ্ছেদ ২৯(১): সকল নাগরিকের জন্য সরকারি নিয়োগ-লাভে সমান সুযোগ থাকবে।
– অনুচ্ছেদ ২৯(২): কোনো নাগরিককে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে সরকারি নিয়োগে অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে না বা তার প্রতি বৈষম্য করা যাবে না।
– অনুচ্ছেদ ২৯(৩): এই অনুচ্ছেদে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বিধান (যেমন: কোটা ব্যবস্থা) রাখার বিষয়ে উল্লেখ আছে, তবে এটি সাধারণ সমতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
অন্যদিকে,
• নৈতিক বিষয়:
– সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা কোনো নৈতিক বিষয় নয়, বরং এটি সংবিধানে আইনগতভাবে সুরক্ষিত একটি অধিকার।
• মানবাধিকার:
– যদিও সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা মানবাধিকারের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে (যেমন: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে), বাংলাদেশের সংবিধানের প্রেক্ষাপটে এটি সুনির্দিষ্টভাবে মৌলিক অধিকার হিসেবে তালিকাভুক্ত।
– তাই ‘মানবাধিকার’ শব্দটি এখানে সঠিক নয়।
• নিয়োগ ও কর্মের শর্ত:
– সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা নিয়োগ প্রক্রিয়ার একটি দিক হলেও, এটি কেবল নিয়োগ বা কর্মের শর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
– এটি একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃত, যা নিয়োগের আগে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে প্রযোজ্য।
সুতরাং ‘সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা’-বিষয়টি সংবিধান মতে মৌলিক অধিকার।
উৎস: বাংলাদেশ সংবিধান।
প্রশ্ন ১৯৫. মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যেবোধ গড়ে উঠে-
ক) আইনের বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে
খ) সামাজিকীকরণের মাধ্যমে
গ) অর্থনৈতিক প্রণোদনার মাধ্যমে
ঘ) উচ্চমানের প্রযুক্তি অনুসরণের মাধ্যমে
সঠিক উত্তর: খ) সামাজিকীকরণের মাধ্যমে
Live MCQ Analytics: Right: 77%; Wrong: 4%; Unanswered: 18%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যেবোধ গড়ে উঠে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে।
সামাজিক মূল্যবোধ:
– যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাই সামাজিক মূল্যবোধ।
– সমাজবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ই.মেরিল এর মতে, “সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের দলীয় কল্যাণের জন্য আচরণ সংরক্ষণ করা, যা মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে।
– বড়দের সম্মান করা, সহনশীলতা, দানশীল হওয়া, আতিথেয়তা ইত্যাদি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ।
– সুতরাং মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যেবোধ গড়ে উঠে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে।
অন্যদিকে,
– আইনের বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে সামাজিক মূল্যেবোধ গড়ে উঠে না।
– অর্থনৈতিক প্রণোদনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মূল্যেবোধ গড়ে উঠে।
– উচ্চমানের প্রযুক্তি অনুসরণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন হয়।
উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন, প্রথম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।
প্রশ্ন ১৯৬. বাংলাদেশ নামক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি-
ক) মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা
খ) মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা
গ) প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
ঘ) উপরের সবকটি
সঠিক উত্তর: ঘ) উপরের সবকটি
Live MCQ Analytics: Right: 68%; Wrong: 31%; Unanswered: 0%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ বাংলাদেশ নামক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি বাংলাদেশ নামক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা ও প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অর্থাৎ উপরের সবকটি।
→ বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে,
– প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে৷
⇒ মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা:
– এটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানুষের সম্মান ও অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে।
– এটি বাংলাদেশের প্রজাতন্ত্রের একটি মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।
⇒ মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা:
– বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।
– এর মধ্যে রয়েছে বাকস্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সমতা, এবং আইনের দৃষ্টিতে সমান সুরক্ষা।
– সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের জনগণের জন্য মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য।
⇒ প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা:
– বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ এবং ১১-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে।
– এটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূলনীতি, যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।
– স্থানীয় সরকার, সংসদীয় নির্বাচন, এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অংশগ্রহণ বাস্তবায়িত হয়।
∴ সুতরাং সঠিক উত্তর উপরের সবগুলো।
উৎস: বাংলাদেশ সংবিধান।
প্রশ্ন ১৯৭. সুশাসন বিষয়ক ধারণাটি প্রথম কোন খ্রিষ্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে-
ক) ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে খ) ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে
গ) ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে ঘ) ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে
সঠিক উত্তর: গ) ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে
Live MCQ Analytics: Right: 55%; Wrong: 11%; Unanswered: 33%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালে “Governance and Development” বা ‘শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন‘ শীর্ষক রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে।
→ ১৯৯৭ সালে UNDP ‘Governance for Sustainable Human Development’ এই নামে তাদের একটি পলিসিতে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান ও এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে।
→ ১৯৯৫ সালে Asian Development Bank (ADB) ‘Governance: Sound Development Management’ শীর্ষক রিপোর্টে ‘সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করে।
• বিশ্বব্যাংক ও সুশাসন:
– ‘সুশাসন’ ধারণাটি বিশ্ব ব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা।
– ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম ‘সুশাসন’ (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়।
– এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সুশাসনের অভাবেই এরূপ অনুন্নয়ন ঘটেছে।
– ১৯৯৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, ‘সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতিই হলো গভর্নেন্স।’
– ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকাশ করে যে, সুষ্ঠু গভর্নেন্স বা সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল।
– বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালে “Governance and Development” বা ‘শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন’ শীর্ষক রিপোর্টে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১৯৮. সুশাসন বিষয়ক ধারণাটি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রথম তাদের প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে-
ক) ইউএনডিপি খ) বিশ্বব্যাংক
গ) ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক ঘ) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল
সঠিক উত্তর: খ) বিশ্বব্যাংক
Live MCQ Analytics: Right: 71%; Wrong: 9%; Unanswered: 19%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালে “Governance and Development” বা ‘শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন’ শীর্ষক রিপোর্টে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে।
বিশ্বব্যাংক ও সুশাসন:
– ‘সুশাসন’ ধারণাটি বিশ্ব ব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা।
– ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম ‘সুশাসন’ (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়।
– এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সুশাসনের অভাবেই এরূপ অনুন্নয়ন ঘটেছে।
– ১৯৯৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, ‘সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতিই হলো গভর্নেন্স।’
– ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকাশ করে যে, সুষ্ঠু গভর্নেন্স বা সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল।
– বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালে “Governance and Development” বা ‘শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন‘ শীর্ষক রিপোর্টে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে বিস্তাড়িত ভাবে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে।
অন্যদিকে,
→ ইউএনডিপি সুশাসনের বিষয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করেছে, বিশেষ করে ১৯৯০-এর দশক থেকে, যখন তারা তাদের প্রতিবেদনে সুশাসনকে টেকসই উন্নয়নের একটি মূল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে।
→ ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IsDB) মূলত ইসলামি অর্থনীতির নীতির ভিত্তিতে সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করে।
– যদিও এই সংস্থা উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে, তবে সুশাসনের ধারণাটি প্রথম বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এর কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।
→ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বিশ্বব্যাংকের ১৯৮৯ সালের প্রতিবেদনের পরবর্তী।
– তাছাড়া, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সুশাসনের ধারণাটি প্রথম তুলে ধরার পরিবর্তে দুর্নীতি প্রতিরোধে বেশি মনোযোগী।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ১৯৯. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশনটি গৃহীত হয়?
ক) ৩১ জানুয়ারি ২০০৩ খ) ৩১ অক্টোবর ২০০৬
গ) ৩১ অক্টোবর ২০০৩ ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮
সঠিক উত্তর: গ) ৩১ অক্টোবর ২০০৩
Live MCQ Analytics: Right: 11%; Wrong: 11%; Unanswered: 76%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা: ◉ ৩১ অক্টোবর ২০০৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশনটি গৃহীত হয়।
– উপরের অন্যান্য অপশন গুলো যুক্তিযুক্ত নয়।
– সুতরাং সঠিক উত্তর: ৩১ অক্টোবর ২০০৩ সালে।
UNCAC:
– জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC):
– UNCAC এর পূর্ণরূপ: United Nations Convention Against Corruption.
– জাতিসংঘের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কনভেনশন হলো আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী বহুপাক্ষিক চুক্তি।
– জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত হয়: ৩১ অক্টোবর, ২০০৩ সালে।
– কার্যকর হয়: ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৫।
– স্বাক্ষরস্থল: মেরিডা, মেক্সিকো।
– বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে: ২০০৭ সালে।
উৎস: UN ওয়েবসাইট।
প্রশ্ন ২০০. ৭ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা-
ক) ১৯২টি খ) ১০৯টি
গ) ১৯০টি ঘ) ১৯১টি
সঠিক উত্তর: ঘ) ১৯১টি
Live MCQ Analytics: Right: 7%; Wrong: 12%; Unanswered: 80%; [Total: 30415]
ব্যাখ্যা:◉ ৭ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত United Nations Convention Against Corruption স্বাক্ষরকারী দেশ ১৯১টি।
• জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে প্রায় সকল দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে মাত্র ২টি দেশ যোগ দেয়নি।
• ১৯২টি: এটি জাতিসংঘের মোট সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যার কাছাকাছি, কিন্তু UNCAC-এর স্বাক্ষরকারী/পার্টি দেশের সংখ্যা নয়।
• ১০৯টি: এটি কোনো প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান নয়; সম্ভবত অন্য কোনো কনভেনশনের সঙ্গে মিশ্রণ।
• ১৯০টি: এটি ২০২৪-এর আগের কোনো আনুমানিক সংখ্যা হতে পারে, কিন্তু ৭ আগস্ট ২০২৪-এর তথ্য অনুসারে ১৯১টি।
মেরিডা কনভেনশন:
– আনুষ্ঠানিক নাম: United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
– জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী একমাত্র বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা।
– UNCAC-এর লক্ষ্য: দুর্নীতি প্রতিরোধ, অপরাধীকরণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং কারিগরি সহায়তা।
– সাধারণ পরিষদে অনুমোদন: ৩১ অক্টোবর, ২০০৩ সালে।
– স্বাক্ষরকাল: ৯-১১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে।
– স্বাক্ষরস্থল: মেরিডা, ইউকাটান, মেক্সিকো।
– কার্যকর হওয়ার তারিখ: ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৫ সালে।
– বর্তমান স্বাক্ষরকারী দেশ: ১৯১টি দেশ।
– বাংলাদেশের স্বাক্ষর: ২০০৭ সালে, এবং পরবর্তীতে অনুমোদনও দিয়েছে।
উৎস: UNCAC ওয়েবসাইট।










ধন্যবাদ এত সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য
স্বাগত ভাইয়া।